রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) শুধু বাংলা সাহিত্যের অগ্রনায়কই নন, তিনি ছিলেন একজন চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক পথিক। তার সাহিত্যকর্ম, বিশেষত কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ও গান এ সবকিছুতেই তার ধর্ম ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। তবে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচর্চা কোনো গোঁড়া ধর্মীয় রীতি-নীতির অনুসারী ছিল না; বরং এটি ছিল গভীর মানবতাবাদী, নিরাকার ব্রহ্মবাদ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যনির্ভর আধ্যাত্মিকতার অনুসন্ধান।
পারিবারিক ঐতিহ্য সাধারণত মানুষের ধর্ম ভাবনা এবং ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে। রবীন্দ্রনাথও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিবেশ ছিল ব্রাহ্ম আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত। তার পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রভাবশালী নেতা। তিনি উপনিষদ পাঠে মনোনিবেশ করতেন এবং ব্যক্তিগত সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। এই পরিবেশেই রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বর, ব্রহ্ম ও আত্মার গভীর ধারণা লাভ করেন। তবে পরিণত বয়সে এসে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের আনুষ্ঠানিকতা ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং নিজের মতো করে একটি সর্বজনীন মানবিক ধর্ম ভাবনার জন্ম দেন।
ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল ধারণা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। তবে বিভিন্ন রেফারেন্স এবং তার ব্যক্তিগত জীবনাচরণ পর্যালোচনা করে যতটা জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ছিল একটি অভ্যন্তরীণ উপলব্ধি, যা ব্যক্তিকে পরমসত্তার সঙ্গে যুক্ত করে। তার মতে, ‘ধর্মের মূল হচ্ছে আত্মার মুক্তি এবং সর্বজীবের সঙ্গে ঐক্য উপলব্ধি করা।’ তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর ব্যক্তির অন্তরে অবস্থান করেন, বাহ্যিক মন্দির-মসজিদে নন। এজন্য তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মতো কোনো আচার অনুষ্ঠান পালন করতেন না। দেব-দেবীর পূজা-অর্চনাও পছন্দ করতেন না। তার কাছে ভক্তি ও করুণাই ধর্মচর্চার আসল রূপ। তিনি মনে করতেন, মানবপ্রেমই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মানুষের সেবা করলেই ঈশ্বরকেই সৃষ্টিকর্তার সন্ধান পাওয়া যাবে। উপনিষদ ও গীতার দর্শন তার ভাবনাকে কিছুটা প্রভাবিত করলেও তিনি তা কেবল দার্শনিক পাঠ হিসেবে নেননি, বরং জীবনানুভবের স্তরে নিয়ে এসেছিলেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমর গ্রন্থ ‘গীতাঞ্জলি’তে তার ধর্মীয় উপলব্ধির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনেকেই মনে করেন, ‘গীতাঞ্জলি’ (১৯১০) হলো তার আধ্যাত্মিক অনুভূতির মহাসার। এতে আমরা দেখতে পাই, রবীন্দ্র জীবনের সঙ্গে অন্তরাত্মার সংলাপ। এই যেমন তিনি বলেছেন, ‘আমার হৃদয় হতে হৃদয়েরে দেখা দিবে তুমি।’ ঈশ্বর এখানে কোনো বিচারের দেবতা নন, বরং প্রেমময়, করুণাময় এক সত্তা, যিনি প্রতিনিয়ত মানব জীবনের সঙ্গে যুক্ত।
সমাজ ও ধর্ম নিয়ে তার অবস্থান ছিল অসাম্প্রদায়িক। যদিও তার কোনো কোনো লেখায় কেউ কেউ মুসলিম বিদ্বেষের অভিযোগ করেছেন। অভিযোগ রয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ তার গল্প কিংবা উপন্যাসে মুসলিম নামীয় চরিত্রগুলোকে যথাযথ মর্যাদা না দিয়ে কিছুটা অবজ্ঞা এবং অবহেলা দেখিয়েছেন। তবে তৎকালীন মুসলমানদের তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিলে এই অভিযোগ তেমন একটা আমলে নেওয়ার মতো না। তবে এও সত্যি যে, বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ধর্মীয় উদারতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে এও সত্যি যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কুসংস্কার, ধর্মীয় বিভাজন, এবং সাম্প্রদায়িকতার কঠোর সমালোচক ছিলেন। তার মতে, ধর্ম যেন মানবতাবিরোধী বিভাজনের অস্ত্র না হয়। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষে ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন সব ধর্মেই পরম সত্যের সন্ধান আছে, তাই কোনো ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলার একচেটিয়া অধিকার নেই।
উল্লেখ্য, শান্তি নিকেতন এবং পরবর্তী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেন, তা ধর্মীয় মৌলিকত্বের বাইরে গিয়ে আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা এবং মানবতাবাদের এক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, শিক্ষা হলো, জীবন ও জগৎকে উপলব্ধির উপায়। ধর্মচর্চা মানে রীতি-নীতি নয়, বরং আত্মদর্শন ও সত্যের অনুসন্ধান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গানেও তার ধর্ম চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের ‘ভক্তিমূলক গান’ তার ধর্মীয় দর্শনের সরাসরি প্রতিফলন। যেমন-
‘তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম’
‘হে নূতন, দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণে’!
এসব গানে ঈশ্বরের কাছে তার আত্মসমর্পণ, জীবনের অর্থের খোঁজ এবং ঈশ্বরকে পাওয়ার আকুতি প্রকাশ পেয়েছে।
আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ না করলেই নয়। আর তা হল, রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ নিছক নৈতিকতাবাদ নয়, বরং সৌন্দর্য চেতনার সঙ্গে যুক্ত। তিনি ঈশ্বরকে শুধু উপাস্য হিসেবে নয়, সৃষ্টি ও সৌন্দর্যের উৎস হিসেবে দেখেছেন। যেমন- তিনি মনে করতেন, ‘শান্তম, শিবম, অদ্বৈতম। এই ব্রহ্মধারায় তিনি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন। ধর্ম ভাবনায় নন্দনতত্ত্ব এবং এর চর্চা রবীন্দ্রনাথের একটা দারুণ সংযোজন। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচর্চা ছিল মুক্তচিন্তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত; যেখানে মানুষ, প্রকৃতি ও পরমতত্ত্ব এক অভিন্ন সত্তায় মিশে যায়। তিনি ধর্মকে ভয়ের জায়গা নয়, ভালোবাসার স্থান বানিয়েছেন। তার ধর্মীয় চেতনা আমাদের শেখায়, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে’। এ যেন এক অন্তর্জাগরণের আহ্বান, এক স্বনির্ভর আধ্যাত্মিক অভিযাত্রা। পরিশেষে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচর্চা কোনো সম্প্রদায়ের গ-িতে আবদ্ধ নয়। বরং তা বিশ্বজনীন, মানবিক ও আধ্যাত্মিক এক অনুসন্ধান। যা আজও অনেক মানুষের ধর্মবোধের এক আলোকবর্তিকা।


-20250822011726.webp)



-20250822090113.webp)
-20250822085850.webp)
-20250822085702.webp)




-20250822084938.webp)

-20250822084444.webp)

-20250822023328.webp)

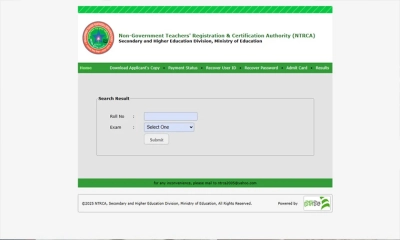









-20250816003654.webp)



আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন