বাংলাদেশ আজ এমন এক সংকটময় মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, যার তাৎপর্য কেবল রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও গভীর। প্রথম দৃষ্টিতে দেখা যায়, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে এক বছরের ব্যবস্থাপনায় দেশ মোটামুটি স্থিতিশীল থেকেছে। বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতি, জ্বালানি সংকট আর খাদ্যদ্রব্যের ঊর্ধ্বগতির ভেতরেও বাংলাদেশ তুলনামূলক নিয়ন্ত্রণ রাখতে পেরেছে দাম। ভর্তুকি, সীমিত মুদ্রানীতি, আর্থিক কড়াকড়ি সব মিলিয়ে সরকার শ্রীলঙ্কা কিংবা পাকিস্তানের মতো বিপর্যয় ঠেকাতে সক্ষম হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও ভালোই বেড়েছে; তৈরি পোশাক খাত এখনো টিকে আছে, রপ্তানি থেকে রোজগার আসছে, অর্থপ্রবাহ চলছে।
এসব অর্জন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। নীতিনির্ধারকরা বারবার বলছেন, ‘আমরা প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়ে ভালো আছি’ সংকীর্ণ অর্থে এ যুক্তি ভুল নয়। কিন্তু সমস্যা হলো, ম্যাক্রো-স্থিতিশীলতা রাজনৈতিক নিশ্চয়তার বিকল্প হতে পারে না। কিছুটা সময় কিনে দেওয়া যায়, কিন্তু ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা কেনা যায় না। অর্থনীতির ভাষায় বলতে গেলে, আস্থার দাম অনেক সময় এক ত্রৈমাসিকের সুন্দর ডেটার চেয়েও বেশি মূল্যবান।
রাজনৈতিক শূন্যতার অর্থনৈতিক খেসারত
বাংলাদেশ যে রাজনৈতিক অচলাবস্থার ভেতর আছে, সেটা শুধু নৈতিক বা সাংবিধানিক সমস্যা নয় এর অর্থনৈতিক খরচও আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এই খরচ নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাদের বিতর্ক মূলত ‘কোন দল ক্ষমতায় যাবে’এই প্রশ্নে সীমাবদ্ধ। অথচ ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সাধারণ মানুষ প্রতিদিন অনুভব করছে অনিশ্চয়তার চাপ। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীরা সতর্ক করেছেন, জাতীয় নির্বাচন ঘিরে অনিশ্চয়তা দেশের আবাসন বাজারকে কার্যত স্থবির করে দিয়েছে ধনীরা বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনতে অনাগ্রহী, আর মধ্যবিত্ত শ্রেণিও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে পুরো খাত থেকে।
বিদেশি বিনিয়োগ বছরের পর বছর শ্লথ। অনেক বহুজাতিক কোম্পানি, যারা হোটেল বা শিল্প-কারখানা তৈরি শুরু করেছিল, তারা ইচ্ছে করেও উদ্বোধন করছে না। কারণ একটাই বাংলাদেশ কোন দিকে যাচ্ছে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আদৌ ফিরবে কিনা, তারা জানে না। এর প্রভাব নেমে আসে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ওপরও। রেস্টুরেন্ট বা মাঝারি ব্যবসায়ীরাও নতুন শাখা খোলায় দোটানায় পড়ে আছে। তাদের মুখে একই কথা: ‘দেশ কোথায় যাচ্ছে, সেটা আগে দেখা যাক।’ এই অপেক্ষা এক ধরনের অদৃশ্য অর্থনৈতিক খরচ, যা আজকের মুদ্রাস্ফীতির পরিসংখ্যানে ধরা পড়ে না, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় ধরায়।
বিনিয়োগ কখনো শুধু বর্তমান সংখ্যার ওপর দাঁড়িয়ে হয় না, বরং গন্তব্যের দিকটাই বিনিয়োগকারীর কাছে বড়। তারা জানতে চায় বাংলাদেশ কি প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল অর্থনীতি হতে চায়, নাকি স্থিতিশীল উৎপাদনশীল দেশ, নাকি সেবাভিত্তিক বাজার? রাজনৈতিক নেতৃত্ব কোন দিশা দিচ্ছে, সেটাই নির্ধারণ করে পুঁজি কোথায় যাবে। কিন্তু যখন ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, তখন সেই পুঁজি জমে যায়।
শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, রাজনৈতিক অস্থিরতা কেবল সরকারকেই নড়বড়ে করে না, অর্থনীতিকেও তছনছ করে দেয়। শ্রীলঙ্কা বছরের পর বছর ‘সব ঠিক আছে’ বলার ভান করেছে, অথচ আস্থার ফাঁক পূরণ করতে পারেনি। পাকিস্তান বারবার নির্বাচনি বিলম্ব আর রাজনৈতিক উলোটপালটে এমন এক আস্থাহীনতায় পড়েছে, যেখানে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা পা রাখতে ভয় পাচ্ছে। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থানকে যদি অবহেলা করা হয়, সেই একই পরিণতির দিকে আমরা এগোচ্ছি।
সাধারণ মানুষের জীবন থেকে বিনিয়োগ পর্যন্ত
এটা শুধু সংখ্যার খেলা নয়। রপ্তানিকারক যদি দীর্ঘমেয়াদি অর্ডার নিতে ভয় পায়, শ্রমিকের চাকরি যায়। আন্তর্জাতিক হোটেল যদি প্রকল্প আটকে রাখে, নির্মাণ শ্রমিকের উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়। ভিসা-সীমাবদ্ধতা যেমন মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিমে শ্রমবাজার সংকুচিত করছে, তেমনি রাজনৈতিক অস্থিরতা নতুন কর্মসংস্থানের দরজাও বন্ধ করে দিচ্ছে।
অন্যদিকে, বেসরকারি খাতের তথ্য আরও হতাশাজনক। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব বলছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে শিল্প খাতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বিতরণ সাত প্রান্তিকের মধ্যে সর্বনি¤œ পর্যায়ে নেমেছে। জুনে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে মাত্র ৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম। মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য এলসি খোলাও টানা দুই বছর ধরে কমছে। এই সংখ্যাগুলো স্পষ্ট করে দিচ্ছে, রাজনৈতিক অচলাবস্থা সরাসরি বিনিয়োগকে শ্বাসরোধ করছে।
এই প্রেক্ষাপটে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত রোববার ঘোষণা করেছেন, ১৩তম জাতীয় নির্বাচন আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথম ভাগেই হবে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ‘নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।’ এ বক্তব্য কেবল রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়, অর্থনীতির জন্যও একটি নির্ভরতার প্রতীক।
তবে সমস্যা হচ্ছে, জামায়াতে ইসলামী বা ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির মতো দলগুলো এখনো গণপরিষদ নির্বাচন বা বিকল্প প্রক্রিয়ার দাবি তুলছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো যত বেশি বিলম্ব, তত বেশি অনিশ্চয়তা, আর সেই অনিশ্চয়তা অর্থনীতিকে গিলে খায়। ড. ইউনূস যথার্থই সতর্ক করেছেন’ যে কোনো বিকল্প চিন্তা জাতির জন্য ধ্বংসাত্মক হবে।’ এদিকে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মো. শফিকুল আলম বলেছেন আমরা ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের মতো জাতীয় নির্বাচনও শান্তিময় করতে চাই।
গণতন্ত্র অর্থনৈতিক সম্পদ
আমরা সাধারণত গণতন্ত্রকে নৈতিক বা সাংবিধানিক অধিকারের দিক দিয়ে দেখি। কিন্তু গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক দিকও আছে। একটি নতুন, বিশ্বাসযোগ্য ম্যান্ডেট পাওয়া সরকার কেবল সংস্কার করতে পারে না, বাণিজ্যচুক্তি করতে পারে আস্থার সঙ্গে, বিদেশি বিনিয়োগ টানতে পারে নির্ভরতার সঙ্গে। জনগণ যখন বিশ্বাস করে, তখন তারা খরচ করে, পরিকল্পনা করে, ব্যবসায়ীরা মূলধন খাটায়। গণতন্ত্র সেই বিশ্বাস তৈরি করে।
কারো কারো কাছে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয়তো স্বল্পমেয়াদে শান্তি রক্ষা মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে সেটা আগুন জ্বালিয়ে রাখা। যত দেরি হবে, তত গভীর হবে অনিশ্চয়তা। যখন ডেটায় এর প্রমাণ ধরা পড়বে, তখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।
বাংলাদেশ এখনো সময় হাতে রেখেছে। আমরা এখনো শ্রীলঙ্কা বা পাকিস্তানের পথে পুরোপুরি যাইনি। কিন্তু সেই পথে না যেতে হলে দ্রুত পদক্ষেপ দরকার। রাজনৈতিক স্পষ্টতা ফিরলেই আস্থা ফিরবে; আস্থা ফিরলেই বিনিয়োগ আসবে; আর বিনিয়োগ ফিরলেই কর্মসংস্থান, উৎপাদন, প্রবৃদ্ধি আবার ঘুরে দাঁড়াবে। ড. ইউনূস যে সতর্কতা দিয়েছেন, তা কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য নয়, পুরো জাতির জন্য। যদি আমরা ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ঐক্যমত তৈরি করতে না পারি, তবে সংকটের দাম দিতে হবে অর্থনীতি দিয়ে, সমাজ দিয়ে, প্রজন্ম দিয়ে।
বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে এক সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের ওপর সময়ে, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন। সেটাই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনবে, সেটাই অর্থনৈতিক আস্থার নতুন দরজা খুলবে। অন্য যে কোনো পথ কেবল অন্ধকার গহ্বরে নিয়ে যাবে।
আসিফ শওকত কল্লোল, সাংবাদিক, দি মিরর এশিয়া অনলাইন


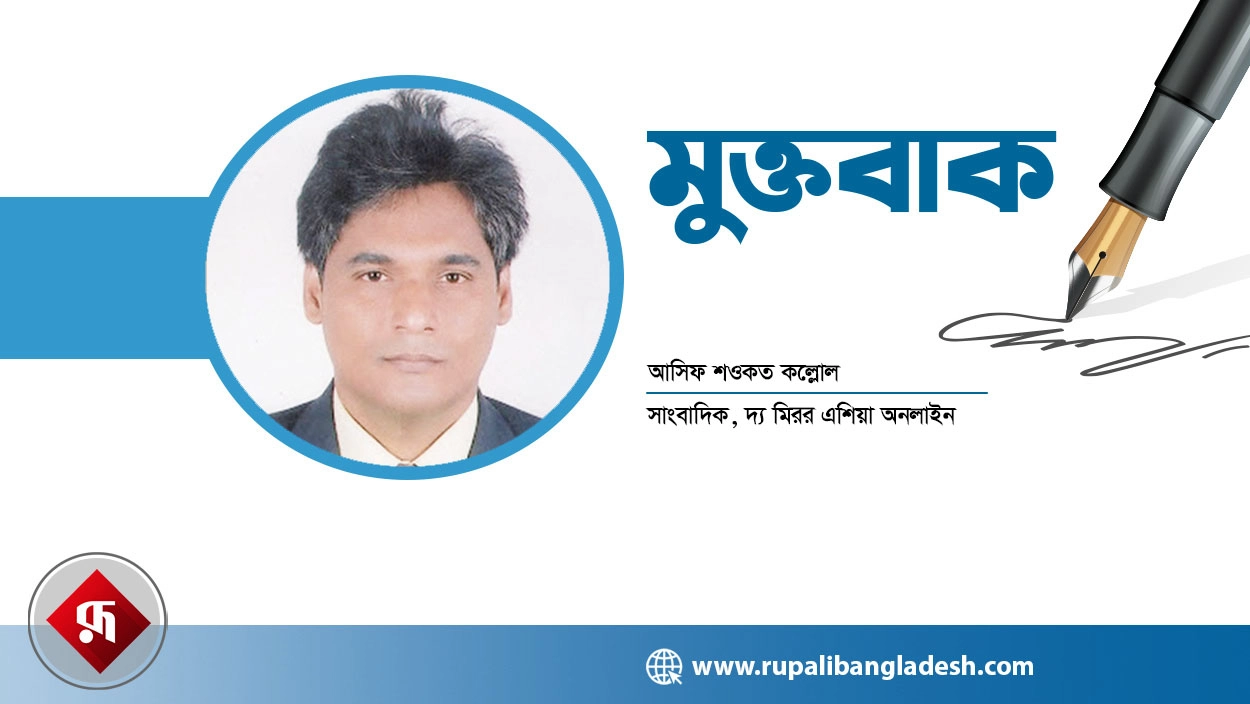
 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন



-20251210025700.webp)






-20251211023341.webp)




-20251211004859.webp)



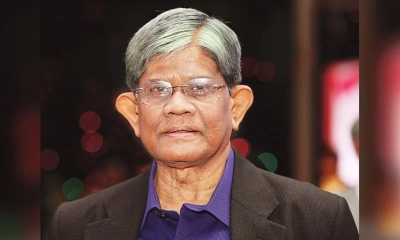

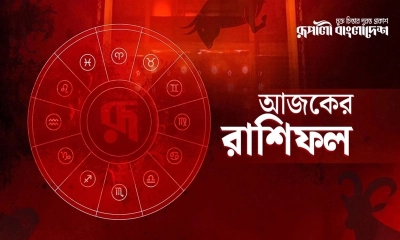

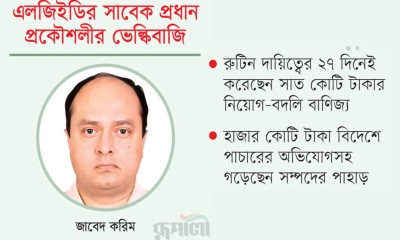
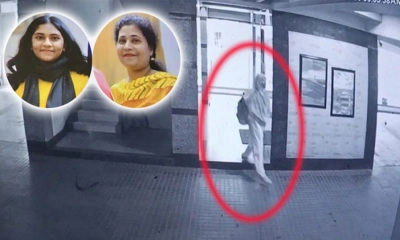


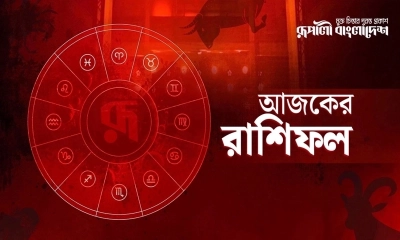







আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন