বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা যত দ্রুত হয়েছে, সামাজিক সচেতনতা ও মানসিকতার পরিবর্তন তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। নারী অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে দেশটি যতই আইন ও নীতি প্রণয়ন করুক না কেন, বাস্তবতায় দেখা যায় নারী এখনো নানা স্তরে বৈষম্য, হেনস্তা ও মানসিক নিপীড়নের শিকার। সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হলো- ডিজিটাল যুগে নতুন এক ধরনের সহিংসতা ও নিপীড়ন তৈরি হয়েছে, যা হলো ট্যাগিং ও সাইবার বুলিং।
এই দুইটি শব্দ এখন আর অপরিচিত নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যক্তিগত আক্রমণ, অবমাননাকর মন্তব্য, মিথ্যা তথ্য ছড়ানো, মানহানি কিংবা নারীর বিরুদ্ধে যৌনসংক্রান্ত ইঙ্গিতপূর্ণ কুরুচিপূর্ণ কনটেন্ট শেয়ার করার ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে যে কেউ যদি নারী অধিকার, নারীর নিরাপত্তা, যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে কিংবা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তাকেই দ্রুত ‘শাহবাগী’, ‘নারীবাদী’ ইত্যাদি ট্যাগ দিয়ে আক্রমণ করা হয়। এর ফলে মূল ইস্যু, নারীর অধিকার ও নিরাপত্তার দাবি, পেছনে পড়ে যায়; সামনে চলে আসে ব্যক্তির চরিত্র হনন।
বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বর্তমানে কয়েক কোটি। এর মধ্যে ফেসবুক, এক্স (টুইটার), ইউটিউব, টিকটকসহ নানান প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছেন তরুণ-তরুণী থেকে শুরু করে নীতি নির্ধারকরাও। এই বিশাল ডিজিটাল জনসমুদ্র একদিকে তথ্যপ্রবাহ ও গণআন্দোলনের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে, অন্যদিকে তৈরি করেছে ‘ডিজিটাল মব’, যেখানে অনলাইন ব্যবহারকারীদের একাংশ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে সংগঠিত বা অগোছালো আক্রমণ চালায়।
নারী অধিকারকর্মী, সাংবাদিক, লেখক বা সাধারণ কোনো নারী যখন কোনো নির্যাতন, হয়রানি বা বৈষম্যের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন, তখন তার বক্তব্যের গঠনমূলক সমালোচনা না করে ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি খুঁজে বের করে তা দিয়ে আক্রমণ করা হয়। কেউ কেউ আবার ভুয়া ছবি, বিকৃত ভিডিও, মিথ্যা গল্প ছড়িয়ে মানহানি করে। এই সমন্বিত আক্রমণ এত দ্রুত ঘটে যে ভুক্তভোগী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।
ট্যাগিং বা কোনো ‘লেবেল’ লাগিয়ে দেওয়া কেবল সামাজিক মাধ্যমে এক ধরনের কুরুচিপূর্ণ আচরণ নয়, বরং এটি একটি কৌশল। এর মাধ্যমে মানুষকে তার প্রকৃত বক্তব্য থেকে সরিয়ে আনা হয়। যেমন, ‘নারীবাদী’ বা ‘শাহবাগী’ বলা মানে শুধু নামকরণ নয়; বরং তাতে বিদ্রুপ, ঘৃণা, এবং এক ধরনের নৈতিক বিচার লুকিয়ে থাকে। এর ফলে সাধারণ মানুষ এমন ‘ট্যাগ’ পাওয়ার ভয়ে নীরব থাকতে শুরু করে। এই ভয়ই মূলত সবচেয়ে বড় ক্ষতি করে। কারণ নারী অধিকার বা নিরাপত্তার প্রশ্নে কেউ যদি মুখ না খোলে, তাহলে সমস্যা আড়ালে থেকে যায়। আর এভাবেই ট্যাগিং ধীরে ধীরে এক ধরনের সামাজিক সেন্সরশিপ হয়ে উঠেছে।
ট্যাগিংয়ের পাশাপাশি সাইবার বুলিং এখন এক ভয়াবহ বাস্তবতা। ফেসবুকের ইনবক্স, কমেন্ট সেকশন, টুইটার রিপ্লাই, এমনকি ইমেলেও নারীরা নিয়মিত কুরুচিপূর্ণ বার্তা, হুমকি কিংবা ব্ল্যাকমেইলের শিকার হন। বিষয়টি শুধু মানসিক কষ্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; এর কারণে অনেক নারী সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হন, কাজের জায়গায় সমস্যায় পড়েন, এমনকি আত্মসম্মানবোধ ভেঙে পড়ায় তারা পেশা বা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে দেন। বিভিন্ন গবেষণা বলছে, বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নারীদের একটি বড় অংশ অনলাইন হয়রানি ও সাইবার বুলিংয়ের শিকার। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকজন আইনগত সহায়তা নিতে পারেন। কারণ একদিকে আইনি প্রক্রিয়ার জটিলতা, অন্যদিকে সামাজিক লজ্জার ভয়।
‘এখন আর কেউ খেয়াল করার নাই, দেখলেও দেখার নাই।’ এই নীরবতা ও উদাসীনতাই সমস্যার মূল। মানুষ যখন নিয়মিত কোনো অন্যায় দেখতে থাকে কিন্তু তাতে প্রতিবাদ করে না, তখন তা ‘নরমালাইজ’ হয়ে যায়। নারীকে টার্গেট করে অপমান করা, ব্যক্তিগত জীবনের ছবি বা তথ্য টেনে আনা, কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার, সবকিছু যেন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এটি সামাজিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বাইস্ট্যান্ডার এফেক্ট, যেখানে সবাই মনে করে অন্য কেউ নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করবে, তাই আমি করলাম না। কিন্তু এর ফলে অনলাইনে নারীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার, হেনস্তা বা বুলিং চালিয়ে যাওয়ার সাহস পেয়ে যায় অপরাধীরা।
বাংলাদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ বেশকিছু আইন রয়েছে, যার মাধ্যমে অনলাইন হয়রানি বা মানহানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে এই আইনের ব্যবহার নারীর সুরক্ষায় কতটা কার্যকর হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন আছে।
প্রথমত, আইনের জটিল ধারা ও দীর্ঘসূত্রতা ভুক্তভোগীকে নিরুৎসাহিত করে। দ্বিতীয়ত, সাইবার ক্রাইম ইউনিটে অভিযোগ করলেও প্রমাণ সংগ্রহ, অপরাধী চিহ্নিত করা এবং মামলা চালিয়ে যাওয়ার ঝক্কি ভুক্তভোগীকে মানসিকভাবে ক্লান্ত করে ফেলে। তৃতীয়ত, সামাজিক লজ্জা ও প্রতিশোধের ভয় নারীদের নীরব থাকতে বাধ্য করে। এ ছাড়া আইন প্রণয়ন হলেও সামাজিক সচেতনতা তৈরি না হলে কেবল আইনের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।
ট্যাগিং ও সাইবার বুলিং বন্ধ করতে হলে গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ডিজিটাল নৈতিকতা ও সাইবার নিরাপত্তাবিষয়ক কোর্স চালু করা যেতে পারে। গণমাধ্যমকে ভুক্তভোগীর গোপনীয়তা রক্ষা করে সচেতনতামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। নারী অধিকারকর্মীদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া এবং ভুয়া খবর ও কুৎসা ছড়ানো বন্ধে ফ্যাক্ট-চেকিং বাড়াতে হবে। যদিও রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানকে বড় ভূমিকা নিতে হবে, তবুও ব্যক্তিগত পর্যায়ে নারীরা কিছু নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ নিতে পারেন। ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি বা লোকেশন খোলাখুলি শেয়ার না করা। হেনস্তাকারীর স্ক্রিনশট, লিংক, প্রমাণ রেখে আইনি সহায়তা চাওয়া। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাইভেসি সেটিংস কঠোর করা। মানসিক চাপ কমাতে হেনস্তাকারীর ব্লক/রিপোর্ট অপশন ব্যবহার করা।
তবে এগুলো কেবল প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, মূল সমস্যার সমাধান নয়। সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তনই মূল চাবিকাঠি। ট্যাগিং ও সাইবার বুলিং বন্ধের জন্য আইনি ও প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি মানসিকতার পরিবর্তন। আমাদের সমাজে এখনো নারীকে ‘সম্মানযোগ্য’ ও ‘অসম্মানযোগ্য’ হিসেবে ভাগ করার প্রবণতা আছে। যে নারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাকে অবলীলায় ‘ট্যাগ’ করে নোংরা কটূক্তি করা হয়। অথচ একই কাজ একজন পুরুষ করলে তাকে ‘সাহসী’ বলা হয়।
এই দ্বিচারিতা না বদলালে নারীর অধিকার রক্ষায় লড়াই সবসময় অসম থাকবে। পরিবারের মধ্যে ছেলে-মেয়েকে যেমন সমানভাবে নারী-পুরুষ সমতা শেখানো হয় না, স্কুল-কলেজেও তেমন কোনো কার্যকর নৈতিক শিক্ষা নেই। তাই সামাজিক মনোভাব পাল্টানোর জন্য গণআলোচনা, মিডিয়া ক্যাম্পেইন ও পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।
এ ছাড়াও সাইবার বুলিংয়ের মামলায় দ্রুত ট্রাইব্যুনাল, ভুক্তভোগীর নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করা। ফেসবুক, এক্স বা ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মে স্থানীয় পর্যায়ে কনটেন্ট মডারেশন শক্তিশালী করা। সরকার, এনজিও ও সামাজিক সংগঠন একত্রে ডিজিটাল নৈতিকতা নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচি চালানো। নারী সাংবাদিক, লেখক, অ্যাক্টিভিস্টদের জন্য মানসিক ও আইনি সহায়তা হটলাইন। ভুয়া খবর ও কুৎসার বদলে প্রমাণনির্ভর সাংবাদিকতা।
ট্যাগিং ও সাইবার বুলিং এখন কেবল ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, বরং সামাজিক ন্যায্যতা ও মানবাধিকারের প্রশ্নে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারী অধিকার রক্ষায় এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কারণ এই আক্রমণের মূল লক্ষ্যই হলো নারীর কণ্ঠরোধ করা, তাকে ভয় দেখিয়ে নীরব রাখা। তবে ইতিহাস বলে, কোনো অন্যায় বা বৈষম্য চিরকাল টিকে থাকে না যদি মানুষ সচেতন ও সংগঠিত হয়। তাই আমাদের এখন প্রয়োজন সংহতি, নৈতিক সাহস ও সচেতনতা। নারী অধিকার বা নিরাপত্তার প্রশ্নে ‘ট্যাগ’ পাওয়ার ভয় নয়, বরং ‘ট্যাগ’ ভেঙে সত্যকে সামনে আনার সাহস দেখানো। সাইবার বুলিং ও ট্যাগিং বন্ধ করা কেবল নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে না; বরং একটি ন্যায্য, সম্মানজনক ও মানবিক সমাজ গঠনের পথও প্রশস্ত করবে। ডিজিটাল যুগে যদি আমরা নারীকে সুরক্ষা ও মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হই, তবে প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক না কেন, আমাদের সামাজিক উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।
সাদিয়া সুলতানা রিমি, শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়







-20250918020810.webp)
-20250918020537.webp)
-20250918020404.webp)
-20250918020048.webp)



-20250910212413-20250912131408.webp)




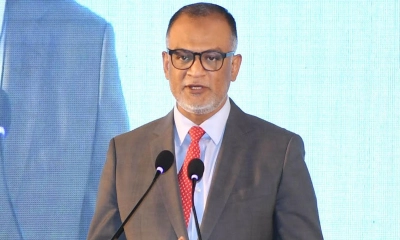







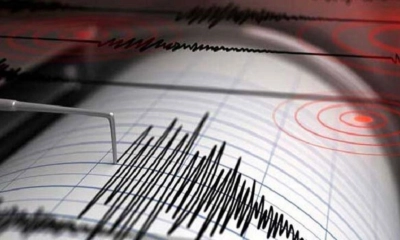

আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন