অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগে আগামী নভেম্বরে ১৮-৩৫ বছর বয়সি যুবকদের জন্য আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের সাতটি বিকেএসপি কেন্দ্রে ১৫ দিনব্যাপী এই কোর্সে ৮ হাজার ৮৫০ জন অংশ নিতে পারবেন। প্রশিক্ষণে জুডো, কারাতে, তায়কোয়ানদো ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রাথমিক কৌশল শেখানো হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে একাধিক ব্যাচে এটি আয়োজন করা হবে।
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ গণমাধ্যমে এটিকে ‘গণপ্রতিরক্ষা’ ও ভবিষ্যৎ রিজার্ভ ফোর্স গঠনের অংশ হিসেবে উপস্থাপন করছেন। অন্যদিকে নিরাপত্তা বিশ্লেষক, সাধারণ জনগণ উদ্বিগ্ন যে সঠিক কৌশল ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই এমন উদ্যোগ বিপজ্জনক ফল ডেকে আনতে পারে। এই প্রস্তাবনার প্রকাশিত বিবরণ থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, উদ্দেশ্য ঘোষিত হলেও নীতিগত ও বাস্তব প্রয়োগে অসংখ্য ঝুঁকি রয়ে গেছে। যা বিবেচনা না করলে ভালোর চাইতে ক্ষতি বাড়ার সম্ভাবনা বেশি।
প্রথম সমস্যাটি হলো- নীতিগত ভিত্তির অভাব। অনেক দেশে তরুণদের বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ দীর্ঘদিনের নীতি ও কৌশলের অংশ। সেটি সংসদে আলোচ্য ও বিধিবদ্ধ হওয়ার পরে বাস্তবায়িত হয়। আমাদের এখানে এ রকম জাতীয় কৌশল বা নীতিমালা নেই বলে বিশ্লেষকরা যে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন তা যুক্তিযুক্ত। কোনো মন্ত্রণালয় এই প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেবে? প্রশিক্ষণের লক্ষ্য-সীমা নির্ধারণ করবে কে? নাগরিকদের ভূমিকা কী? এগুলো স্পষ্ট নয়। নীতিহীন উদ্যোগ কখনো নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেয় না। বরং রাজনৈতিক-সামাজিক উত্তেজনা বেড়ে যেতে পারে।
‘অস্ত্র প্রশিক্ষণ’, এটা স্পর্শকাতর। ঘোষণায় প্রশিক্ষণে লাইভ রাউন্ড ফায়ারিং শিখানোর বিষয়ও এসেছে। যদিও উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ গণমাধ্যমে বাজেট ও অবকাঠামো সমস্যা বলে তা এখনো সম্ভব নয় বলছেন। তবু যে ধারণা থেকে শুরু, সাধারণ নাগরিকদের অস্ত্র চালনার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, তার সঙ্গে অবৈধ অস্ত্র পরিসরের বাস্তবতা যুক্ত হলে বিপদ বড় হতে পারে। জুলাই আন্দোলনের সময় অনেক পুলিশ-আর্মস লুট হয়েছে। আর অনেক অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি। অবৈধ অস্ত্র বাজার তো আছেই। সাম্প্রতিক সময়ে অনেক অস্ত্রের চালান আইনশৃঙ্খলা বাহিনী উদ্ধার করেছেন। এমতাবস্থায় যে কাউকে অস্ত্রচালনায় প্রশিক্ষণ দিলে তা পরে কোথায় ব্যবহার হবে? সেই প্রশ্ন অনিবার্য।
অন্যদিকে আছে যাচাই-বাছাই জটিলতা। উপদেষ্টা বলেছেন যে, গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে ছাত্র-যুবকদের যাচাই-বাছাই করা হবে। কিন্তু বাস্তবে কতটা কার্যকর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব হবে? ৮২৫০ জন ও ৬০০ তরুণী, মোট ৮৮৫০ জনকে ১১৪ ব্যাচে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ, এই স্কেলে মানুষের ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই করা এবং প্রশিক্ষণের পর তদারকি করা কঠিন। বিশেষত আমাদের দেশে উচ্চ বেকারত্ব, রাজনৈতিক লড়াই। সমাজের মানসিক স্থবিরতার বাস্তবতায় ‘ভুল মানুষ’ প্রশিক্ষণ পেলে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম নয়। অনেকে তো তফসিলবিহীনভাবে বিদেশি সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণœ করেছে। এই ইতিহাস কিন্তু আগেই ছিল। তাই আমাদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত।
এই প্রশিক্ষণ মেয়েদের জন্য দরকার। সে দিকটি মানতে হবে। ক্রমবর্ধমান লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার সময় আত্মরক্ষার দক্ষতা নারীদের প্রয়োজন। তবে আত্মরক্ষা ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষণ নারীকে শিখিয়ে দিলে তার নিরাপত্তা বাড়বে না। যদি পরিবেশে অস্ত্রের সহজতর প্রবাহ ও শক্তিহীন নিয়ন্ত্রণ থেকে থাকে। নারী-ভিত্তিক প্রশিক্ষণে অবশ্যই হার্ডওয়্যার নয়, কৌশল, আইনগত অধিকার, লিঙ্গভিত্তিক হেল্পলাইন ও নিরাপদ সড়ক-পরিবেশ তৈরির দিকগুলোর পদক্ষেপ আগে নেওয়া উচিত।
আরেকটি সমস্যা উদ্দেশ্য ও কমান্ড-চেইন। একজন প্রশিক্ষিত যুবক/যুবতি অনির্দিষ্ট আদেশ বা নো-কমান্ড-চেইন পরিবেশে কীভাবে ব্যবহার করবে? এই প্রশ্ন অপরিহার্য। সেনাবাহিনী বা আনুষঙ্গিক সংস্থাগুলোর মতো নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত প্রশিক্ষিত জনগণ নিজস্ব সিদ্ধান্তে অস্ত্র ব্যবহার করলে তা বিশৃঙ্খলা ডেকে আনতে পারে। উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ গণমাধ্যমে বলেছেন ‘কোনো বাহিনী গঠনের চেষ্টা নয়’, কিন্তু বাস্তবে সামাজিক কাঠামো কীভাবে পরিচালিত হবে? তা নিয়ন্ত্রণ না করে বলা কঠিন।
অন্তর্বর্তী সরকার বিষয়টি জাতীয় কৌশল ও নীতি হিসেবে সংসদীয় আঙ্গিকে আলোচনা করা উচিত। কেবল একটি মন্ত্রণালয়ের ছোট উদ্যোগ হিসেবে নয়। নিরাপত্তা, বিচার বিভাগ, সোসিওলজি, নারী নেতৃবৃন্দ ও সিভিল সোসাইটি মিলিয়ে একটি বহুমাত্রিক নীতিমালা করতে হবে। অস্ত্র-প্রশিক্ষণের বদলে আত্মরক্ষার ওপর জুডো/কারাতে ও আইনগত জ্ঞানকে প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া যায়। এগুলো নেতিবাচক ব্যবহার ঝুঁকি কমায়। যদি অস্ত্র প্রশিক্ষণের ইচ্ছা থাকে, তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ, লাইসেন্সিং, মাইক্রো-অডিটিং ও নির্দিষ্ট প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। তথ্যভিত্তিক ডেটাবেস, ব্যক্তিগত মনিটরিং ও প্রশিক্ষণ প্রত্যয়ের মাধ্যমে। এছাড়া প্রশিক্ষণের পরে পরবর্তী মানসিক মূল্যায়ন ও আত্মপর্যবেক্ষণ করা জরুরি।
কারণ অস্ত্রাধিকার ও মানসিক প্রস্তুতির মধ্যে সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়াতে নারী-বান্ধব নিরাপত্তা ও সমর্থন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। কেবল গুণগত প্রশিক্ষণ নয়, আইনগত ও মানসিক সহায়তা অবশ্যকীয়।
বিষয়টি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও বিবেচনা করতে হবে। প্রকাশিত বক্তব্যগুলোতে গণপ্রতিরক্ষা ও ভূরাজনৈতিক ভাবনা উঠে এসেছে। এগুলো রাজনৈতিক জনপ্রিয়তার হাতিয়ারও হতে পারে। সামরিক বা প্রতিরক্ষা বিষয়ের স্পর্শকাতর ভাষা জনমনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তাই বিষয়টি স্বচ্ছতা, প্রকাশ্যতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে এগোতে হবে। যদি জনস্বার্থে কাজ করা হয়ে থাকে, এই সরকারকে এই প্রস্তাবনার প্রতিটি ধাপ গণতান্ত্রিক ও নিয়ন্ত্রিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে। কাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে? কেন? কী প্রয়োজন? পরে তার পারস্পরিক কর্তৃত্ব কেমন থাকবে? এসব প্রশ্নের জবাব আগে নিয়ে নেওয়া জরুরি।
এ বিষয়ে সম্প্রতি নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) আ. ন. ম. মুনীরুজ্জামান বিবিসিকে বলেছেন,
‘যদি ব্যাকগ্রাউন্ড চেক না করে ভুল ব্যক্তিদের এমন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, এবং তারা পরবর্তীতে সেই দক্ষতা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, তবে তা দেশের জন্য উপকারের চেয়ে ক্ষতির কারণ হতে পারে। তা ছাড়া, এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণরা যেহেতু সেনাবাহিনী বা প্রতিরক্ষা সংস্থার মতো চেইন অব কমান্ডের আওতায় থাকবে না, তাই তারা এই প্রশিক্ষণ কীভাবে এবং কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে, সেই প্রশ্নটি থেকেই যায়।’
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা জোরদার বা আত্মরক্ষার নামে তরুণদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ অনেক সময় আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর অনেক দেশে। ইতিহাস বলছে, এমন উদ্যোগ ভুল হাতে পড়লে তা ভয়াবহ অস্থিরতা ডেকে আনে।
শ্রীলঙ্কায় ১৯৮-৯০-এর দশকে তামিল তরুণদের আত্মরক্ষার নামে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যা পরবর্তীতে লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলম (এলটিটিই) সন্ত্রাসী গোষ্ঠীতে রূপ নেয়। তারা দীর্ঘকাল গৃহযুদ্ধ চালায়। হাজারো প্রাণহানি ঘটায় এবং দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে। ইয়েমেনে সরকার ও উপজাতীয় পর্যায়ে তরুণদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয় আত্মরক্ষার অজুহাতে। কিন্তু পরে এই তরুণরা হুথি ও অন্যান্য বিদ্রোহী দলে যোগ দেয়। যার ফলে দেশ দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ ও মানবিক সংকটে পড়ে।
তরুণদের আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ দেওয়া আবশ্যক ও সময়োপযোগী হতে পারে। বিশেষত লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা মোকাবিলায় আত্মরক্ষার দক্ষতা প্রয়োজন। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ, বিশেষত লাইভ ফায়ারিং পর্যন্ত, কেন ও কাদের জন্য হবে? তার নীতিগত ভিত্তি, সিলেকশন পদ্ধতি, পরবর্তী তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকলে এটি ভিন্নরকম ঝুঁকি ডেকে আনবে। নিরাপত্তা বাড়ানোর ইচ্ছা প্রশংসনীয়। কিন্তু নিরাপত্তা বাড়ানোর পথে যদি নীতি, আইন ও তত্ত্বাবধান না থেকে মানবতার ক্ষতি হয়, তবে তা সমাজের জন্য হুমকি। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে ঝুঁকি-মুক্ত, স্বচ্ছ ও নৈতিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ নীতি প্রণয়ন করা। তার আগে এই ধরনের প্রশিক্ষণকে বিকল্প হিসেবে নয়, পরিমাপ ও শর্তসাপেক্ষ পদক্ষেপ হিসেবে নেওয়া শ্রেয়।
লেখক : সাহিত্যিক ও গণমাধ্যমকর্মী


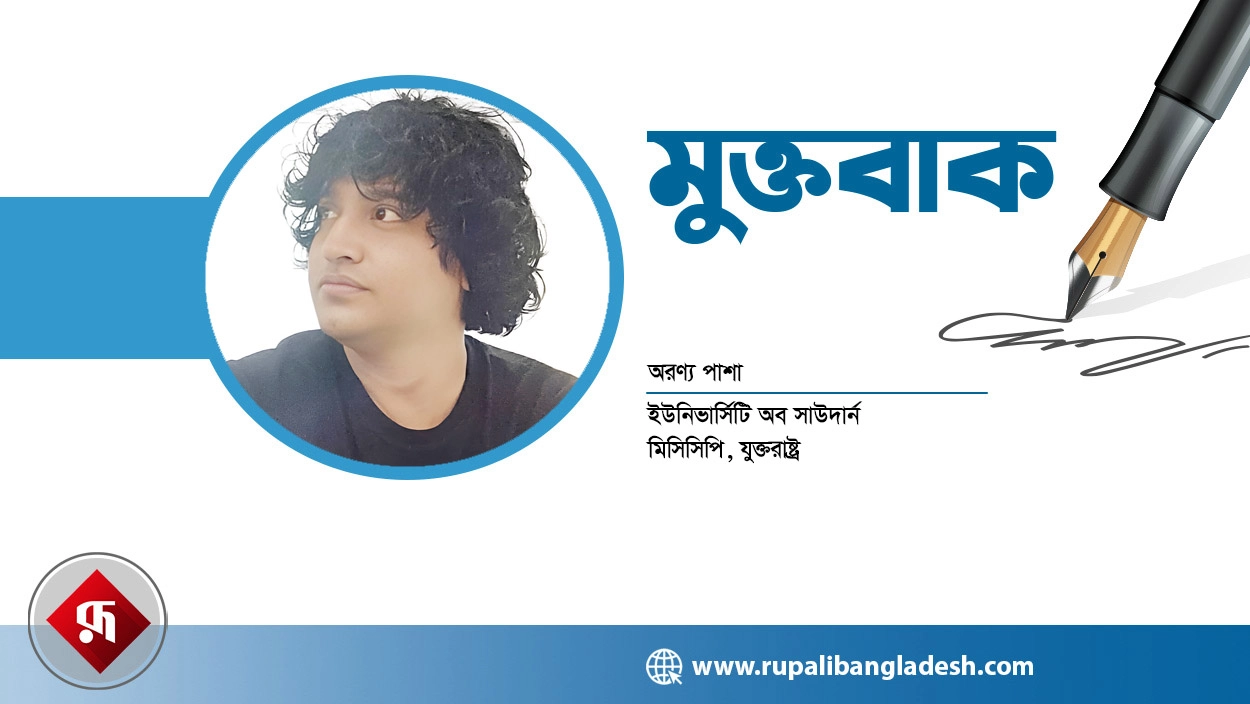
 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন



-20251103022517.webp)

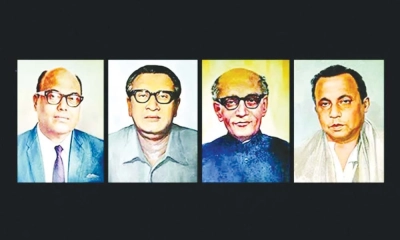



-20251103022341.webp)
-20251103022253.webp)
-20251103022203.webp)
-20251103022100.webp)





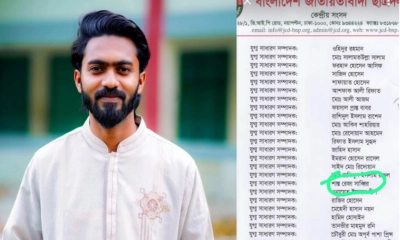







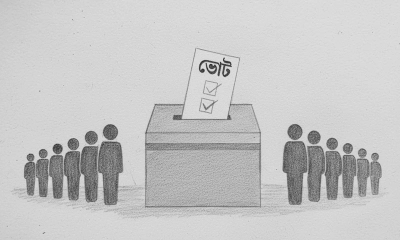

আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন