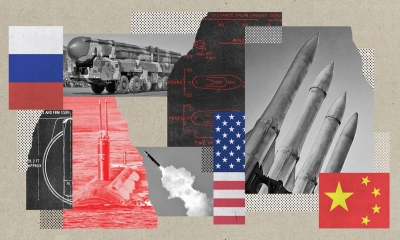সম্প্রতি ব্যাপক পরিবর্তনের মুখে পড়েছে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। মাত্র তিন বছর আগে যখন বিশ্বশক্তিরা ভারতের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিল, সেখানে বর্তমানে চীন-পাকিস্তান জোটের কৌশলগত চাপ এবং চীন-যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক চাপের মুখোমুখি হচ্ছে ভারত।
ভারতের গর্বের বিষয় ছিল—শাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) এবং কোয়াড সদস্যপদ, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্কের উন্নতি ও রাশিয়ার সঙ্গে ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর রাশিয়ার তেল কেনা ছিল ভারতীয় কূটনীতির অভাবণীয় দক্ষতার একটি অংশ। মনে করা হচ্ছিল, ভারত একসঙ্গে বিভিন্ন দিক সামলে নিতে পারছে।
কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এসে এই স্থিতিশীলতা ধ্বংসের মুখে পড়েছে। ট্রাম্পের অভিযোগ ভারত-রাশিয়ার জ্বালানি ও সামরিক সম্পর্ক নিয়ে। এছাড়া কৌশলগত ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে ভারতের উদ্বেগের প্রতি চীনের উদাসিনতাও লক্ষণীয়। বড় শক্তিগুলো ভারতকে পাশ কাটিয়ে এখন ‘দেউলিয়া’ পাকিস্তানের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক তৈরি করছে।
কিন্তু এই পরিস্থিতির কারণ কী—শুধুই ভাগ্য নাকি ভুল নীতি? নাকি আন্তর্জাতিক শক্তির পরিবর্তন, যা ভারতের নিয়ন্ত্রণের বাইরে?
বিশ্লেষকরা বলছেন, সবকিছু মিলেই মূল কারণ। তবে এর পেছনে একটা বড় কারণ আছে—ভারত যে সূক্ষ্ম ভূ-রাজনৈতিক ‘ইতিবাচক অবস্থানে’ ছিল, এখন সেই অবস্থান থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে, যেখানে কোনো ভালো বিকল্পও নেই। এই পরিবর্তন কীভাবে ঘটল তা বোঝা জরুরি।
ইতিবাচক ও তিক্ত ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান
ইতিহাসে ‘ইতিবাচক অবস্থান’ যেমন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তেমনি ‘তিক্ত স্থান’ দেখা যায় জার্মানির ক্ষেত্রে। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে ১৯০০ শতক থেকে একটি নিরাপদ ‘ইতিবাচক স্থান’ পেয়ে যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে বড় শক্তিগুলোর সাথে তেমন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি হতো না। অন্যদিকে জার্মানি ইউরোপের কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় সব সময়ই বড় শক্তিগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়ত।
স্টালিনের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের কূটনীতির মাধ্যমে ‘ইতিবাচক স্থান’ তৈরির চেষ্টা করেছিল, যা কেবল কিছু সময়ের জন্য সফল হয়েছিল।
ভারতের প্রথম ‘ইতিবাচক অবস্থান’
ভারত স্বাধীনতার আগে থেকেই কূটনীতি চালিয়ে ‘ইতিবাচক অবস্থান’ অর্জনের চেষ্টা করেছিল। নেহেরুর নির্দেশনা অনুযায়ী, ভারতে কোনো একটি পক্ষের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব এড়িয়ে চলার কৌশল ছিল মূলমন্ত্র, যাতে ভারত কৌশলগত অবস্থান শক্তিশালী করতে পারে।
‘কোল্ড ওয়ার’-এর প্রেক্ষাপটে ভারত একটি সুশৃঙ্খল ‘ইতিবাচক স্থান’ পেয়েছিল, যা ১৯৫০-৬০ এর দশক পর্যন্ত টিকে ছিল। এ সময় ভারত ইউরোপ ও এশিয়ার শক্তির খেলায় গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবে আবির্ভূত হয়।
বর্তমান ‘ইতিবাচক অবস্থান’র উত্থান-পতন
২০০০ সালের পর ভারতকে চীনের বিরুদ্ধে একটি গণতান্ত্রিক সমতুল্য দেশ হিসেবে দেখতে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। ভারতের ১৯৯৮ সালের পারমাণবিক পরীক্ষা ও অর্থনৈতিক সংস্কারের সফলতা এই কৌশলগত সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তোলে।
২০০৪ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক অভাবণীয় উন্নতি লাভ করে। ভারত এসসিওর সদস্যপদ পায়, কোয়াড গঠন হয় এবং আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতিতে ভারতের গুরুত্ব বেড়ে যায়। এই সময় ভারত পশ্চিমা শিবিরের প্রতি কিছুটা ঝুঁকে থাকলেও এককভাবে কোনো দৃঢ় জোটে আবদ্ধ হয়নি।
ইতিবাচক অবস্থানের অবনতি
২০২০ সাল থেকে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। বিশ্বে সংঘাত ও সংকট বেড়ে যায়। দ্রুত বাড়তে থাকে চীনের শক্তি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ভারতের ‘স্বাধীন’ কূটনীতিকে শক্তি দেয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ভারতের প্রতি আস্থা কমিয়ে দেয়।
ভারতের প্রযুক্তি, সামরিক ও উৎপাদন খাতে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি না হওয়ায় পশ্চিমারা আগ্রহ কমিয়ে দেয়। পাশাপাশি চীনের আগ্রাসী আচরণ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক ‘ইতিবাচক অবস্থান’ সংকুচিত হতে থাকে।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ: মূল প্রভাবক
২০২২-২৪ সালের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ভারতের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানে বড় প্রভাব ফেলে। যুক্তরাষ্ট্র আশা করেছিল, রাশিয়াকে চাপ দিতে পারবে ভারত, তবে ভারতের এই ক্ষমতা ও প্রভাবের মাত্রাকে অতিরঞ্জিতভাবেই তুলে ধরা হয়েছিল। যদিও ভারত এই চাহিদাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে।
ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ ও কৌশল
বর্তমানে ভারত কোনো ‘ইতিবাচিক অবস্থান’ ছাড়াই নতুন ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি। পাকিস্তান ও চীনের সামরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়ার কারণে ভারতের সমর্থনের প্রতি নির্ভরতা কমে যাচ্ছে।
ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক অবশ্য ধীরে ধীরে পুনঃস্থাপিত হবে, কিন্তু আগের মতো সোনালি দিন ফিরে আসবে না। রাশিয়া চীন-পাকিস্তান জোটের সঙ্গে সম্পর্ক আরো মজবুত করেছে, যার ফলে বাড়ছে ভারতের কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ।
এই পরিস্থিতিতে ভারতকে বাস্তববাদী ও আত্মনির্ভর কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আগের অহংকার ও শক্তি প্রমাণের বদলে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে।
বিশ্লেষক
সিদ্ধার্থ রাইমেধি
কাউন্সিল ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ডিফেন্স রিসার্চের (সিএসডিআর) একজন ফেলো