বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হরহামেশা যেসব রাজনৈতিক কর্মকা- দেখা যায়, তাতে অংশগ্রহণ করে গুটিকয়েক শিক্ষার্থী। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই এসবে অনাগ্রহ। এই অনাগ্রহ কি স্বাভাবিক বিষয়? ইতিহাসের পরিক্রমায় যে মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি, সেখানে এই উদাসীনতার সুলুকসন্ধান একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব।
বাংলাদেশ অভ্যুত্থানের দেশ। আর এখানে অভ্যুত্থান মানেই তরুণ ছাত্রদের দুর্বার অংশগ্রহণ। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান পর্যন্ত যত আন্দোলন-অভ্যুত্থান এ দেশে ঘটেছে, সবগুলোতে ছাত্ররা শুধু অংশগ্রহণই করেনি; বরং নেতৃত্বও দিয়েছে। কিন্তু চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে ব্যাপক অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা থাকার পরেও সামগ্রিকভাবে ছাত্রদের রাজনৈতিক কর্মকা-ের প্রতি আগ্রহ কমেছে বলেই প্রতীয়মান হয়।
এই অনাগ্রহের কারণ হিসাবে অনেকেই প্রধানভাবে সন্ত্রাস ও দখলদারিত্বের রাজনীতিকে দায়ী করলেও একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। বাংলাদেশের ছাত্র-রাজনীতির ইতিহাসে সন্ত্রাস ও দখলদারিত্ব তো নতুন কিছু না; বরং নব্বই ও নব্বই-পূর্ববর্তী দশকগুলোতে তা ভয়াবহভাবে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে হাজির ছিল। তবুও ব্যাপক ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতির প্রতি অনাগ্রহ এত প্রবল ছিল না কেন? অর্থাৎ সংকটের গোড়াটা অন্যখানে।
গত শতকের শেষ দশকে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর গোটা বিশ্বব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসে। এ সময় থেকেই মুক্তবাজার অর্থনীতি অর্জন করে অভূতপূর্ব প্রতিপত্তি। বিশেষত আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই প্রভাব বেশ পাকাপোক্ত হয়। শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও এই প্রভাববলয়ের বাইরে থাকতে পারে না। ফলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও মুক্তবাজার অর্থনীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে তোলা হয়।
বাংলাদেশে এই সময় থেকেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কীভাবে চলবে সে ব্যাপারে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী ইউজিসির কৌশলপত্র নির্ধারণ করা হয়। এভাবে শিক্ষাকে করে তোলা হয় বাজারমুখী। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একমাত্র কাজ হয়ে ওঠে বাজারে প্রতিযোগিতার সার্টিফিকেট প্রদান।
বাংলাদেশের অর্থনীতি টিকে আছে সস্তা শ্রম রপ্তানি করে। ফলে এখানে স্বাভাবিকভাবেই বেকারত্ব একটা বড় সমস্যা। বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির দোর্দ- প্রতাপের মুখে টিকে থাকা তরুণদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় বাজারে প্রতিযোগীর সংখ্যা অগুনতি। ফলে নি¤œবিত্ত-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের কাছে পড়ার টেবিল ছাড়া বিকল্প অপশন থাকে না বললেই চলে।
ফলে রাজনীতির প্রতি তরুণদের অনাগ্রহ আসলে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ছকে ফেলে দেখার সুযোগ নেই। একে দেখতে হবে সামগ্রিকভাবে সমাজের বাস্তব কাঠামোর ভেতর দিয়ে।
তবে চব্বিশের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই কাঠামোগত অনাগ্রহ জয় করা সম্ভব। অভ্যুত্থানে ছাত্রদের অংশগ্রহণ দেখিয়েছে তারা নতুন ব্যবস্থা চায়। তবে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে যখন স্পষ্ট হলো কাক্সিক্ষত নতুন ব্যবস্থাটি এখনো অধরা, তখন হতাশাগ্রস্ত এই তরুণ তুর্কিরা যদি রাজনৈতিক কর্মকা- থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।
এখান থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া দরকার। পুরোনো বুলি আউড়ানো রাজনীতি এই প্রজন্মকে আর আশ্বস্ত করতে পারছে না। কিন্তু বিপত্তিটা হলো, তারা যে নতুন ব্যবস্থা চায় তার স্পষ্ট কোনো রূপরেখা তাদের কাছে নেই। এর প্রধান কারণ তারা অসংগঠিত। যদি বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করে নতুন কিছু করতে হয়, তাহলে ছাত্রসমাজকে সর্বপ্রথম সংগঠিত হতে হবে। সমাজের সংকটটা গভীরভাবে চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী নিতে হবে পরবর্তী পদক্ষেপ।
আরাফাত ইমরান
শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়


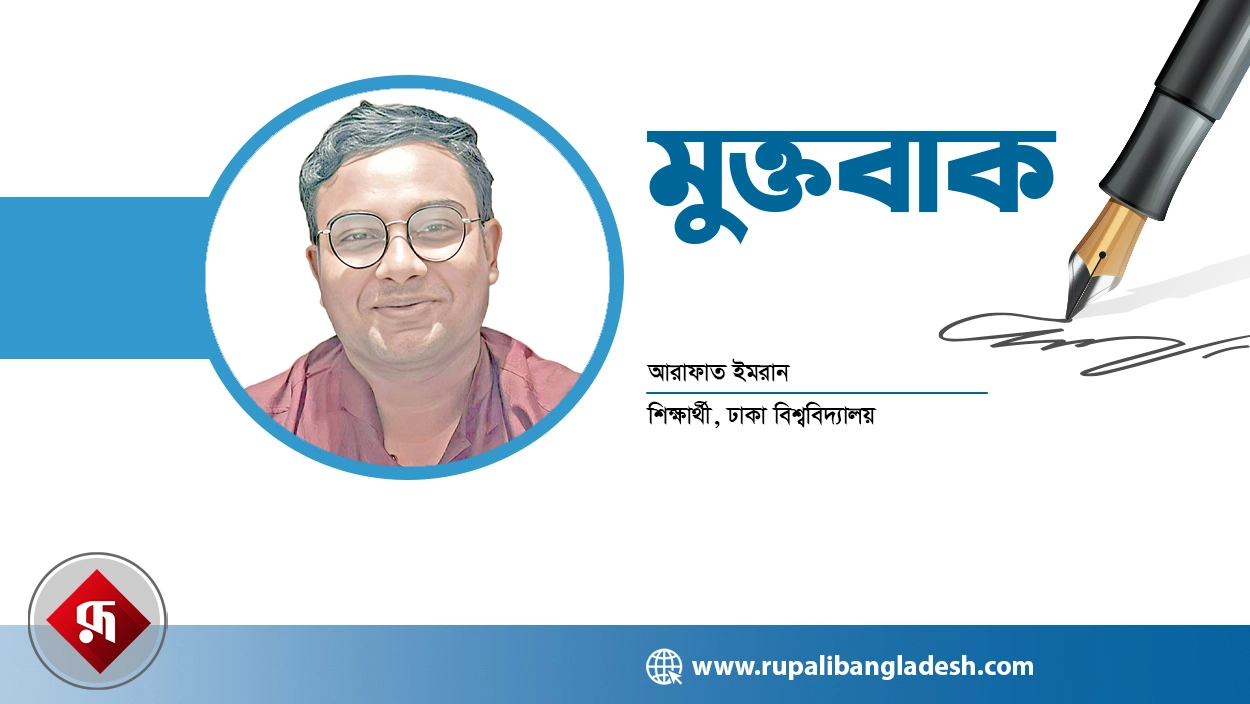



-20250924020958.webp)

-20250924020619.webp)
-20250924020502.webp)


-20250924020342.webp)
-20250924020010.webp)
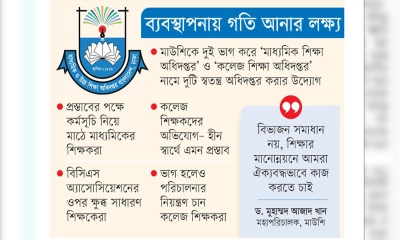













-20250917232525.webp)
আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন