সাংবাদিকতা পেশাকে বলা হয় সমাজের চতুর্থ স্তম্ভ। গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের প্রশ্নে সাংবাদিকতার ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো- এই মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিককে প্রায়ই পড়তে হয় ভয়ংকর ঝুঁকির মুখে। বিশেষত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বা ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম হচ্ছে সাংবাদিকতার সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ও বিপজ্জনক ক্ষেত্র। যখন কোনো সাংবাদিক ভূমিদস্যু, বনদস্যু, জলদস্যু, টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ বা রাজনৈতিক আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা অপরাধচক্রের বিরুদ্ধে কলম ধরেন, তখনই তিনি হয়ে ওঠেন ক্ষমতাশালী মহলের চোখের কাঁটা। তার জীবনে নেমে আসে হুমকি-ধমকি, ভয়ভীতি, মিথ্যা মামলা, এমনকি প্রাণনাশের আশঙ্কাও।
অন্যদিকে, তথাকথিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি সাংবাদিকতা- যেখানে সভা-সেমিনার, পুরস্কার বিতরণী, দিবসভিত্তিক অনুষ্ঠান বা অনুদান প্রদানের খবর প্রচারিত হয়, তা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি নিরাপদ। এতে কোনো প্রতিপক্ষ তৈরি হয় না, আবার সাংবাদিক পরিচয়ের কার্ড ঝুলিয়ে নির্ভয়ে চলাফেরা করা যায়। কিন্তু এ ধরনের সাংবাদিকতা সমাজে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনে না; বরং এটি সাংবাদিকতার প্রকৃত চেহারাকে বিকৃত করে।
বিশ্ব সাংবাদিকতার ইতিহাসে অনুসন্ধানী রিপোর্টের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে, যা প্রমাণ করে সাংবাদিকতার আসল শক্তি নিহিত আছে ঝুঁকিকে অগ্রাহ্য করে সত্য প্রকাশের মধ্যেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি তার অন্যতম উদাহরণ, যেখানে ওয়াশিংটন পোস্ট-এর দুই সাংবাদিক বব উডওয়ার্ড ও কার্ল বার্নস্টেইন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রশাসনের দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার প্রকাশ করে তাকে পদত্যাগে বাধ্য করেছিলেন। ২০১৬ সালের প্যানামা পেপারস দেখিয়েছে, বৈশ্বিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কীভাবে শত শত রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রভাবশালী মহলের দুর্নীতি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। একইভাবে মাল্টার দাফনে কারুয়ানা গালিজিয়া কিংবা রাশিয়ার আনা পলিটকোভস্কায়া সত্য অনুসন্ধানের দায়ে জীবন দিয়েছেন। তাদের মৃত্যুই প্রমাণ করে, সত্য উচ্চারণে সাহস দেখানো সাংবাদিকদের ভাগ্যে অনেক সময় রক্তাক্ত পরিণতি অপেক্ষা করে থাকে।
বাংলাদেশও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা থেকে মুক্ত নয়। ২০১২ সালে সাংবাদিক দম্পতি সাগর সারোয়ার ও মেহেরুন রুনি ঢাকায় নির্মমভাবে খুন হন। তাদের হত্যা আজও বিচারহীনতার কালো অধ্যায় হয়ে আছে, যা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ভয়াবহ ঝুঁকি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এর আগে খুলনায় সাংবাদিক মানিক সাহা বোমা হামলায় নিহত হন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতেও স্থানীয় পর্যায়ের বহু সাংবাদিক মাদক ব্যবসা, অবৈধ বালু উত্তোলন বা নদী দখলের মতো ইস্যুতে লিখতে গিয়ে হামলা, মারধর ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। এসব ঘটনা দেখায়, সাংবাদিকরা যদি সত্য বলার সাহস করেন, তবে সমাজের অন্ধকার শক্তিগুলো তাদের চরম শত্রুতে পরিণত করে।
তবু সাংবাদিকতার আসল নীতি-নৈতিকতা এখানেই- সাহসিকতার সঙ্গে সত্য প্রকাশে অবিচল থাকা। সাংবাদিকের প্রথম দায় জনগণের প্রতি, ক্ষমতাসীন বা প্রভাবশালী মহলের প্রতি নয়। সত্য যত অস্বস্তিকরই হোক, তা উদ্ঘাটন করা সাংবাদিকতার প্রাণ। ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে কলম ধরাই সাংবাদিকের কর্তব্য। প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠ করা সাংবাদিকতা নয়, বরং সেটি কেবল প্রভাবশালীদের সুবিধাবাহী তথ্য পরিবেশনের আরেক রূপ। প্রকৃত সাংবাদিকতা হলো ঝুঁকি নিয়ে হলেও সত্যানুসন্ধানে অবিচল থাকা, জনগণের স্বার্থকে সর্বাগ্রে রাখা এবং পেশার সততা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করা।
অতএব বলা যায়, সাংবাদিকতার পথ কখনো সহজ নয়। নিরাপদ সংবাদ হয়তো সাংবাদিককে বাঁচিয়ে রাখে, কিন্তু অনুসন্ধানী সংবাদই সমাজকে জাগিয়ে তোলে। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে এবং জনগণের আস্থা অর্জন করে কেবল সেই সাংবাদিক, যিনি ভয়কে উপেক্ষা করে সত্যকে সামনে আনেন। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের নিজস্ব ইতিহাস প্রমাণ করে, যারা ঝুঁকি নিয়ে সত্যানুসন্ধান চালান, তারাই হয়ে ওঠেন সমাজের প্রকৃত পথপ্রদর্শক। আর সেই পথপ্রদর্শক হওয়ার দায়ই সাংবাদিকতার প্রকৃত নীতি-নৈতিকতা।
শিব্বির আহমেদ রানা
লেখক ও গণমাধ্যমকর্মী



 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন


-20251209053648.webp)
-20251209053543.webp)


-20251209052553.webp)
-20251209052326.webp)
-20251209052201.webp)
-20251209052038.webp)




-20251203221210.webp)
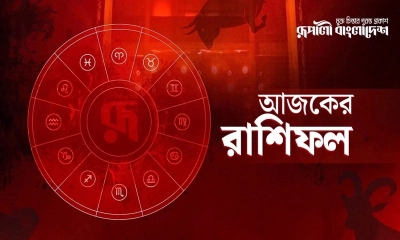






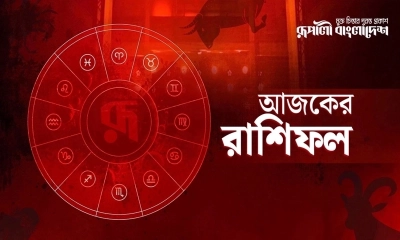


আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন