বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান পরিসরে শিক্ষক আন্দোলন যেন এক অনিবার্য কিন্তু বিভ্রান্ত আন্দোলনের প্রতিমূর্তি। যেখানে দাবির ভাষা আছে, কিন্তু দায়বোধের গভীরতা নেই; যেখানে অর্থনৈতিক হিসাব আছে, কিন্তু নৈতিক উপলব্ধি অনুপস্থিত। আমি শিক্ষক আন্দোলনের বিপক্ষে নই, কিন্তু আমি সেই আন্দোলনের দিকনির্দেশ, দর্শন ও নৈতিক ভিত্তির বিপরীতে দাঁড়াই, কারণ আমি বিশ্বাস করিÑ যে আন্দোলন শিক্ষার্থীর সময় গ্রাস করে, সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ায়, রাষ্ট্রকে আর্থিক দায়ে জর্জরিত করে কিন্তু শিক্ষার মান বাড়ায় না, সে আন্দোলন আসলে শিক্ষার নয়, স্বার্থের। তাই আমি স্পষ্ট ভাষায় বলিÑ শিক্ষক আন্দোলনের উল্টো পথে আমি।
আমরা এমন এক সময় পার করছি, যেখানে পেশার নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ ক্রমে বিলীন হয়ে যাচ্ছে প্রশাসনিক সুবিধাবাদের দাপটে। শিক্ষক নামক পেশাটি, যা একসময় জাতির আত্মার স্থপতি হিসেবে বিবেচিত হতো, আজ অনেকাংশে পরিণত হয়েছে এক প্রকারের বেতন-নির্ভর চাকরিজীবী পরিচয়ে। এককালে শিক্ষকতা মানে ছিল আত্মনিবেদন, জ্ঞানচর্চা, মানস গঠনের কঠোর সাধনা; এখন শিক্ষকতা মানে মাসিক বেতন, পদোন্নতি, ভাতা, টোকেন, এবং সুবিধার তালিকা। এর সঙ্গে এসেছে আন্দোলনের রাজনীতিÑযেখানে শ্রেণিকক্ষের বদলে রাস্তাই হয়ে উঠেছে দাবি আদায়ের মঞ্চ। এই রূপান্তর শুধু শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত অবক্ষয়ের সূচক নয়, বরং সামাজিক চেতনার ভাঙনের এক নগ্ন প্রতিচ্ছবি।
বাংলাদেশের প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ শিক্ষক নিজ নিজ এলাকায় বা আশপাশে কর্মরত। এটি নিছক একটি পরিসংখ্যান নয়; এটি প্রশাসনিক সুবিধা ও সামাজিক প্রভাবের এক জটিল বাস্তবতা। কারণ একজন শিক্ষক যখন নিজের গ্রামে বা নিজের উপজেলার বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকেন, তখন তিনি কেবল একজন শিক্ষকই থাকেন নাÑ তিনি হয়ে ওঠেন সেই এলাকার প্রভাবশালী চরিত্র। তার হাতে থাকে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষমতা, অভিভাবকের সামাজিক মর্যাদা, এবং স্থানীয় রাজনীতির নীরব নিয়ন্ত্রণ। এই অবস্থান তাকে এমন এক প্রকার প্রভাববৃত্তে নিয়ে আসে, যা তাকে শিক্ষক থেকে ক্ষমতাধর সামাজিক অভিনেতায় রূপান্তরিত করে। তাই প্রশ্ন উঠেÑ যখন শিক্ষক নিজ এলাকাতেই আরামদায়কভাবে কর্মরত, যখন তাকে অন্যত্র বদলির যন্ত্রণা পোহাতে হয় না, যখন তার পরিবারের সঙ্গে দূরত্বের কষ্ট নেই, তখন তার বাড়িভাড়া ভাতা বৃদ্ধির দাবি কতটা নৈতিক?
বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ শিক্ষকই প্রশাসনিক চাকরিজীবীদের মতো স্থানান্তরিত হয়ে কাজ করতে বাধ্য নন। একজন পুলিশ কর্মকর্তা, চিকিৎসক বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে বদলি হন, তাকে ভাড়া বাসা নিতে হয়, পরিবার থেকে দূরে থাকতে হয়, সন্তানের পড়াশোনা বিঘিœত হয়। কিন্তু শিক্ষক সাধারণত তার নিজের গ্রামেই থেকে যান, নিজের ঘরে থাকেন, পরিবারের সঙ্গে প্রতিদিনের জীবনযাপন করেন। তবু আন্দোলনের দাবিতে তিনি একই পরিমাণ বাড়ি ভাতা চান, যা দূর-প্রেরিত কর্মকর্তার সমান। এটি নিছক অসমতা নয়; এটি এক ধরনের নৈতিক বৈপরীত্য, যা সমাজে শিক্ষকদের দায়িত্ববোধের ধারণাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়Ñ শিক্ষক আন্দোলনের আর্থিক যুক্তিগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, এবং সেই অসঙ্গতি থেকেই জন্ম নেয় সামাজিক বিভ্রান্তি।
শিক্ষকতার মূল সত্তা অর্থ নয়, দায়িত্ব। কিন্তু এই মৌল ধারণাটি এখন প্রায় হারিয়ে গেছে। শিক্ষকরা আজ নিজের পেশাকে একধরনের ‘আর্থিক সেবা’ হিসেবে দেখতে শুরু করেছেন। তাদের কথাবার্তায় জ্ঞানের আলোচনার চেয়ে আর্থিক অসন্তোষের প্রতিধ্বনি বেশি শোনা যায়। তারা বলেন, ‘বেতন কম, ভাতা কম, মূল্যস্ফীতি বেড়েছে’Ñ এই কথাগুলো সত্য, কিন্তু আংশিক সত্য। কারণ শিক্ষকতার পেশা কখনো কেবল অর্থের হিসাবের ওপর দাঁড়ায় না; এটি দাঁড়ায় মনন, ত্যাগ, দায়িত্ব ও নৈতিকতার ওপর। যেদিন শিক্ষকতা কেবল বেতনের অঙ্কে পরিণত হয়, সেদিন থেকেই শিক্ষার আত্মা নিঃশেষ হতে শুরু করে। আর সেই নিঃশেষিত আত্মাই আজকের শিক্ষক আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতা।
আরেকটি বাস্তব দিক হচ্ছে কর্মদিবসের সীমাবদ্ধতা। বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাবর্ষের ৩৬৫ দিনের মধ্যে কার্যত প্রায় ১৮০ দিনই পাঠদান হয়। বাকিটা কখনো পরীক্ষা, কখনো প্রশাসনিক সভা, কখনো ধর্মীয় বা সরকারি ছুটি। অর্থাৎ, একজন শিক্ষক কার্যত বছরে অর্ধেক সময় শিক্ষাদান করেন, অথচ দাবি করেন পূর্ণকালীন ভাতার কাঠামো। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রশাসনিক বা পুলিশ বিভাগে কর্মরত কেউ এত কম কর্মদিবসে পূর্ণ বেতন পাওয়ার কল্পনাও করতে পারেন না। অথচ শিক্ষা বিভাগে এটি এক প্রকার ‘প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মে’ পরিণত হয়েছে। প্রশ্ন উঠতেই পারেÑযেখানে কাজের পরিমাণ সীমিত, সেখানে বেতন বৃদ্ধির নৈতিক দাবি কতটা সঙ্গত?
আরও একটি বড় সমস্যা হলো ফলাফলভিত্তিক মূল্যায়নের ভ্রান্ত ধারণা। আমাদের দেশে শিক্ষকের কর্মদক্ষতা মাপা হয় শিক্ষার্থীর পাসের হার দিয়ে। যত বেশি ছাত্র পাস করে, তত বেশি ‘সফল’ বলা হয় শিক্ষককে। কিন্তু পাসের হার মানেই মানসম্মত শিক্ষা নয়। বরং অনেক সময়ই এই পাসের হার প্রশাসনিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়Ñবিদ্যালয়ের সম্মান বাঁচানোর জন্য, অথবা শিক্ষা কর্মকর্তার নির্দেশ পালনের জন্য। ফলে প্রকৃত শিক্ষাদান কোথাও হারিয়ে যায়, আর শেখার গভীরতা পরিণত হয় কাগজের পরিসংখ্যানে। এই বিকৃত মূল্যায়ন ব্যবস্থার ফলে শিক্ষকরা শিক্ষার মানোন্নয়নের পরিবর্তে ‘পাসের হার’ বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। এতে জ্ঞানচর্চা নয়, বরং সংখ্যা-নির্ভর সাফল্যের এক মায়াবৃত্ত সৃষ্টি হয়েছে। তাই প্রস্তাব করা যায়Ñশিক্ষকের বেতন বা সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করা উচিত শিক্ষার্থীদের শেখার প্রকৃত মান, সৃজনশীল দক্ষতা, আর মানবিক চেতনার উন্নতির ভিত্তিতে, পাসের হার নয়।
নিজ এলাকায় চাকরি করার সুবিধা থেকে জন্ম নিয়েছে আরেকটি গুরুতর সমস্যাÑস্থানীয় প্রভাব ও পক্ষপাতের সংস্কৃতি। শিক্ষক যেহেতু স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী, তিনি প্রায়ই সামাজিক বা রাজনৈতিক চাপে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। অনেক সময় দেখা যায়, তিনি ছাত্র ফেল করাতে পারেন না কারণ সে তার আত্মীয়ের সন্তান, কিংবা সে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির ভাতিজা। আবার অনেক সময় বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়েও তিনি সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে নরম হয়ে যান। ফলে বিদ্যালয় হয়ে ওঠে অনানুষ্ঠানিক সামাজিক রাজনীতির কেন্দ্র। শিক্ষকতার মতো এক পবিত্র পেশা এভাবে পরিণত হয় প্রভাব ও পক্ষপাতের সামাজিক নেটওয়ার্কে।
রাষ্ট্র যদি সত্যিই শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনতে চায়, তাহলে প্রথম কাজ হওয়া উচিতÑ শিক্ষকদের স্থানীয় চাকরির এই প্রথা বাতিল করা। তাদেরও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মতো বদলির আওতায় আনতে হবে। একজন শিক্ষক যদি জীবনের বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করেন, তবে তার অভিজ্ঞতা বাড়বে, সামাজিক প্রভাব হ্রাস পাবে, এবং তিনি শিক্ষাকে পেশা হিসেবে নয়, দায়িত্ব হিসেবে উপলব্ধি করবেন। এর মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশা মুক্ত হবে স্থানীয় প্রভাবের ছায়া থেকে, যা বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার নীরব পঙ্গুতার অন্যতম কারণ।
এখন আসি আন্দোলনের নৈতিকতায়। শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রেখে আন্দোলন করা নিজেই এক প্রকার আত্মবিরোধী কাজ। শিক্ষক যখন রাস্তায় অবস্থান নেন, তখন তার ছাত্র শ্রেণিকক্ষে অপেক্ষা করে। সেই ছাত্রের সময় নষ্ট হয়, শিক্ষার ধারাবাহিকতা ভেঙে যায়, অভিভাবকরা অনিশ্চয়তায় ভোগেন। অথচ এই আন্দোলনের দাবিগুলো কখনো শিক্ষার্থীর মানোন্নয়নের জন্য নয়; সব দাবি কেন্দ্র করে নিজের বেতন, নিজের ভাতা, নিজের সুবিধা। এটি এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিক আন্দোলন, যা সমাজে শিক্ষকের নৈতিক অবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কারণ একজন শিক্ষক জাতির নৈতিক পথপ্রদর্শক, তিনি যখন নিজের সুবিধার জন্য ছাত্রকে বলি দেন, তখন তার শিক্ষকতা পেশার মর্যাদা নিজ হাতেই খর্ব করেন।
আজ সমাজে শিক্ষক মর্যাদার সংকট বাড়ছে, কিন্তু সেই সংকটের মূল কারণ অন্য কেউ নয়Ñ শিক্ষকরাই। তারা সমাজের কাছে মর্যাদা চেয়ে নিচ্ছেন, কিন্তু সেই মর্যাদা আদায়ের শর্তগুলো পূরণ করছেন না। মর্যাদা দেওয়া হয় না, অর্জন করতে হয়। আর সেই অর্জনের পথে থাকতে হয় আত্মনিয়োগ, ত্যাগ, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার। যখন শিক্ষক ক্লাসে সময় দেন না, দায়িত্বে গাফিলতি করেন, ছাত্রের মানসিক গঠন নিয়ে উদাসীন থাকেন, তখন সমাজ তাকে কেবল বেতনভোগী হিসেবে দেখে, গুরু হিসেবে নয়। এ বাস্তবতাই শিক্ষক আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়।
আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় জরুরি হলো আত্মসমালোচনা। রাষ্ট্রের দায়িত্ব শিক্ষকের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কিন্তু শিক্ষকের দায়িত্ব শিক্ষার মান উন্নয়ন করা। দুয়ের ভারসাম্যই উন্নত জাতির পূর্বশর্ত। কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে এই ভারসাম্য সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। সরকার বারবার বেতন বাড়িয়েছে, ভাতা বৃদ্ধি করেছে, বিভিন্ন সুবিধা দিয়েছে, কিন্তু শিক্ষার মান তাতে উন্নত হয়নি। কারণ এই বৃদ্ধির সঙ্গে কোনো ‘দায়বদ্ধতা কাঠামো’জুড়ে দেওয়া হয়নি। একদিকে আর্থিক সুযোগ বাড়ছে, অন্যদিকে নৈতিক দায়বদ্ধতা কমছেÑ এটি এক প্রকার অসামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন, যা দীর্ঘমেয়াদে বিপজ্জনক।
এখন প্রশ্নÑ এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী? প্রথমত, শিক্ষকদের নিয়োগ, বদলি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ সংস্কার করতে হবে। শিক্ষককে নিজের এলাকায় নয়, দেশের যে কোনো প্রান্তে পাঠানো যেতে হবে, যেন তিনি স্থানীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয় বছরের কাঠামো পুনর্গঠন করতে হবেÑ কমপক্ষে ২৫০ কার্যদিবস নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ছাত্রদের শেখার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। তৃতীয়ত, শিক্ষকদের মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবেÑ পাসের হার নয়, শেখার মান, উপস্থিতি, ক্লাস পারফরম্যান্স, এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর ভিত্তি করে প্রণোদনা দিতে হবে। চতুর্থত, শিক্ষকদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ ও নৈতিকতা চর্চার কোর্স থাকতে হবে, যাতে তারা পেশাকে পেশা হিসেবে নয়, এক ধরনের নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন।
একটি সমাজ তখনই উন্নত হয়, যখন তার শিক্ষক শ্রেণি আত্মসমালোচনায় সক্ষম হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, আমাদের শিক্ষকেরা এখন আত্মসমালোচনার বদলে আত্মঅহমে বিশ্বাসী। তারা দাবি করেনÑ ‘আমরাই জাতি গড়ি’Ñ কিন্তু প্রশ্ন করলে দেখা যায়, সেই জাতি গড়ার কাজের মধ্যে তাদের সময় ব্যয় কতটুকু? শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে তারা কতটা অবদান রাখছেন? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি তারা নিজের কাছে সৎভাবে দেন, তবে আন্দোলনের পথ বদলে যাবে।
আন্দোলন প্রয়োজন, কিন্তু তার লক্ষ্য হতে হবে শিক্ষা সংস্কার, সুবিধা নয়। যদি শিক্ষকেরা সত্যিই জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাতা হতে চান, তবে তাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত আত্মশুদ্ধি। নিজের দায়িত্ব বুঝে নেওয়া, নিজের সীমাবদ্ধতা মেনে নেওয়া, এবং নিজের পেশাকে নতুন করে মূল্যায়ন করা। শিক্ষক যখন নিজের মধ্যের অজুহাতগুলো দূর করবেন, তখনই তিনি সমাজে সত্যিকারের আলোর বাহক হয়ে উঠবেন।
আজকের শিক্ষক আন্দোলন সেই আত্মসমালোচনার বিপরীতে দাঁড়িয়েছে। এটি শিক্ষকতার নৈতিক আত্মার বিরুদ্ধে এক নীরব বিদ্রোহ। তাই আমি বলিÑ শিক্ষক আন্দোলনের উল্টো পথে আমি। আমি সেই পথে আছি যেখানে শিক্ষকতার পুনর্জাগরণ সম্ভবÑ যেখানে দাবিপত্রের জায়গায় দায়িত্ববোধ, ভাতার জায়গায় মূল্যবোধ, আর আন্দোলনের জায়গায় আদর্শ ফিরে আসবে। আমি সেই শিক্ষকের পক্ষে, যিনি নিজের ক্লাসে থেকেও জাতিকে আলো দেন, কিন্তু আমি তার বিপক্ষে, যিনি ক্লাস বন্ধ রেখে স্লোগান তোলেন। আমাদের সমাজে শিক্ষা তখনই পুনরুজ্জীবিত হবে, যখন শিক্ষকরা বুঝবেনÑ আলোর কাজ কখনো ছায়ায় হয় না। নিজেদের স্বার্থের অন্ধকার থেকে তারা যত দ্রুত বেরিয়ে আসবেন, জাতির ভবিষ্যৎ তত উজ্জ্বল হবে। শিক্ষকের দাবি হোক দায়িত্বের প্রতিশ্রুতি, সুবিধার নয়। আর আন্দোলনের চূড়ান্ত স্লোগান হোকÑ‘বেতন নয়, বোধ চাই; সুবিধা নয়, সচেতনতা চাই।’ কারণ শিক্ষকতা কোনো চাকরি নয়Ñ এটি এক পবিত্র প্রতিশ্রুতি। যে শিক্ষক তা ভুলে যায়, সে জাতিকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়। আর যে শিক্ষক তা স্মরণে রাখে, সে নিজের আলোয় পুরো জাতিকে পথ দেখায়। আর সেই কারণেই আমি আজও উচ্চারণ করিÑ শিক্ষক আন্দোলনের উল্টো পথে আমি, কারণ আমি চাই শিক্ষক জাগুক, আন্দোলন নয়Ñ আত্মবোধের আলোয়।
রাফায়েল আহমেদ শামীম, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কলাম লেখক



 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন



-20251017034015.webp)
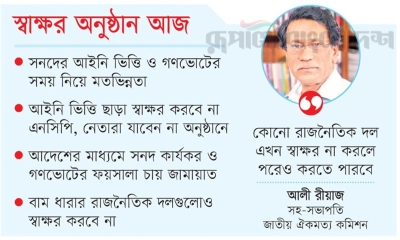


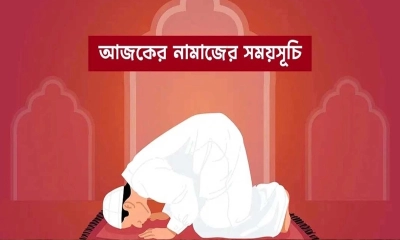
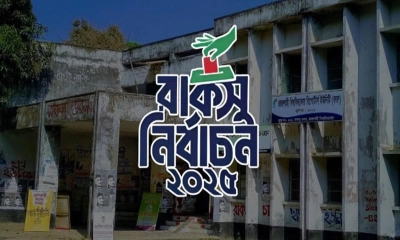

-20251017033729.webp)
-20251017033509.webp)
-20251017033412.webp)
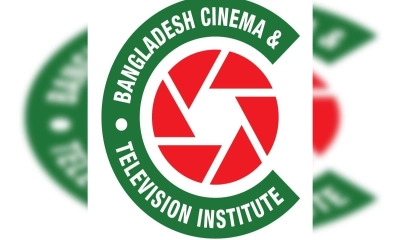




-20251011202107.webp)




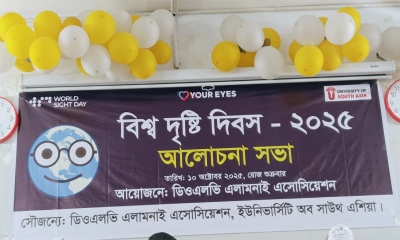



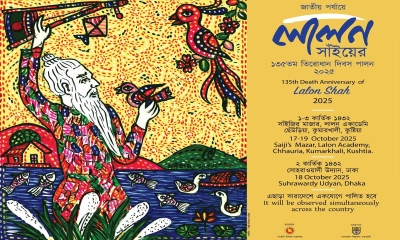
আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন