মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকা- কেবল একটি দুর্ঘটনা নয়, এটি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার নগ্ন প্রতিচ্ছবি, প্রশাসনিক কাঠামোর জীর্ণতা ও সমাজের নৈতিক সংকটের এক কঠিন দলিল, যেখানে আগুনে পুড়ে মারা গেছে কেবল মানুষ নয়Ñদগ্ধ হয়েছে মানবিকতা, নীতি, জবাবদিহিতা ও রাষ্ট্র নামের একটি কাঠামোর অদৃশ্য অথচ গভীর ব্যর্থতা। এই আগুনের ধোঁয়া শুধু ভবনের ভেতরে ছড়িয়ে পড়েনি, ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের সমষ্টিগত বিবেকের ওপর, আমাদের রাষ্ট্রের মানচিত্রে এক কালো দাগ হয়ে, যেখানে শ্রমিকের প্রাণকে দেখা হয় পরিসংখ্যানের দৃষ্টিতে, যেখানে মৃত্যুর খবর শিরোনাম হয় কয়েকদিনের জন্য, তারপর মুছে যায় প্রশাসনিক কাগজের কোণায়। এই অগ্নিকা-ের পেছনে লুকিয়ে আছে বহু বছরের একটি পচে যাওয়া শাসন কাঠামো, যেখানে নিয়ম-কানুন আছে কাগজে, তদারকি আছে প্রতিবেদনে, আর দায়বদ্ধতা আছে কেবল ভাষণে, বাস্তবে যার অস্তিত্ব প্রায় শূন্যের কোঠায়।
একটি চারতলা ভবন, যেখানে ছিল রাসায়নিক গুদাম, সেখানে শ্রমিকেরা দিনরাত কাজ করছিল অথচ ছিল না অগ্নিনিরাপত্তার ন্যূনতম কোনো ব্যবস্থা, ছাদের দরজায় ছিল তালা, বের হওয়ার পথ বন্ধ, ফায়ার এক্সিট ছিল কেবল কল্পনায়, আর অনুমোদনের কাগজ ছিল হয়তো কারো ড্রয়ারেÑএই সবকিছু আসলে একটি সিস্টেমেটিক অবহেলার প্রতীক, যা একদিন না একদিন অগ্নিকু-ে পরিণত হবেই, এবং সেটাই হলো। এই রাষ্ট্রে প্রতিটি বড় দুর্ঘটনার পর এক অভিন্ন নাটক চলেÑদুঃখ প্রকাশ, তদন্ত কমিটি, প্রশাসনিক সভা, প্রতিশ্রুতির ঝাঁপি, মিডিয়ার হেডলাইন, আর তারপর নীরবতা। কিন্তু আগুন কখনো নীরব হয় না; তার তাপ থেকে যায়, জ্বলতে থাকে অঘোষিত প্রশ্নের মতোÑএই রাষ্ট্রের দায় কে নেবে? এই সমাজের বিবেক কে জাগাবে? এই প্রশাসনের তন্দ্রা কে ভাঙবে?
রাষ্ট্র যে কেবল প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে, তা আর আড়াল করার কিছু নেই। আগুন লাগার পর ফায়ার সার্ভিস আসে, পুলিশ আসে, সেনাবাহিনী আসে, মন্ত্রী আসে, ক্যামেরা আসেÑকিন্তু আগুন লাগার আগেই যে কেউ আসেনি সেটাই মূল সমস্যা। প্রতিরোধমূলক সংস্কৃতি এই রাষ্ট্রে নেই, আছে কেবল পরবর্তী ধাপের প্রতিক্রিয়া। যেন রাষ্ট্র কেবল মৃত দেহ দেখলে জেগে ওঠে, কিন্তু জীবিত মানুষ বাঁচানোর কোনো দায়িত্ব তার নেই। রাসায়নিক গুদাম যদি অনুমোদিত হতো, যদি শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রোটোকল থাকত, যদি ফায়ার এক্সিট খোলা থাকত, যদি ছাদের দরজায় তালা না থাকত, তাহলে হয়তো আজ এতগুলো প্রাণ হারাতে হতো না। কিন্তু ‘যদি’ শব্দটি বাংলাদেশের প্রশাসনিক বাস্তবতায় এক নিষ্ঠুর বিদ্রুপে পরিণত হয়েছে। কারণ এই ‘যদি’ শব্দের পেছনে লুকিয়ে আছে দুর্নীতি, ঘুষ, রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়া, ক্ষমতার দম্ভ এবং শ্রমিকের জীবনের অবমূল্যায়ন। এখানে শ্রমিককে দেখা হয় উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে, মানুষ হিসেবে নয়। একজন শ্রমিক বাঁচে কারখানার দেয়ালের ভেতরে, মরে পরিসংখ্যানের পাতায়।
এই রাষ্ট্রে প্রতিটি বড় দুর্ঘটনা একই ধাঁচে ঘটে, কারণ রাষ্ট্রীয় কাঠামোটি এমনভাবে গড়ে উঠেছে যাতে অব্যবস্থাপনা স্থায়ী হয় এবং জবাবদিহিতা স্থগিত থাকে। দুর্যোগের পর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়, প্রতিবেদনে কিছু সুপারিশ লেখা হয়, কয়েকজন নিম্নপদস্থ কর্মচারীর ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু মূল নীতিনির্ধারক বা মূল দায়ী গোষ্ঠী অক্ষত থেকে যায়। এই চক্র এতটাই শক্তিশালী যে শ্রমিকের আর্তনাদও সেটিকে ভাঙতে পারে না। আমরা যখন অগ্নিকা-ের ভিডিও দেখি, তখন দেখি শ্রমিকেরা ছাদের তালাবদ্ধ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, বের হতে পারছে না, বিষাক্ত ধোঁয়ায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছে। এটি কেবল একটি দুর্ঘটনার দৃশ্য নয়, এটি এই রাষ্ট্রের এক গভীর প্রতীকী চিত্রÑযেখানে দরজা খোলা থাকে ক্ষমতাবানদের জন্য, আর দরজা বন্ধ থাকে শ্রমিকদের জন্য, যেখানে মৃত্যু অবধারিত, আর ন্যায়বিচার অনিশ্চিত।
রাষ্ট্রের নৈতিক দায় এখানে নিছক একটি ধারণাগত বিষয় নয়; এটি একটি বাস্তব দায়। রাষ্ট্র মানে কেবল সরকার নয়, রাষ্ট্র মানে প্রশাসনিক কাঠামো, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, স্থানীয় সরকার, তদারকি সংস্থা, নীতি নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠানÑসবাই মিলে এক বৃহৎ দায়িত্বশীল সত্তা। কিন্তু এই সত্তা কার্যত নিষ্ক্রিয়, অকার্যকর, উদাসীন এবং প্রায়শই দুর্নীতিগ্রস্ত। এই অগ্নিকা-ের পেছনে যে রাসায়নিক গুদাম ছিল তা অনুমোদনবিহীন, অথচ বছরের পর বছর চালু ছিলÑএটা কি কেবল গুদাম মালিকের অপরাধ, নাকি প্রশাসনিক তদারকির চরম ব্যর্থতা? নিয়মিত পরিদর্শন কোথায় ছিল? স্থানীয় প্রশাসন কি ঘুমিয়ে ছিল? নাকি ঘুষের বিনিময়ে চোখ বন্ধ করে রেখেছিল? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কোনো তদন্ত কমিটি কখনো দেয় না, আর সেখানেই লুকিয়ে আছে রাষ্ট্রীয় উদাসীনতার কেন্দ্র।
শ্রমিক নিরাপত্তা এই দেশে কেবল কাগজে লেখা একটি শব্দবন্ধ। শ্রম আইন আছে, কিন্তু তার প্রয়োগ নেই। ফায়ার সেফটি প্রটোকল আছে, কিন্তু তা মানার সংস্কৃতি নেই। অধিকাংশ শিল্প কারখানায় জরুরি বহির্গমন পথ নেই, থাকলেও তালাবদ্ধ থাকে। শ্রমিকেরা জানে না কীভাবে বিপদে বাঁচতে হয়, কারণ তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। তারা জানে কেবল কীভাবে দ্রুত উৎপাদন বাড়াতে হয়। এই অমানবিক বাস্তবতায় শ্রমিক কেবল একটি সংখ্যা, একটি শ্রমঘণ্টা, একটি প্রোডাক্টিভ ইউনিট। আর রাষ্ট্রও সেটিকে মেনে নিয়েছে, কারণ রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের কোনো কণ্ঠ নেই, আছে কেবল মালিক ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের কণ্ঠ। তাই আগুনে পুড়ে ১৬ জন শ্রমিক মারা গেলে রাষ্ট্র দুঃখ প্রকাশ করে, কিন্তু ব্যবস্থাপনা বদলায় না।
এই দুর্ঘটনা একটি বড় সত্যকে সামনে নিয়ে এসেছে এই রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো আসলে অদক্ষ এবং নৈতিকভাবে পঙ্গু। এখানে দুর্যোগ প্রতিরোধ নয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হয়; এখানকার নীতি প্রণয়ন হয় শোকবার্তার পর, প্রতিরোধমূলক পরিকল্পনা নয়। আর জনগণÑবিশেষ করে শ্রমজীবী জনগণÑএখানে কেবল ভিকটিম, কখনো সিদ্ধান্তগ্রহণকারী নয়। রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কেবল মৃত্যুর পরে শুরু হয়, জীবিত অবস্থায় নয়। অথচ একটি সভ্য রাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণিই শিল্পায়নের ভিত্তি, অর্থনীতির প্রাণশক্তি। কিন্তু বাংলাদেশে এই শ্রেণিকে দেখা হয় তুচ্ছ চোখে, তাদের রক্ত ও ঘাম দিয়ে শিল্প বাণিজ্যের চাকা ঘোরে, অথচ নিরাপত্তার ন্যূনতম নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না।
নৈতিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাষ্ট্রের আইন কেবল আইন বইয়ে থেকে গেলে তা অর্থহীন। নৈতিক রাষ্ট্র মানে এমন একটি কাঠামো যেখানে জীবনের মূল্য ক্ষমতার চেয়ে বড়। কিন্তু আজ আমরা যে রাষ্ট্রে বাস করছি, সেখানে জীবন নয়, ক্ষমতাই বড়; শ্রমিক নয়, মালিকই গুরুত্বপূর্ণ; ন্যায় নয়, দায় এড়ানোই নিয়ম। এই অগ্নিকা-ের পর যেমন কিছু দিন হইচই হবে, মিডিয়া শিরোনাম করবে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে পড়বে, তারপর সবকিছু থেমে যাবে, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ধুলায় ঢেকে যাবে, আর ঠিক সেই একই জায়গায় আবার নতুন গুদাম উঠবে, নতুন অগ্নিকা-ের বীজ বপন হবে। এই চক্র ভাঙবে কে? রাষ্ট্র নিজে কি কখনো তার দায় স্বীকার করবে?
রাষ্ট্রের এই উদাসীনতা আসলে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতির ফল। এই সংস্কৃতি হলো দায় এড়িয়ে যাওয়া, তদারকিকে প্রহসনে পরিণত করা এবং জবাবদিহিতাকে ক্ষমতার বাইরে রেখে দেওয়া। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জানেন কোথায় কোথায় অনুমোদন ছাড়া গুদাম চলছে, কিন্তু রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় কেউ কিছু বলতে পারে না। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা জানে কোন স্থাপনাগুলো ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু তারা অভিযান চালায় না। কারণ এই রাষ্ট্রে আইন সবার জন্য সমান নয়। শ্রমিকদের জন্য আইন কঠোর, কিন্তু মালিকদের জন্য আইন নমনীয়। এই দ্বৈত কাঠামোই জন্ম দিয়েছে এক ভঙ্গুর রাষ্ট্রিক বাস্তবতা, যেখানে দুর্ঘটনা আসলে অবধারিত।
এই আগুন আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেÑরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এক ভয়াবহ বৈষম্য বিরাজ করছে। একদিকে ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর জন্য সুরক্ষা, প্রটোকল, জরুরি নির্গমন, অ্যালার্ম সিস্টেম, বহির্গমন পরিকল্পনা; অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণির জন্য তালাবদ্ধ ছাদ, রাসায়নিক ধোঁয়া, শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু। এই বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক নয়, এটি নৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য। এটি এমন এক প্রকার শ্রেণি বৈষম্য যা রাষ্ট্রীয় নীতি দ্বারা পুষ্ট হয়, প্রশাসনিক নীরবতায় টিকে থাকে এবং জনগণের অসহায়ত্বে বৈধতা পায়। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে কোনো শক্তিশালী সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে না ওঠা পর্যন্ত শিয়ালবাড়ির মতো অগ্নিকা- আবার ঘটবেইÑশুধু জায়গা আর তারিখ বদলাবে।
এই রাষ্ট্রে অগ্নিকা-ের মতো দুর্ঘটনাগুলোকে আমরা যতবার দেখি, ততবার আমরা একটি সমষ্টিগত অভ্যস্ততার মধ্যে ঢুকে যাই। যেন আগুন লাগা কোনো ব্যতিক্রম নয়, একটি নিয়মিত ঘটনা। এই অভ্যস্ততা আসলে সবচেয়ে ভয়ংকর। কারণ রাষ্ট্র যখন ব্যর্থ হয় আর সমাজ যখন চুপ থাকে, তখন ব্যর্থতাই নিয়মে পরিণত হয়। আমরা তখন আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া শ্রমিকদের মৃত্যু নিয়ে একটি নিরাবেগ পরিসংখ্যান তৈরি করি, মানবিকতার শোককে পরিণত করি তথ্যের সারিতে। কিন্তু এই শ্রমিকেরা কেবল সংখ্যা নয়; তারা জীবিত মানুষ ছিল, তাদের ছিল পরিবার, স্বপ্ন, প্রিয়জন, ছোট্ট সন্তান, বুড়ো মা। রাষ্ট্র তাদের দেখেনি জীবিত অবস্থায়, আর মরে যাওয়ার পরও তারা কেবল খবরের কাগজের হেডলাইন। এখানেই রাষ্ট্রের নৈতিক ব্যর্থতা সবচেয়ে প্রকট। কারণ কোনো রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি তার অর্থনীতি বা অস্ত্রে নয়, বরং সে কতটা তার নাগরিকের জীবনকে মর্যাদা দিতে পারে তার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এখানে জীবন সস্তা, দায়িত্ব লঘু, আর ন্যায়বিচার বিলম্বিত। এই অগ্নিকা-ের বিচারও হয়তো হবে নাÑহলেও তাতে মূল দায়ীরা ধরা পড়বে না। হয়তো কোনো গুদাম মালিক বা ভবন মালিককে সাময়িকভাবে আটক করা হবে, তারপর জামিনে মুক্তি, তারপর মামলা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে। আর এই সময়ে রাষ্ট্র নতুন কোনো দুর্ঘটনার জন্য অপেক্ষা করবে, যেন সেটাই তার কাজ।
একটি রাষ্ট্র তখনই ব্যর্থ হয়, যখন তার মানুষগুলো মরে যাওয়াকে ভাগ্য হিসেবে মেনে নেয়। শিয়ালবাড়ির শ্রমিকেরা মরে গেছে রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার আগুনে, আর আমরা বাকিরা বেঁচে থেকেও এক ধরনের পুড়ে যাওয়া অনুভব করছিÑএই রাষ্ট্রের নীরবতা আমাদের বিবেককেও দগ্ধ করছে। রাষ্ট্র যদি এই নীরবতা ভাঙতে না পারে, যদি শ্রমিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকারে না আনে, যদি জবাবদিহিতার শৃঙ্খল শক্ত না করে, তাহলে এই আগুনের ধারা চলতেই থাকবে। একদিন হয়তো আগুন কেবল একটি গুদামে নয়, পুরো রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরেই জ্বলে উঠবে। এই আগুন কেবল শ্রমিকের মৃত্যু নয়, এটি রাষ্ট্রের নৈতিক মৃত্যুঘণ্টা। আর এই মৃত্যুঘণ্টার শব্দ আমাদের সবার কানেই বাজছেÑপ্রশাসনের, রাজনীতির, সমাজের, নাগরিকের।
এখন প্রশ্ন হলোÑআমরা কি এই শব্দ শুনে জেগে উঠব, নাকি অভ্যস্ত হয়ে যাব এই শব্দে? রাষ্ট্রকে তার মৌলিক দায়িত্বে ফিরে যেতে হবে, কারণ শ্রমিকের জীবন কোনো তুচ্ছ পরিসংখ্যান নয়, এটি একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতি। আর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা মানে কেবল অগ্নিকা- রোধ করা নয়, রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তিকে পুনর্গঠন করা। শিয়ালবাড়ির আগুন সেই আহ্বান আমাদের সামনে ছুড়ে দিয়েছেÑএখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা রাষ্ট্রের।



 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন



-20251207041530.webp)
-20251207041322.webp)


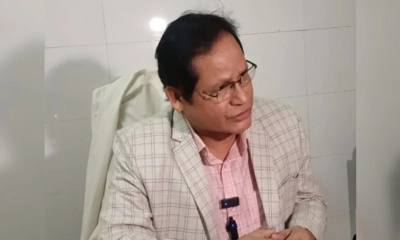
-20251207154913.webp)






-20251207205040.webp)


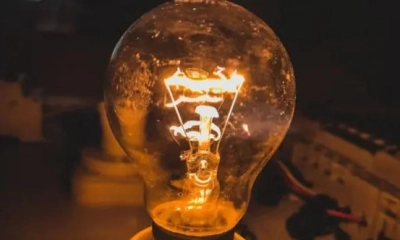






-20251203221210.webp)
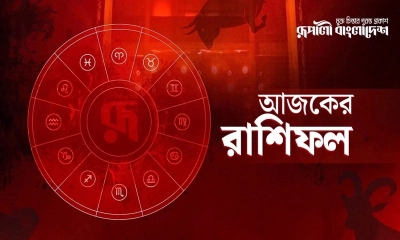









আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন