বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ পূর্বাভাসে রয়েছে এক ধরনের সংযত আতঙ্কের সুর। একসময় মহামারি-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুত্থানের প্রতীক হিসেবে যে দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, এখন সেই অঞ্চলের অগ্রযাত্রা থমকে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। কারণ আবারওÑ সুরক্ষাবাদ। বিশ্বব্যাংক অনুমান করছে, ২০২৬ সালে দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধি ৬.৪ শতাংশ থেকে নেমে ৫.৮ শতাংশে দাঁড়াবে, যার প্রধান কারণ মার্কিন শুল্কবৃদ্ধি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে ওয়াশিংটনের নবজাগরিত বাণিজ্য জাতীয়তাবাদ।
এই সংখ্যাগুলো শুধু অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের গল্প নয়Ñ এগুলো ক্ষমতা ও দুর্বলতার এমন এক বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি, যেখানে ভূরাজনীতির আত্মকেন্দ্রিকতা বিশ্ব অর্থনীতির কাঠামোকেই নড়বড়ে করে তুলছে। যে বৈশ্বিক অর্থনীতি একসময় দক্ষিণ এশিয়ার সস্তা শ্রম ও দ্রুত উৎপাদনের ওপর ভর করে চলত, এখন সেই ব্যবস্থাই তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ব্যাপক শুল্ক আরোপ করেছেÑ ভারতের বেশিরভাগ পণ্যে ৫০ শতাংশ, বাংলাদেশের রপ্তানিতে ২০ শতাংশ, এবং শ্রীলঙ্কার পণ্যে ২০ শতাংশ পর্যন্ত। যুক্তি হিসেবে বলা হচ্ছে, রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করা বা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ধারাবাহিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত রাখার জন্য এসব দেশকে ‘শাস্তি’ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাসে দেখা গেছে, অর্থনৈতিক কূটনীতির এই ভোঁতা অস্ত্র প্রমাণ করেছেÑ যাদের টার্গেট করা হয়, তাদের নয়, বরং নিরপরাধরাই এর সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।
দক্ষিণ এশিয়ার জন্য সময়টা অত্যন্ত কঠিন। মহামারি-পরবর্তী পুনরুদ্ধার ও ২০২২ সালের জ্বালানি সংকট কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই নতুন এক বহিরাগত ধাক্কা এসে পড়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের পোশাক খাত, ভারতের ওষুধ ও অটোমোবাইল শিল্প, এবং শ্রীলঙ্কার তৈরি পোশাক রপ্তানি এখন এমন এক আঘাতের মুখে, যা কোনো প্রণোদনা দিয়েই সহজে সামাল দেওয়া সম্ভব নয়।
বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের শিল্প খাত মূলত আমদানি করা সুতা, যন্ত্রপাতি ও রঙের ওপর নির্ভরশীল। এসব উপকরণে বাড়তি শুল্ক মানে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, যা রপ্তানি প্রতিযোগিতা কমিয়ে দেবে। লাখ লাখ নারী শ্রমিকের জন্য এর মানে হতে পারেÑ কাজ হারানো, মজুরি হ্রাস, এমনকি কারখানা বন্ধ। এটি এক নির্মম বিদ্রুপÑ যেসব দেশ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বুলি উচ্চারণ করে, তারাই এখন সস্তা পোশাক সরবরাহকারীদের জীবিকা বিপন্ন করছে।
বিশ্ব কেবল এবারই প্রথম সুরক্ষাবাদের ফাঁদে পড়েনি। ১৯৩০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্মুট-হাওলি ট্যারিফ অ্যাক্ট ২০,০০০ পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়িয়ে তৎকালীন মহামন্দাকে আরও গভীরতর করেছিল। তখনকার যুক্তিও ছিল এ সময়ের মতো আমেরিকান চাকরি রক্ষা, অন্যায্য বাণিজ্যকারীদের শাস্তি। কিন্তু ফল হয়েছিল ভয়াবহ: দুই বছরের মধ্যে বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রায় ৭০ শতাংশ কমে যায়, যার ফলে অর্থনৈতিক মন্দা আরও তীব্র হয় এবং বিশ্বজুড়ে চরমপন্থা বেড়ে যায়।
আজকের অর্থনীতি অনেক জটিল হলেও ইতিহাস আমাদের সতর্ক করেÑ বাণিজ্যপ্রাচীর কখনোই স্থিতি আনে না, বরং প্রতিশোধ, বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তা ডেকে আনে। বর্তমান পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক কারণ এটি ঘটছে এমন এক অস্থির ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেÑ যেখানে ইউক্রেন যুদ্ধ, মার্কিন-চীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার প্রতি আস্থাহীনতা একই সঙ্গে কাজ করছে।
দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে স্থিতিশীল অর্থনীতি হিসেবে ভারত এখনো এগিয়ে। বৃহৎ অভ্যন্তরীণ বাজার, শক্তিশালী ভোক্তা ব্যয় ও ডিজিটাল পরিবর্তনের কারণে দেশটি এখনো বিশ্বের দ্রুততম প্রবৃদ্ধিশীল বড় অর্থনীতি হিসেবে টিকে আছে। তবুও, এর প্রান্তে ফাটল ধরছে।
মার্কিন শুল্ক নীতি ভারতীয় রপ্তানিতে বড় ধাক্কা দিয়েছে, পাশাপাশি রুশ তেল আমদানিতে ২৫ শতাংশ শুল্ক ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিকস ও ফার্মাসিউটিক্যালÑ বিশ্বের সরবরাহ চেইনের তিনটি খাতই এখন বিঘিœত হচ্ছে। ফলে ২০২৬-২৭ সালের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ৬.৫ শতাংশ থেকে কমে ৬.৩ শতাংশে নেমে গেছে।
ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন দাবি করেছেন, সংস্কার, ডিজিটাল রূপান্তর ও সরকারি বিনিয়োগের ওপর ভর করে ভারত ‘ধাক্কা সামলানোর ক্ষমতা’ রাখে। তার আত্মবিশ্বাসের যুক্তি আছে, কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য যে সহনশীলতারও সীমারেখা আছে। ভারতের সামান্য মন্থরতাও গোটা উপমহাদেশে ঢেউ তুলবে। কারণ দক্ষিণ এশিয়ার মোট জিডিপির ৭৫ শতাংশ আসে ভারত থেকে; সেখানে ধীরগতি মানে বাণিজ্য হ্রাস ও বিনিয়োগ স্থবিরতা।
বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে এক অর্থনৈতিক সাফল্যের কাহিনি যা রেমিট্যান্স, নারীশ্রমিক অংশগ্রহণ এবং রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের উপর দাঁড়িয়ে। কিন্তু এখন সেই মডেলেই চাপ পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিতে শুল্কবৃদ্ধি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাজারকে হুমকির মুখে ফেলেছে। তাই এখন দরকার উচ্চমূল্য সংযোজিত শিল্পে যেমনÑ ইলেকট্রনিকস, ওষুধ ও চামড়াজাত পণ্য ইত্যাদি এর দ্রুত বিকল্প বাজারের সৃষ্টি করা।
বিশ্বব্যাংক সতর্ক করেছে, সরবরাহ চেইনের আধুনিকায়ন ও লজিস্টিক উন্নয়ন ছাড়া বাংলাদেশ প্রতিযোগী বাজার হারাতে পারে। বাড়তি আমদানি ব্যয় বাণিজ্য ঘাটতি বাড়াবে এবং টাকার মান দুর্বল করবে, যা মুদ্রাস্ফীতি বাড়াবে।
অন্যদিকে, ২০২২ সালের অর্থনৈতিক ধস থেকে সামলে উঠতে না উঠতেই শ্রীলঙ্কা আবারও নতুন চাপে। আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়া ও রপ্তানি আয় কমে যাওয়ায় তাদের রাজস্ব ভারসাম্যকে বিপন্ন করছে। আইএমএফের সহায়তা ও পর্যটন পুনরুদ্ধারের ওপর নির্ভরশীল এই অর্থনীতি সহজেই নড়বড়ে হয়ে পড়তে পারে। যে দেশ এখনো ঘাটতি ও প্রতিবাদের ভূতুড়ে স্মৃতিতে তাড়িত, তাদের জন্য হাজার মাইল দূরে আরোপিত শুল্ক যেন এমন এক ভূমিকম্পের পরাঘাতÑ যার সূত্রপাত তারা কখনো ঘটায়নি।
ভুটান, নেপাল ও মালদ্বীপের জন্য বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট আরও উদ্বেগজনক। রেমিট্যান্স হ্রাস, জলবায়ুজনিত জলবিদ্যুৎ বিঘœতা, ও বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতিÑ সব মিলিয়ে এসব অর্থনীতি আগেই নাজুক। মার্কিন শুল্ক সরাসরি আঘাত না করলেও এটি বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে। এতে বোঝা যায়, আন্তঃনির্ভরশীল বিশ্বের ধাক্কা এক প্রান্তে লাগলেও তার প্রতিধ্বনি দূরতম প্রান্তেও পৌঁছে যায়।
সুরক্ষাবাদ সমস্যার একটি অংশ মাত্র। বিশ্বব্যাংক আরও যেসব চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছে তাহলো বিশ্বব্যাপী মন্দা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি। এগুলোও পরিস্থিতিকে জটিল করছে। জ্বালানি ও খাদ্যের দাম বেড়ে দরিদ্র শ্রেণিকে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে এবং অসমতার ব্যবধান বাড়াচ্ছে। শ্রমবাজারের অস্থিরতা ও জনতাবাদী রাজনীতি সামগ্রিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি আরও বাড়াচ্ছে।
সাধারণ দক্ষিণ এশীয়দের জন্য এসব সামগ্রিক অর্থনীতি মানে-বাজারে দাম বাড়া, চাকরির সুযোগ কমে যাওয়া, ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস। একসময় গর্বের বিষয় ছিল এই অঞ্চলের তরুণ জনসংখ্যা। আজ সেটিই ঝুঁকিতে, প্রবৃদ্ধি না থাকলে এই বেকরত্বের কারণে সহজেই বোঝায় পরিণত হতে পারে।
এটি কেবল অর্থনৈতিক সংকটই নয়, নৈতিক সংকটও। যে দেশ মুক্ত বাজার ও প্রতিযোগিতার নীতিতে দাঁড়িয়ে বৈশ্বিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেই দেশই আজ নিজস্ব স্বার্থকে সর্বোচ্চে স্থান দিচ্ছে। আমেরিকার এই শুল্কনীতি হয়তো মধ্য-পশ্চিমে কয়েক হাজার চাকরি বাঁচাবে, কিন্তু একই সঙ্গে ঢাকা, কলম্বো ও চেন্নাইয়ে লাখো শ্রমিকের জীবিকা কেড়ে নেবে।
দক্ষিণ এশিয়ার নীতিনির্ধারক ও ব্যবসায়ী সমাজের জন্য একটি স্পষ্ট শিক্ষা। কেবল একটি বাজারের ওপর নির্ভরতা, তা যত লাভজনকই হোক না কেন, ভয়াবহ ঝুঁকিপূর্ণ। বাজারের বৈচিত্র্য সৃষ্টি এখন বিলাসিতা নয়, অস্তিত্বের প্রশ্ন। আঞ্চলিক বাণিজ্য জোরদার করা, পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গভীর করা, এবং দেশীয় উৎপাদনে বিনিয়োগ বাড়ানোÑ এসবই এখন জরুরি।
বাংলাদেশের আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি (জঈঊচ) তে সম্ভাব্য অংশগ্রহণ, ভারতের আসিয়ান-কেন্দ্রিক কূটনীতি, এবং শ্রীলঙ্কার পুনরায় বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগে যোগ দেওয়ার চেষ্টাÑ সবই এ অঞ্চলকে ওয়াশিংটনের খামখেয়ালিপনা থেকে কিছুটা সুরক্ষা দিতে পারে।
একই সঙ্গে, যুক্তরাষ্ট্রেরও উচিত তার সুরক্ষাবাদের ভূরাজনৈতিক মূল্য বিবেচনা করা। দ্রুত বর্ধনশীল অংশীদারদের দূরে ঠেলে দিয়ে, তারা কার্যত চীনের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি করছে। চীন ইতোমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিগুলোর জন্য শুল্ক-ছাড় ও নতুন ঋণসুবিধা দিচ্ছে। এটি যেমন কৌশলগত পদক্ষেপ, তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত কূটনীতিও।
বিশ্বব্যাংকের এই সতর্কবার্তা কেবল কিছু পরিসংখ্যান নয়Ñ এটি এক সতর্কতামূলক গল্প, যা দেখিয়ে দেয় বৈশ্বিকীকরণ আজ কতটা ভঙ্গুর। দশকের পর দশক দক্ষিণ এশিয়ার সাফল্য দাঁড়িয়ে ছিল একটি বিশ্বাসের ওপর: মুক্ত বাণিজ্য, দক্ষতা ও উদ্ভাবনই উন্নতির চাবিকাঠি। আজ সেই বিশ্বাসটাই প্রশ্নবিদ্ধ।
যদি ওয়াশিংটন শুল্ককে রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করতে থাকে, তবে ২০২৬ হয়তো শুধু প্রবৃদ্ধির মন্থরতার বছর হবে না, বরং এক সেই যুগের অবসান চিহ্নিত করবে যে যুগে উন্নয়নশীল দেশগুলো বুঝতে পারবে, বিশ্ববাজারও এখন শক্তির রাজনীতিতেই চালিত, ন্যায্যতায় নয়।
ইতিহাস হয়তো একে এমন এক সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করবে, যখন আমেরিকার অন্তর্মুখী নীতি অন্যদের নেতৃত্ব নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। দক্ষিণ এশিয়ার জন্য টিকে থাকার একমাত্র উপায়Ñ পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং এমন এক বিশ্বের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া, যেখানে অর্থনৈতিক দেয়াল উঠছে সেতুর চেয়েও দ্রুত।


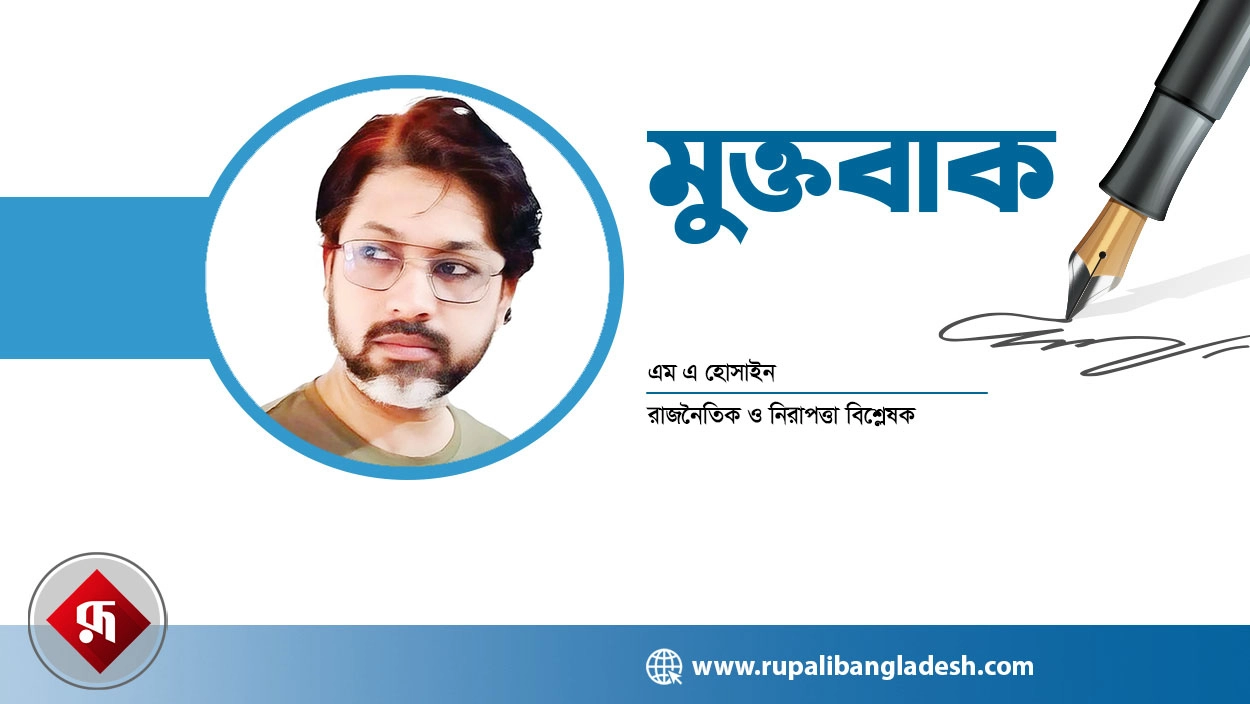
 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন



-20251016024200.webp)
-20251016023952.webp)


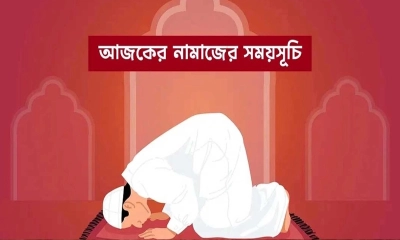



-20251016023824.webp)
-20251016023712.webp)
-20251016023549.webp)
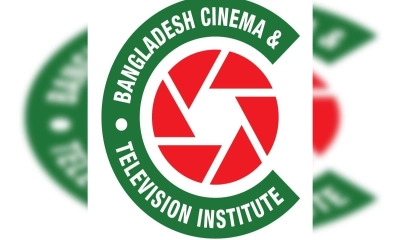



-20251011202107.webp)










আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন