বিশ্বব্যাপী শিল্পায়ন ও আধুনিক অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হচ্ছে শেয়ারবাজার। উন্নত দেশ হোক কিংবা নবীন শিল্পোন্নয়নশীল অর্থনীতি সব ক্ষেত্রেই মূলধন বাজারকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার মাধ্যমে শিল্পায়নের ধারা গতিশীল হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া কিংবা প্রতিবেশী ভারতÑ সব দেশেই শেয়ারবাজারকে অর্থ সংগ্রহ ও শিল্পায়নের প্রধান উৎসে পরিণত করা হয়েছে।
বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়ে গেলেও দেশের শেয়ারবাজার এখনো প্রান্তিক পর্যায়ে অবস্থান করছে। উদ্যোক্তারা মূলধন সংগ্রহের জন্য ব্যাংক ঋণের ওপর নির্ভরশীল থেকে যাচ্ছেন। ফলে শিল্পোন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম তৈরি হচ্ছে না। শেয়ারবাজারের দুর্বলতা শিল্পায়নের পথে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ব্যাংকনির্ভর উদ্যোক্তা ও শেয়ারবাজারের বাইরে কোম্পানিগুলো:
যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মগুলোর পরিদপ্তরের (আরজেএসসি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত দেশে নিবন্ধিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সংখ্যা ৩ হাজার ৭৭৭। অথচ দেশের শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা মাত্র ৩৯৭। অর্থাৎ নিবন্ধিত কোম্পানির মাত্র ১০ শতাংশ শেয়ারবাজারে এসেছে। বাকি ৯০ শতাংশ শেয়ারবাজারের বাইরে থেকে গেছে।
এর বিপরীতে প্রতিবেশী ভারতে ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা ৫ হাজার ছাড়িয়েছে। ভারতের শেয়ারবাজার ইতোমধ্যেই বিশ্বের শীর্ষ পাঁচে জায়গা করে নিয়েছে। ফলে দেশটিতে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। বাংলাদেশে উদ্যোক্তারা যদি ব্যাংক ঋণের বাইরে এসে শেয়ারবাজারকে অর্থ সংগ্রহের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করতেন, তবে শিল্পায়নে বিনিয়োগ আরও বহুমুখী ও স্থায়ী হতো।
দুর্বল আর্থিক ভিত্তি ও জেড গ্রুপের চিত্র
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) তালিকাভুক্ত ৪৩৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৯৭টি কোম্পানি এবং ৩৬টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড রয়েছে। এর মধ্যে ২১৯টি ‘এ’ গ্রুপে, ৮১টি ‘বি’ গ্রুপে এবং ৯৭টি ‘জেড’ গ্রুপে অবস্থান করছে। অর্থাৎ, তালিকাভুক্ত কোম্পানির প্রায় এক-চতুর্থাংশ এমন অবস্থায় আছে যে তারা নিয়মিত লভ্যাংশ দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। কিছু কিছু কোম্পানি বছরের পর বছর বিনিয়োগকারীদের কোনো লভ্যাংশ দেয়নি।
এই চিত্র বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমিয়ে দিচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা মূলধন হারিয়ে দীর্ঘমেয়াদি শিল্পায়নে অংশ নেওয়ার আগ্রহ হারাচ্ছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল কোম্পানিগুলো বাজারে এসে শুধুই সাধারণ বিনিয়োগকারীর অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে।
আইপিও খরা নতুন রক্তের অভাব
প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (আইপিও) শেয়ারবাজারে নতুন কোম্পানি ও বিনিয়োগের ‘রক্তসঞ্চালন’ হিসেবে বিবেচিত হয়। অথচ ২০২৪ সালের জুন থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানা ১৫ মাসে কোনো কোম্পানি নতুন আইপিও আনতে পারেনি।
অতীতে প্রতি বছরই গড়ে ১০টির বেশি প্রতিষ্ঠান বাজারে আসত। যেমনÑ ২০১০ সালে ১৮টি, ২০১৪ সালে ২০টি, ২০২১ সালে ১৫টি কোম্পানি আইপিওর মাধ্যমে বাজারে প্রবেশ করেছিল। সেই তুলনায় বর্তমান স্থবিরতা শেয়ারবাজারের গভীর সংকটের প্রতীক। নতুন কোম্পানি না আসায় বাজারে বৈচিত্র্য তৈরি হচ্ছে না, শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নও সীমিত হয়ে পড়ছে।
নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিতর্কিত সিদ্ধান্ত
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) বাজার নিয়ন্ত্রণে একাধিক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত হলো ২০২২ সালের জুলাইয়ে আরোপিত ‘ফ্লোর প্রাইস’। শেয়ারদর পতন ঠেকাতে নির্দিষ্ট দামে শেয়ারের লেনদেন বাধ্যতামূলক করার এই সিদ্ধান্তে বাজারে লেনদেন কার্যত অচল হয়ে পড়ে।
ফ্লোর প্রাইস কার্যকর হওয়ার আগে যেখানে বাজারে দৈনিক লেনদেন হতো দুই হাজার কোটি টাকার বেশি, সেখানে তা নেমে আসে ২০০ কোটি টাকার ঘরে। ফ্লোর প্রাইস তুলে নেওয়ার পর বাজারে ব্যাপক দরপতন ঘটে। অধিকাংশ বিনিয়োগকারী মূলধনের ৬০-৭০ শতাংশ পর্যন্ত হারান।
রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিনিয়োগকারীর আস্থাহীনতা
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর শেয়ারবাজারে কিছু সংস্কার আনা হলেও বিনিয়োগকারীর আস্থা ফেরেনি। বাজার সূচকের ওঠানামা আস্থার ঘাটতিকে স্পষ্ট করে। ৩১ আগস্ট ডিএসইএক্স সূচক ছিল ৫ হাজার ৫৯৪ পয়েন্ট। সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ তা নেমে আসে ৫ হাজার ৪১৫ পয়েন্টে। একই সময়ে বাজার মূলধন কমে যায় দুই হাজার কোটি টাকার বেশি।
অর্থনীতিবিদদের মতে, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দীর্ঘমেয়াদি নীতির অনিশ্চয়তা বিনিয়োগকারীদের শেয়ারবাজার থেকে দূরে রাখছে।
বিদেশি ও প্রবাসী বিনিয়োগকারীর সরে যাওয়া
বিদেশি ও প্রবাসী বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের শেয়ারবাজার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে তাদের নামে বিও হিসাব ছিল ৫৫ হাজার ৫১২টি, যা ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ কমে দাঁড়িয়েছে ৪৩ হাজার ৮০১টিতে। অর্থাৎ প্রায় ১২ হাজার বিও হিসাব বন্ধ হয়ে গেছে।
যদিও সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশি ও প্রবাসী বিনিয়োগকারীর বিও হিসাব সামান্য বেড়েছে, কিন্তু এর আগে দীর্ঘ সময় ধরে তারা বাজার ছেড়ে যাচ্ছিলেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, সুশাসনের অভাব, স্বচ্ছতার ঘাটতি ও অনিশ্চয়তা এ খাত থেকে বিদেশিদের সরিয়ে দিয়েছে।
স্থানীয় বিনিয়োগকারীর ক্ষতি
২০১৯ সালের জুনে যেখানে স্থানীয় বিনিয়োগকারীর বিও হিসাব ছিল ২৮ লাখ ৪৫ হাজার ২৬টি, সেখানে বর্তমানে তা কমে ১৬ লাখ ৫২ হাজার ২২৭টিতে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ছয় বছরে প্রায় অর্ধেক বিনিয়োগকারী শেয়ারবাজার ছেড়েছেন।
এই আস্থাহীনতার কারণে উদ্যোক্তারা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের জন্য বাজারকে ব্যবহার করতে পারছেন না, শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনও সীমিত হয়ে পড়ছে।
ব্যাংক শেয়ার থেকে আস্থা হারানো
একসময় ব্যাংক খাতের শেয়ারকে শেয়ারবাজারের প্রাণ বলা হতো। কিন্তু বর্তমানে তালিকাভুক্ত ৩৬টি ব্যাংকের মধ্যে ১৭টির শেয়ারের দাম অভিহিত মূল্যের নিচে এবং সাতটির শেয়ার ৫ টাকারও নিচে লেনদেন হচ্ছে। ব্যাংক খাতের অনিয়ম, খেলাপি ঋণ ও স্বচ্ছতার অভাব এ খাতের শেয়ারকে বিনিয়োগকারীদের কাছে অগ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।
মিউচ্যুয়াল ফান্ডে দীর্ঘমেয়াদি সংকট
মিউচ্যুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারীদের জন্য নিরাপদ ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত হলেও বাংলাদেশে এ খাতও ধুঁকছে। বর্তমানে তালিকাভুক্ত ৩৬টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মধ্যে ৩৩টির শেয়ারের দাম ফেস ভ্যালুর নিচে এবং ২০টির দাম ৫ টাকারও নিচে। ফলে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়েছেন।
শিল্পায়নের পথে শেয়ারবাজারের সীমাবদ্ধতা
বিশ্বের সফল অর্থনীতিগুলো শক্তিশালী শেয়ারবাজারের মাধ্যমে শিল্পায়নের ভিত্তি তৈরি করেছে। দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান কিংবা মালয়েশিয়া পুঁজিবাজারকে কার্যকর করে শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হয়েছে। অথচ বাংলাদেশে ব্যাংকনির্ভর অর্থ সংগ্রহ উদ্যোক্তাদের সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। এতে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ ব্যাহত হচ্ছে, শিল্প খাতের প্রসার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
অর্থনীতিবিদরা বলছেন, শেয়ারবাজারকে গতিশীল করা ছাড়া বাংলাদেশের শিল্পায়নের যাত্রা টেকসই হবে না। স্বচ্ছতা, সুশাসন, নিয়মিত আইপিও, আর্থিকভাবে শক্তিশালী কোম্পানি তালিকাভুক্ত করা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার আস্থা অর্জনÑ এই কয়েকটি পদক্ষেপ ছাড়া কোনো পরিবর্তন আসবে না।
অর্থনীতিবিদ ও বাজার বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিএসইসি কর্তৃক গঠিত পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের সদস্য মো. আল-আমিন বলেছেন, বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সাধারণ বিনিয়োগকারীর মতোই ব্যবহার করা হয়। অথচ রাষ্ট্রীয়ভাবে পুঁজিবাজারকে নেগলেক্ট করে রাখা হয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সক্রিয়ভাবে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করলেও বাংলাদেশে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা (আমলা) নিজেদের অবস্থান ছাড়তে চান না। এতে পুঁজিবাজারে নেগলেকশন চলছে এবং তারা এখান থেকে ব্যক্তিগত সুবিধা নিচ্ছেন। ফলে শিল্পায়নে পুঁজিবাজারের কোনো ভূমিকা থাকছে না।
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, শেয়ারবাজার একটি কার্যকর শিল্পায়নের মঞ্চ হিসেবে কাজ করতে পারত। কিন্তু বাংলাদেশে এটি এখন স্বল্পমেয়াদি জল্পনা-কল্পনার বাজারে পরিণত হয়েছে। অনেক কোম্পানি আইপিওর মাধ্যমে বাজারে আসছে না, বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমছে এবং উদ্যোক্তারা ব্যাংক ঋণের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই চক্র ভাঙা না গেলে শেয়ারবাজার শিল্পায়নের কাজে সহায়ক হবে না।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ব্রোকার্স সমিতির সভাপতি সাঈফুর ইসলাম বলেন, বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সিদ্ধান্ত ও হস্তক্ষেপ বাজারকে স্থবির করেছে। ফ্লোর প্রাইসের মতো কঠোর নিয়ম বাজারের গতিশীলতা কমিয়ে দিয়েছে। যেদিন নীতিমালা স্বচ্ছ ও ধারাবাহিক হবে, সেদিন শেয়ারবাজার শিল্পায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্র হিসেবে পুনরায় কার্যকর হয়ে উঠবে।
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষক ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ ড. নাজনীন আহমেদ বলেন, বিদেশি ও প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য শেয়ারবাজারে স্বচ্ছতা এবং নীতির ধারাবাহিকতা অপরিহার্য। যারা বিদেশে বিনিয়োগ করে, তারা এমন দেশে বিনিয়োগ করতে চায় যেখানে সুশাসন ও নিয়মিত নীতি বিদ্যমান। বাংলাদেশে এই ঘাটতি থাকায় তারা সরে যাচ্ছে। আস্থা ফেরাতে হলে কোম্পানিগুলোর আর্থিক সক্ষমতা বাড়ানো এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যক্রম উন্নত করা প্রয়োজন।
ফেলো চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (এফসিএ) মাহমুদ হোসেন বলেন, স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নেই। ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড আসলে হয়ে উঠেছে আনক্লেইমড ডিভিডেন্ডের ওপর এফডিআর করে সুদ খাওয়ার প্ল্যাটফর্ম। এই ফান্ড থেকে বাজারে কত টাকা বিনিয়োগ হয়েছে? কোনো রেগুলেটর বা মিডিয়া কি সেই তথ্য প্রকাশ করেছে?
পুঁজিবাজারে রাজনৈতিক বন্দোবস্তে পুঁজি লুট হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের পুঁজিবাজারে বছরের পর বছর যা ঘটেছে, তা কোনো দুর্ঘটনা নয়। এটি একটি রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে সংঘটিত পুঁজি লুট।



 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন


-20251005020735.webp)

-20251005020325.webp)



-20251005020010.webp)
-20251005015751.webp)


-20250928135250.webp)
-20250929230040.webp)
-20251001000604.webp)
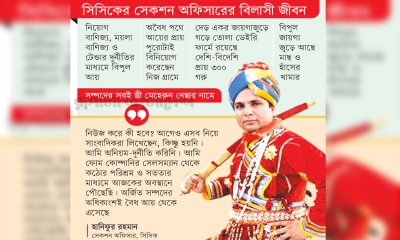









আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন