ভারত এক সময় ছিল বৈচিত্র্যের গর্বে গর্বিত এক সভ্যতার প্রতীকÑ যেখানে ধর্ম, ভাষা, জাত ও সংস্কৃতির মিলনে গড়ে উঠেছিল বহুত্ববাদী মানবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু আজকের ভারতের চিত্র যেন উল্টোÑ এখানে বহুত্বের জায়গা নিয়েছে বিভাজন, মানবতার জায়গা নিয়েছে বিদ্বেষ, আর নাগরিকত্বের জায়গা দখল করেছে পরিচয়ের রাজনীতি। আজকের ভারতের সবচেয়ে ভয়ংকর বাস্তবতা হলো, মুসলমানদের ঘৃণা এখন কেবল রাজনীতির হাতিয়ার নয়; এটি পরিণত হয়েছে নিত্যদিনের জনবিনোদন, এক সাংস্কৃতিক উৎসব, যেখানে অপমানই আনন্দ, আর নিপীড়নই সংবাদ।
আজ টেলিভিশনের পর্দা থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়ার মিমÑ সবখানেই মুসলমানদের অস্তিত্ব যেন হাসির উপকরণ। প্রতিদিনের খবরের ভেতর লুকিয়ে থাকে এক ভয়াবহ বাস্তবতাÑ কারো নামাজ বন্ধ করা হয়েছে, কারো দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছে, কারো সন্তানকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। অথচ এসব ঘটনা এখন আর ক্ষোভ জাগায় না; বরং দর্শক তা দেখে ‘রিয়েলিটি শো’-এর মতো উপভোগ করে। এ এক অদ্ভুত রূপান্তরÑ যেখানে নিষ্ঠুরতা হারিয়েছে লজ্জা, আর সহানুভূতি পরিণত হয়েছে দুর্বলতার প্রতীকে।
ভারতের এই পরিস্থিতি বুঝতে হলে আগে বুঝতে হবেÑ ঘৃণা কীভাবে পরিকল্পিতভাবে এক বিনোদন শিল্পে পরিণত হলো। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি কখনোই ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য রাখেনি; এর গভীরে ছিল সংস্কৃতি পুনর্লিখনের উচ্চাকাক্সক্ষা। তারা ভারতের আত্মপরিচয় বদলে দিয়েছেÑ যেখানে ‘ভারতবর্ষ’ মানে এখন আর সকলের দেশ নয়; বরং ‘হিন্দু ভারতের’ একচেটিয়া কল্পনা। এই কল্পনাতেই মুসলমানদের জায়গা নেই, কিংবা থাকলেও তা কেবল শত্রু বা সন্দেহভাজন হিসেবে।
টেলিভিশনের ‘প্রাইম টাইম’ বিতর্কগুলো এখন যেন আধুনিক যুগের জনসমক্ষে শাস্তি প্রদর্শন। কোনো মুসলিম ছাত্রের মন্তব্য, কোনো মুসলিম অভিনেত্রীর পোশাক, কোনো মুসলিম নেতার বক্তব্যÑ সবই সেখানে বিচারের কাঠগড়ায়। সাংবাদিকেরা আর সংবাদ পরিবেশন করেন না; তারা একধরনের বিচারক, যারা প্রতিদিন ঘোষণা করেন কে ‘দেশদ্রোহী’ আর কে ‘দেশপ্রেমিক’। এই মিডিয়া সার্কাসে মুসলমানরা কখনোই নির্দোষ হতে পারে না। তাদের সব প্রশ্ন সন্দেহজনক, তাদের সব দাবি উসকানিমূলক।
তবে এই ঘৃণার থিয়েটার কেবল পর্দায় নয়Ñ রাস্তা, বাজার, মসজিদ, এমনকি স্কুলেও ছড়িয়ে পড়েছে। আজমগড়, ইন্দোর, কানপুর বা দিল্লির মুসলমানদের কাছে ঘৃণা কোনো সংবাদ নয়, এটি তাদের জীবনের প্রতিদিনের বাস্তবতা। কখনো তাদের বাড়ি ভাঙা হয় ‘আইনশৃঙ্খলা রক্ষার’ নামে, কখনো তাদের দোকান উচ্ছেদ করা হয় ‘অবৈধ নির্মাণ’-এর অজুহাতে। অথচ একই অপরাধে হিন্দু নাগরিকরা পার পেয়ে যায়। রাষ্ট্রের চোখে মুসলমান যেন এক চিরস্থায়ী সন্দেহভাজনÑ যে জন্মগতভাবে অভিযুক্ত। এই প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যকে বৈধতা দেয় মিডিয়া ও প্রশাসন। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনো মুসলমানকে ‘লাভ জিহাদ’-এর অভিযোগে মারধর করা হয়, তখন টেলিভিশন চ্যানেলগুলো সেটিকে ‘সংস্কৃতি রক্ষার লড়াই’ হিসেবে তুলে ধরে। আবার যখন কোনো মুসলমান ‘আই লাভ মুহাম্মদ’ লেখা প্ল্যাকার্ড তোলে, তখন পুলিশ তার বিরুদ্ধে এফআইআর করে। ভালোবাসার প্রকাশও আজ অপরাধ, কারণ ভালোবাসা হিন্দুত্বের বৃত্তে ফিট হয় না।
ভারতের উত্তর প্রদেশ আজ এই ঘৃণার রাজনীতির সবচেয়ে দৃশ্যমান ল্যাবরেটরি। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ভাষণে মুসলমানদের ‘অনুপ্রবেশকারী’ বা ‘সন্ত্রাসের সহানুভূতিশীল’ বলা হয়, অথচ তা সাধারণের কাছে হয়ে ওঠে জনপ্রিয় স্লোগান। রাজ্য প্রশাসন এখন এক রাজনৈতিক মঞ্চ, যেখানে সংখ্যালঘুদের অপমান মানেই জনপ্রিয়তা। এক সময় যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের রক্ষা করত, আজ সেই রাষ্ট্রই হয়ে উঠেছে নির্যাতনের পরিচালক।
এই বাস্তবতাকে সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন ‘স্টেট অব ডিনায়াল’Ñ অস্বীকারের রাষ্ট্র। যখন একটি সমাজ সহিংসতাকে এতটাই স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয় যে তা আর আলোড়ন সৃষ্টি করে না, তখন মানবতার মৃত্যু ঘটে নীরবতার ভেতরেই। আজকের ভারত সেই অবস্থায় পৌঁছেছে। মুসলমান শিশুর মৃত্যু কিংবা মসজিদ ধ্বংসের খবর এখন আর প্রতিবাদ জাগায় না; বরং সংবাদপত্রের নিচের দিকে ছোট করে ছাপা হয়, যেন সেটি তুচ্ছ ঘটনা।
কিন্তু কেন এই ঘৃণা এত সফলভাবে প্রোথিত হলো? এর উত্তর খুঁজতে গেলে দেখতে হয়, ঘৃণা এখন আর কেবল আবেগ নয়Ñ এটি এক অর্থনীতি। ঘৃণার চারপাশে গড়ে উঠেছে ভোটব্যাংক, মিডিয়া স্পনসরশিপ, সোশ্যাল মিডিয়া ক্লিক, এমনকি চলচ্চিত্রের বাজারও। মুসলমানদের ‘ভয়’ বিক্রি করে এখন কোটি কোটি রুপি উপার্জন হয়। টিভি ডিবেটের রেটিং বাড়ে, ইউটিউব চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার বাড়ে, আর রাজনৈতিক দলগুলো এই আবেগকে ভোটে রূপান্তর করে। অর্থাৎ ঘৃণা এখন পণ্য, আর মুসলমানদের কষ্ট হলো সেই পণ্যের ‘ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি’।
তবে বিষয়টি কেবল অর্থনৈতিক নয়; এটি এক মনস্তাত্ত্বিক অভিযোজনও বটে। দীর্ঘদিনের প্রপাগান্ডা মানুষকে এমনভাবে অভ্যস্ত করেছে যে তারা আর অন্যায়ের বিরোধিতা করতে পারে না। বরং তারা মনে করেÑ এটাই স্বাভাবিক। ইতিহাসে এমন পরিস্থিতি নতুন নয়। নাৎসি জার্মানিতে ইহুদি নিধনের সময় সাধারণ জার্মান নাগরিকরাও একইভাবে নীরব ছিল। তারা ভাবত, ইহুদিরাই সমস্যা। আজকের ভারতের অনেক মানুষও ঠিক তাই ভাবেÑ ‘মুসলমানরা দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে’। এই চিন্তাই ফ্যাসিবাদের প্রাথমিক খাদ্য।
মাহমুদ মামদানি তার বই এড়ড়ফ গঁংষরস, ইধফ গঁংষরস–এ বলেছিলেন, রাষ্ট্র সবসময় মুসলমানদের দুই ভাগে ভাগ করেÑ ‘গ্রহণযোগ্য’ আর ‘অগ্রহণযোগ্য’। যে মুসলমান প্রতিবাদ করে না, সে ভালো; আর যে মর্যাদা চায়, সে বিপজ্জনক। ভারতেও ঠিক এই কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে মুসলমান চুপচাপ থেকে যায়, সে ‘দেশপ্রেমিক’; কিন্তু যে নিজের পরিচয়ে গর্ব করে, সে সঙ্গে সঙ্গে ‘দেশদ্রোহী’।
এই নীরব বিভাজনই আজ ভারতের সামাজিক কাঠামো ভেঙে দিয়েছে। একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের আত্মতুষ্টি, অন্যদিকে সংখ্যালঘুদের আতঙ্ক। প্রতিদিনের সহিংসতা এখন একধরনের উৎসব, যেখানে মানুষ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব উদ্যাপন করে অন্যের অপমানের মধ্য দিয়ে। সামাজিক মাধ্যমে ঘৃণার ভিডিও, লিঞ্চিংয়ের দৃশ্য, ধর্মীয় অপমানÑ সবই আজ ‘ভাইরাল কনটেন্ট’। কেউ নিহত হলে মন্তব্য আসে, ‘ঠিক হয়েছে, দেশবিরোধী ছিল।’ এই হাসি আসলে সভ্যতার সমাধিলিপি।
ফ্যাসিবাদ কখনো একদিনে জন্ম নেয় না; এটি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে মানুষের মগজে, সংবাদে, বিনোদনে, হাসিতে। ভারতের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে। এখন ‘হিন্দু গর্ব’ মানে মুসলমানবিরোধিতা; ‘দেশপ্রেম’ মানে সংখ্যালঘুদের সন্দেহ করা। অথচ ভারতের সংবিধান যে নীতিতে গঠিত হয়েছিল, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল মূল স্তম্ভ। সেই স্তম্ভ এখন চূর্ণবিচূর্ণ।
তবে এই ঘৃণার পরিণতি কেবল মুসলমানদের জন্য নয়, পুরো ভারতের জন্যই ভয়ংকর। ইতিহাস বলেÑ যে সমাজ সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার করে, শেষ পর্যন্ত সেই সমাজই আত্মবিনাশে পতিত হয়। জার্মানি নাৎসিবাদের দুঃস্বপ্ন থেকে বের হতে যে মূল্য দিয়েছে, তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহন করেছে। আমেরিকায় দাসপ্রথার উত্তরাধিকার এখনো জাতিগত বিভাজন সৃষ্টি করে। ভারতও যদি এই ঘৃণার আগুনে পুড়তে থাকে, তবে তার ফল হবে এক ভেতর থেকে পচে যাওয়া প্রজাতন্ত্র।
আজ প্রশ্ন উঠছে: ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠরা কি এখনো মানুষটিকে চিনতে পারে? প্রতিবেশীর নাম আজান শুনে যদি কারো চোখে ঘৃণা জাগে, তবে সেই সমাজে মানবতা বেঁচে থাকে না। যারা আজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে নীরব, কাল তাদের সন্তানরাও অন্য কোনো পরিচয়ের জন্য নিপীড়িত হবে। কারণ, ঘৃণা একবার বৈধতা পেলে তা আর কোনো সীমানা মানে না।
এই ভয়াবহ বাস্তবতার মধ্যেও আশা পুরোপুরি নিঃশেষ হয়নি। ভারতের অসংখ্য উদারমানুষ এখনো প্রতিবাদ করছেন, লিখছেন, দাঁড়াচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ প্রজন্মের এক অংশ এখনো ঘৃণার বিরুদ্ধে ভালোবাসার ভাষা শেখাচ্ছে। কিন্তু এই প্রতিরোধ এখনো ক্ষীণ, আর রাষ্ট্রযন্ত্রের আওয়াজ এত প্রবল যে তা প্রায় ঢেকে দেয় মানবতার কণ্ঠ। তবু মনে রাখতে হবে, নীরবতা কখনো নিরপেক্ষ নয়। যে নীরব থাকে, সে আসলে ঘৃণার সহযোগী। তাই ভারতের নাগরিকদের এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবেÑ তারা কি এই ঘৃণার বিনোদনে দর্শক হয়ে থাকবে, নাকি পর্দা ভেঙে সত্যের পক্ষে দাঁড়াবে?
আজকের ভারত এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখানে ঘৃণা আর হাসির মাঝের ব্যবধান মুছে গেছে। যখন লিঞ্চিং ভিডিও হাসির ইমোজিতে পরিণত হয়, তখন গণতন্ত্র মৃত। আর যখন শিশুর মৃত্যু টেলিভিশনের ব্রেকিং নিউজে জায়গা পায় না, তখন মানবতা নির্বাসিত হয়।
ঘৃণার রাজনীতি ক্ষণিকের ক্ষমতা এনে দিতে পারে, কিন্তু তা কোনো সমাজকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের একাংশকে চিরশত্রু মনে করে, সে কখনো নিরাপদ হতে পারে না। কারণ, ভয়ভিত্তিক রাজনীতি নিজেই একদিন নিজের ভয় তৈরি করে। আজ ভারতের শাসকগোষ্ঠী মুসলমানদের ভয় দেখিয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রেখেছে; কাল সেই ভয়ই তাদের গ্রাস করবে।
শেষ পর্যন্ত, ঘৃণার এই উল্লাস একদিন থামবেÑ যেভাবে ইতিহাসের সব মিথ্যা থেমেছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাবে: তখন কতজন বেঁচে থাকবে বিবেক নিয়ে?
ভারতের গণতন্ত্রের প্রকৃত পরীক্ষা এখন। এটি কোনো নির্বাচনের লড়াই নয়; এটি আত্মার লড়াইÑ মানবতার বনাম ঘৃণার। যদি এই লড়াইয়ে মানুষ হারে, তবে শুধু মুসলমান নয়, গোটা ভারত হারাবে তার আত্মা, তার সভ্যতা, তার ইতিহাস।
তাই এখনো সময় আছেÑ যারা ঘৃণার হাসিতে মগ্ন, তাদের জানা উচিত, এই হাসি চিরস্থায়ী নয়। কারণ, যে জাতি সংখ্যালঘুদের কষ্টে আনন্দ খুঁজে পায়, ইতিহাসের অন্ধকারে তার নিজের পরিণতিও লেখা হয়ে যায়।
আজকের ভারতের জন্য প্রশ্ন একটাই: তারা কি সেই অন্ধকারে ডুবতে চায়, নাকি মানবতার আলোয় ফিরে আসতে চায়? সিদ্ধান্ত তাদেরই, কিন্তু তার মূল্য দেবে পুরো সভ্যতা।



 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন


-20251024022324.webp)





-20251024021636.webp)
-20251024021527.webp)
-20251024021426.webp)
-20251024021330.webp)
-20251024021216.webp)
-20251024021056.webp)




-20251019140621.webp)
-20251020114155.webp)





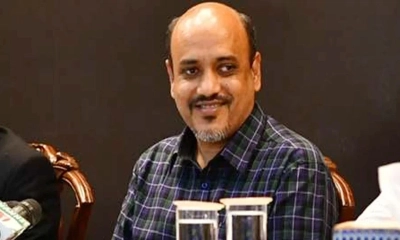



আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন