‘এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম-গাছের তলে, তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে’ পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের ‘কবর’ কবিতার প্রথম দুটি লাইন, বাংলা সাহিত্যের সাধারণ থেকে শুরু করে বিদগ্ধ সব পাঠকই একবার হলেও পাঠ করেছেন। এমন অসংখ্য মানুষও আছেন, যারা সম্পূর্ণ কবিতাটি আত্মস্থ করেছেন কাব্যিক প্রেম থেকে।
ছন্দের দ্যোতনা আর দৃশ্যকল্পের বন্ধনে কোনো এক অজানা বৃদ্ধের জীবনের দুঃখগাথার সঙ্গে পাঠক অবচেতনে হয়তো নিজেকেই খুঁজে নিয়েছেন। আনন্দের কথা হলো অমর কবিতাটি প্রকাশের শতবর্ষে পা রেখেছে চলতি বছর।
আজ থেকে একশ বছর আগে ১৯২৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের কলকাতা থেকে প্রকাশিত কল্লোল পত্রিকার জুন-জুলাই সংখ্যায় কবিতাটি প্রথম মুদ্রিত হয়। কল্লোল পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় ‘গ্রাম্য কবিতা’ পরিচয়ে প্রকাশিত ‘কবর’ পাঠক মহলে তুমুল সাড়া ফেলে। কবি জসীমউদ্দীন তখন বিএ ক্লাসের ছাত্র।
১৯২৫ সালে কবিতাটি যখন কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন কবিতাটি নিয়ে ড. দীনেশচন্দ্র সেন ফরোয়ার্ড পত্রিকায় যে আলোচনা করেছিলেন, তার শিরোনাম ছিল ‘অ্যান ইয়াং মোহামেডান পোয়েট’।
এই আলোচনাই বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি কেড়েছিল। কবিতাটি তখন নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রেও ড. সেনের ভূমিকা ছিল। দীনেশ সেন কবিকে ‘মোহামেডান পোয়েট’ বলে পরিচয় করে দিয়েছিলেন। তখন কবির সঙ্গে যে মুসলমান অভিধা যুক্ত ছিল। অল্প সময়ের ব্যবধানে তা উধাও হয়ে যায়। তিনি হয়ে ওঠেন পল্লীকবি। মুসলিম সম্প্রদায়ে তার জন্ম হলেও তিনি হিন্দু-মুসলমান সবার কবি, বাংলা ভাষার অন্যতম শক্তিমান কবি। রবীন্দ্রনাথ জাতপাতের ঊর্ধ্বে ছিলেন, নজরুল জাতপাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, জসীমউদ্দীন জাতপাত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে গ্রাম-বাংলার জনজীবনের ছবি এঁকেছেন।
বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরের নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত এই কবিতা নিবিড়ভাবে মিশে আছে বাঙালির প্রাণে। এর প্রতিটি পঙক্তিতেই রয়েছে শোক, বেদনাবোধ ও আত্মিক প্রকাশ। ফলে শত বছর পেরিয়ে গেলেও বাংলা সাহিত্যে কবিতাটি এখনো স্বতন্ত্র জায়গা দখলে নিয়ে পাঠকের হৃদয় থেকে হৃদয়ে নির্মলভাবে বিচরণ করছে।
পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের ‘রাখালী’ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ‘কবর’ কবিতাটি রচিত হয়েছে ষাণত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। যেখানে এক গ্রামীণ বৃদ্ধের একে একে সব প্রিয়জন হারানোর হৃদয়বিদারক বেদনা কবি ১১৮টি চরণে দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখা এই কবিতাটি শুধু প্রিয়জনদের জন্য শোক নিয়েই নয়, বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের একটি সুন্দর চিত্র অথচ নির্মম বটে। কবিতাটিতে গাঢ় বেদনা আর ভালোবাসার রঙে আঁকা বাংলার পল্লীজীবনের এই অসাধারণ প্রতিচ্ছবি ফুঁটে উঠেছে। কাহিনি বর্ণনাকারী গ্রামীণ বৃদ্ধ আর শ্রোতা হলো তার নাতি। যে পাঁচজন স্বজন হারানোর ব্যথা বৃদ্ধ দাদু এক এক করে বর্ণনা করেছেন তারা হলেন: বৃদ্ধের স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনি ও মেয়ে। এরা নাতির দাদি, পিতা, মাতা, বুজি ও ছোট ফুপু।
কবিতায় বৃদ্ধ দাদু তার জীবনের সব প্রিয়জনকে হারিয়ে জীবনের বোঝা আর বইতে চান না। তাই তিনি নাতিকে বলছেন, ‘ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিয়ে ঘন আবিরের রাগে / অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে’।
১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে কবির জন্ম। কবি যে ঘরে থাকতেন, সে বাড়ির সামনে ছিল একটি সিঁড়ি; সিঁড়ির দু’পাশে লেবুগাছ, মাঝখানে ডালিম গাছ। এই জায়গাটিই তার কবিতার সৃষ্টির উৎসভূমি। তাই তার লেখায় উঠে এসেছে পল্লীমানুষের জীবনের হালচাল, সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা ও বিচ্ছেদ। কবি গ্রাম-বাংলায় জন্ম নিলেও তার জীবনসংগ্রাম গ্রামে আটকে থাকেনি। তিনি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে পড়িয়েছেন। কিন্তু তার কলম ছিল গ্রাম-বাংলায় নিবদ্ধ।
তিনি কবিতায়, গানে, নাটকে পরম মমতায় গ্রাম-বাংলার জনজীবনের সুখ-দুঃখ চিত্রায়িত করেছেন। এ কারণেই তিনি পল্লীকবি বলে খ্যাত। তবে তিনি বাংলা সাহিত্যের এক আধুনিক কবি, তার রচনাশৈলী আধুনিক। তিনি সুনিপুণ মুনশিয়ানায় বঙ্গবাসীর জীবন ও সংস্কৃতি তুলে ধরেছেন। গ্রাম-বাংলা আগের মতো নেই। বদলেছে অনেক। জসীমউদ্দীন গ্রামের যে চিত্র এঁকেছেন, তা শত বছর আগে দেখা।
তখন পাকা সড়ক, গাড়ি, বৈদ্যুতিক আলো কিছুই ছিল না। ছিল শুধু অবারিত মাঠ, মাঠ চিরে বয়ে যাওয়া নদী, বিল-ঝিল, নালা-ডোবা। এই পরিবেশ অনেকটা বদলালেও এখনো প্রকৃতি ঘিরেই কৃষকের জীবনসংগ্রাম। মাঠে কিষান সোনালি ফসল ফলায়, সেই ফসল বোনা, পরিচর্যা, ঘরে তোলা ইত্যাদিতে ব্যতিব্যস্ত তাদের জীবন। সে জীবনে প্রেম আছে, ভালোবাসা আছে, হাসি-আনন্দ আছে, তার চেয়ে ভয়ংকর রূপে আছে প্রিয়জন হারানোর শোক। কবির কবর কবিতাটি কৃষকের জীবনের এমনই এক শোকগাথা। এই শোকগাথার প্রতিটি পঙ্ক্তি পাঠককে স্পর্শ করে, আবহমান বাংলায় নিয়ে যায়।

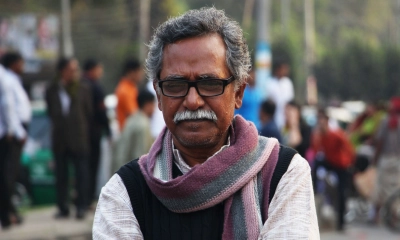
-20250601234135.webp)

