আজকের পৃথিবীতে ভোগ যেন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। মানুষ আজ শুধু প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভোগ করছে না, বরং ভোগকে ব্যবহার করছে মর্যাদা ও পরিচয়ের প্রতীক হিসেবে। কে কত দামি মোবাইল ব্যবহার করছে, কে কত বিলাসবহুল পোশাক পরছে, কে কোন রেস্টুরেন্টে খাচ্ছে এসব দিয়েই সামাজিক অবস্থান মাপা হচ্ছে। এ প্রতিযোগিতা কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং পুরো সমাজকে এক অদৃশ্য কারাগারে বন্দি করেছে, যার নাম ভোগবাদ।
ভোগবাদ বা কনজিউমারিজমকে সমাজবিজ্ঞানীরা শুধু অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেন না। এটি একটি সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ, যা সমাজের শ্রেণি-অবস্থান, সম্পর্ক ও মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে। ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী পিয়েরে বোর্দিউ তার উরংঃরহপঃরড়হ গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ভোগ আসলে এক ধরনের ‘সাংস্কৃতিক পুঁজি।’ ধনী শ্রেণি নিজেদের ভোগের ধরন দিয়ে আলাদা পরিচয় তৈরি করে, আর সাধারণ মানুষ সেই ভোগকে অনুকরণ করতে গিয়ে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করে। ফলে ভোগবাদ শুধু অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নয়, বরং সামাজিক বিভাজনের এক শক্তিশালী অস্ত্র।
কার্যকারণবাদীরা ভোগবাদকে সমাজের স্থিতিশীলতার উপাদান হিসেবে দেখেন। তাদের মতে, মানুষ ভোগ করলে শিল্পকারখানা সচল থাকে, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয় এবং অর্থনীতি ঘুরতে থাকে। ভোগ তাই সমাজে এক ধরনের সমন্বয় আনে। তবে একই সঙ্গে তারা এটাও স্বীকার করেন, অতিরিক্ত ভোগ ব্যক্তি ও সমাজকে অস্থির করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, উৎসবের সময় অতিরিক্ত ভোগ মানুষকে সাময়িক আনন্দ দিলেও দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক চাপ ও মানসিক অস্থিরতা বাড়িয়ে তোলে।
সংঘাতবাদীরা, বিশেষ করে কার্ল মার্কস, ভোগবাদকে দেখেছেন পুঁজিবাদের কৌশল হিসেবে। তার মতে, পুঁজিবাদ মানুষকে এমন সব পণ্য ভোগে বাধ্য করে যেগুলো প্রকৃতপক্ষে তার প্রয়োজন নেই। এভাবে মানুষকে একধরনের ঈড়সসড়ফরঃু ঋবঃরংযরংস-এ আবদ্ধ করা হয়, যেখানে জিনিসের প্রতি মানুষের আসক্তি তৈরি হয়, কিন্তু সেই জিনিস তৈরির পেছনে শ্রমিকের কষ্ট ও শোষণ অদৃশ্য থেকে যায়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা বিলাসবহুল পোশাক কিনতে গিয়ে ভাবি না, সেই পোশাক তৈরির শ্রমিক হয়তো ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছে না। ভোগবাদ এভাবেই শ্রেণি-বৈষম্যকে গভীর করে তোলে।
প্রতীকী আন্তঃক্রিয়াবাদীরা ভোগকে দেখেন সামাজিক যোগাযোগের প্রতীক হিসেবে। একজন মানুষ যখন বিলাসবহুল গাড়ি চালায় বা দামি রেস্টুরেন্টে যায়, তখন সে শুধু নিজের প্রয়োজন মেটাচ্ছে না, বরং সে বোঝাতে চাচ্ছে ‘আমি এই সামাজিক অবস্থানে আছি।’ ভোগ এখানে একটি শব্দবিহীন ভাষার মতো কাজ করে, যার মাধ্যমে মানুষ নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করে থাকে। আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে দিকটি আরও স্পষ্ট। মানুষ ভোগ করছে শুধু নিজের জন্য নয়, বরং অন্যকে দেখানোর জন্য।
ভোগবাদ শুধু সমাজের কাঠামো নয়, ব্যক্তির মানসিক জগতকেও প্রভাবিত করছে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, ভোগ সাময়িক আনন্দ বা রহংঃধহঃ মৎধঃরভরপধঃরড়হ দেয়। নতুন মোবাইল কিনলে বা নতুন পোশাক নিলে মুহূর্তের জন্য আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই আনন্দ অল্প সময়ের মধ্যেই ম্লান হয়ে যায়। তখন আবার নতুন কিছুর খোঁজ শুরু হয়। এই চক্র মানুষকে অসন্তুষ্ট, অস্থির ও হতাশ করে তোলে। গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত ভোগবাদী সমাজে হতাশা ও মানসিক রোগের প্রবণতা অনেক বেশি।
শিশুদের জীবনেও ভোগবাদের প্রভাব ভয়াবহ। টেলিভিশন ও ইউটিউব বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছোটবেলা থেকেই তাদের মনে কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করা হয়। কোন খেলনা, কোন জামাকাপড় বা কোন খাবার জনপ্রিয়, তা নির্ধারণ করে বিজ্ঞাপন ও বাজার। ফলে শিশুরা খুব অল্প বয়সেই শিখে যায়, নিজের পরিচয় ও মর্যাদা তৈরি করতে হলে ভোগ করার ধরনের বিকল্প নাই। শৈশবের সরলতা হারিয়ে তারা হয়ে ওঠে প্রতিযোগিতার অংশীদার।
প্রযুক্তি ও গ্লোবালাইজেশন ভোগবাদকে আরও তীব্র করে তুলছে। একসময় ভোগ ছিল কেবল ব্যক্তিগত, আজ তা হয়ে উঠেছে প্রকাশ্য। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষ প্রতিনিয়ত নিজেদের প্রদর্শন করছে নানা ভাবে। কে কোথায় ভ্রমণ করছে, কে কোন পোশাক পরছে, কে কোন খাবার খাচ্ছে এসব ছবি ও ভিডিও যেন এক ধরনের প্রতিযোগিতার মাঠ। এ তুলনামূলক সংস্কৃতি (ঈড়সঢ়ধৎরংড়হ ঈঁষঃঁৎব) মানুষকে আরও বেশি ভোগে উৎসাহিত করছে। অন্যদিকে গ্লোবালাইজেশন আমাদের সামনে এমন সব পণ্য হাজির করছে, যা আগে কল্পনাও করা যেত না। ফলে মানুষের চাহিদা সীমাহীন হয়ে পড়ছে।
অতিরিক্ত ভোগের ক্ষতি শুধু ব্যক্তি বা সমাজেই সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রভাব পড়ছে পুরো পৃথিবীর ওপর। শিল্পায়নের নামে অতিরিক্ত উৎপাদন, অপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারজাতকরণ, প্লাস্টিকের ব্যবহার, বন উজাড় সবই ভোগবাদী মানসিকতার ফল। জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতা, প্রাকৃতিক সম্পদের সংকটের পেছনে ভোগবাদ সরাসরি দায়ী। পরিবেশবিদরা বলেন, ভোগবাদ হলো মানব সভ্যতার আত্মঘাতী প্রবণতা। কারণ আমরা যত বেশি ভোগ করছি, তত বেশি প্রকৃতিকে ধ্বংস করছি, আর শেষ পর্যন্ত সেই ধ্বংসই আমাদের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলছে।
ভোগবাদ কি সত্যিই আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে, নাকি নতুন এক দাসত্বে আবদ্ধ করেছে? একদিকে ভোগ আমাদের জীবন সহজ করেছে, আধুনিক প্রযুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে এটি আমাদের চিন্তা-চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, আমাদের ইচ্ছাকে বানাচ্ছে বিজ্ঞাপন আর বাজারের অন্যতম হাতিয়ার। আমরা আর স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না পরোক্ষভাবে ভোগের দ্বারা শাসিত হচ্ছি।
ভোগবাদিতার দাসত্বে আজকের সমাজ শ্বাসরুদ্ধ। মানুষ সুখ খুঁজছে পণ্যে, মর্যাদা খুঁজছে ব্র্যান্ডে, অথচ হারাচ্ছে অন্তরের শান্তি ও মানবিক মূল্যবোধ। সমাজবিজ্ঞানের আলোয় দেখা যায়, ভোগবাদ একদিকে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হলেও অন্যদিকে এটি সামাজিক বৈষম্য, মানসিক অস্থিরতা ও পরিবেশ ধ্বংসের মূল কারণ। তাই ভোগবাদী জীবন থেকে সরে এসে টেকসই জীবনধারায় অভ্যস্ত হওয়া আবশ্যক। যেখানে ভোগ থাকবে প্রয়োজনের সীমায়, আর সুখ ও মর্যাদা নির্ভর করবে মানবিকতা, সহমর্মিতা ও সৃজনশীলতার ওপর।
এখন সময় এসেছে ভাবনায় নতুনত্ব আনার। নতুন প্রজন্মকে শেখাতে হবে, জীবনের মূল্য ভোগে নয়, বরং মানবিকতায়। রাষ্ট্রকে ভোগবাদী সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার নীতি নিয়ে কাজ করতে হবে এবং পরিবেশবান্ধব ভোগবাদকে উৎসাহিত করতে হবে। সমাজকে ফিরে যেতে হবে সেই মূল্যবোধে, যেখানে ভোগ নয়, ভাগাভাগিই ছিল জীবনের আনন্দ। তবেই হয়তো ফিরে পাবো নতুন বিশ্বকে।
হুমায়ুন আহমেদ নাইম , সমাজবিজ্ঞান বিভাগ , জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়



 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন



-20251207041530.webp)
-20251207041322.webp)

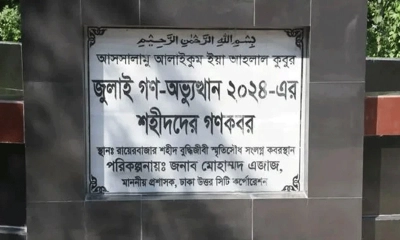





-20251207090711.webp)



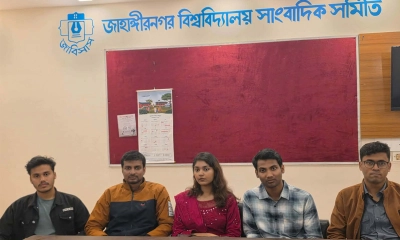









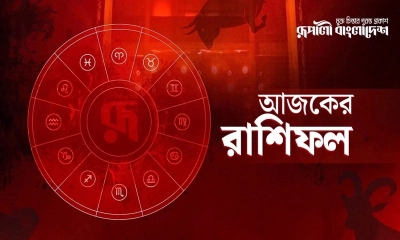
-20251203221210.webp)








আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন