বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আন্দোলন, দাবি-দাওয়া ও সরকারবিরোধী উত্তাপ নতুন নয়। কিন্তু কিছু কিছু সময়সীমা ও ঘটনা একত্রে জুড়ে গেলে তা কেবল সামাজিক বা পেশাগত দাবি থাকে না, বরং তা হয়ে ওঠে বৃহত্তর রাজনৈতিক ঘটনার অংশ। সাম্প্রতিক প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন এবং একই সময়ে আওয়ামী লীগের লকডাউন কর্মসূচি- এই দুই ঘটনাকে তাই আলাদা করে দেখা কঠিন। এ ঘটনা বিশেষত, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় ঘোষণার সম্ভাব্য সময়সীমাকে ঘিরে রাজনীতির মঞ্চে নতুন উত্তাপ তৈরি হয়েছে।
প্রেক্ষাপট: রায়ের আগের রাজনৈতিক পরিবেশ
আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মামলা বা রাজনৈতিক চাপ নতুন নয়। তবে এবার পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। আন্তর্জাতিক আদালত, মানবাধিকার সংস্থা, গণহত্যার দাবি, সংঘর্ষের বয়ান- সব মিলিয়ে প্রতিবেশী ভূরাজনীতিও এখানে যুক্ত। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ওপর এর প্রভাব সরাসরি না হলেও, মনস্তাত্ত্বিক চাপ অস্বীকার করা যায় না। পরিস্থিতি যখন এমন, তখন দলীয় নেতৃত্বের চারপাশে প্রয়োজন নিরাপদ রাজনৈতিক পরিবেশ, জনমতের সংহতি এবং সড়ক-রাজপথের নিয়ন্ত্রণ। ঠিক এই সময়েই আওয়ামী লীগ লকডাউন কর্মসূচিতে যায়। এমন কর্মসূচি সাধারণত বিরোধীদল দেয়। দেশে এই মুহূর্তে নির্বাচিত কোনো সরকার নেই, তাহলে আওয়ামী লীগের এ কর্মসূচি কাকে উদ্দেশ করে?
শিক্ষকদের আন্দোলন: দাবি ন্যায্য, সময়কাল প্রশ্নবিদ্ধ
প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি- বেতন গ্রেড পুনর্বিন্যাস, পদমর্যাদা নিশ্চিত করা, ক্যাডার সমমান সুবিধা- এসবকে অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক বলা যাবে না। বহু বছর ধরেই এই দাবি রয়েছে। মাঠপর্যায়ের শিক্ষক সমাজ দীর্ঘদিন ধরেই পেশাগত মর্যাদা নিয়ে বঞ্চনার বোধে ছিলেন। তাই কোনো পর্যায়ে আন্দোলন হতেই পারত। কিন্তু প্রশ্ন হলোÑ এই মুহূর্তে কেন? ধরা যাক দুটি সম্ভাবনা: ১. দীর্ঘদিনের অসন্তোষ স্বাভাবিকভাবে বিস্ফোরিত হয়েছে। ২. কারো ইঙ্গিতে, অথবা বৃহত্তর রাজনৈতিক আবহে আন্দোলনটি ‘সময়ে-সন্ধিক্ষণে’ শক্তি পেয়েছে।
বাংলাদেশে পেশাজীবী আন্দোলন অনেক সময় দলীয় রাজনীতির পরোক্ষ ধারক-বাহক হিসেবে কাজ করে। শিক্ষক সমাজ ঐতিহাসিকভাবে মাঠে মানুষ নামাতে পারে, জনমত গঠন করতে পারে। এই শক্তি রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
লকডাউন ও আন্দোলনের ছায়া-সম্পর্ক
আওয়ামী লীগের লকডাউনের লক্ষ্য ছিল দলীয় পুনর্গঠন, কর্মীদের মাঠে সক্রিয় রাখা, রাজপথে নিজেদের অবস্থান প্রদর্শন এবং জনমত নিজের দিকে আনা। এ সময় শিক্ষকদের আন্দোলন রাজপথে নতুন ভিড় তৈরি করল। এর ফলে যা হয়েছে তাহলো-
- সড়কে নিরাপত্তা বাহিনীর মুভমেন্ট বাড়ল,
- প্রশাসনিক দৃষ্টি রাজধানীর কেন্দ্রে আটকে রইল,
- বিরোধীদল রাজপথে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ কিছুটা কম পেল,
- এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলোÑ রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্র অদৃশ্যভাবে ‘শেখ হাসিনার মামলার রায়’ থেকে ‘শিক্ষকদের দাবিতে সরে গেল। এটাকে রাজনীতি বলে, কৌশল বলে, কখনো বলে ইস্যু-রিডাইরেকশন।
কার লাভ হলো?
শিক্ষকরা তাদের দাবি সামনে আনলেন, যা ন্যায্য। কিন্তু সরকারের দৃষ্টিতে, আন্দোলনটি শক্তি দেখানোর জায়গাও হয়ে গেল। এই আন্দোলন কর্মসূচি ঘিরে যা হচ্ছে তাহলো-
- দেখানো হলো, সরকার এখনো জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট অংশের সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী।
- দেখানো হলো, রাজপথের নিয়ন্ত্রণ এখনো সরকারের হাতে।
তবে, আওয়ামী বলয়ের রাজনৈতিক দলগুলো শেখ হাসিনার সম্ভাব্য রায়কে আন্তর্জাতিক চাপ তৈরির সুযোগ মনে করলেও, রাজপথে তারা তেমন সক্রিয় হতে পারছে না। তার কারণÑ সড়ক এরইমধ্যে ব্যস্ত। ব্যস্ত শিক্ষক, ব্যস্ত পুলিশ, ব্যস্ত মিডিয়া- বিরোধী আন্দোলনের স্পেস সংকুচিত।
এটি কেবল ঘটনাপঞ্জি নয়, রাজনৈতিক সংকেত
বাংলাদেশের রাজনীতিতে কখনোই ঘটনা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। প্রতিটি পরিবর্তন, কর্মসূচি ও আন্দোলন নতুন অর্থ বহন করে। এখানে মূলত তিনটি সংকেত:
১. আওয়ামী লীগ দেখাতে চাইছে যে, তারা এখনো ‘মাঠ-রাজনীতির’ মালিক।
২. রাষ্ট্র-প্রশাসন-রাজনীতি এক সুতোয় বাঁধা আছে- এ বোধ সচল রাখা।
৩. আন্তর্জাতিক চাপের মুহূর্তে দেশকে ‘অস্থিতিশীল অবস্থায়’ দেখানোর সুযোগ না দেওয়া।
তাহলে কি শিক্ষকদের আন্দোলন ‘ব্যবহৃত’? এ প্রশ্নটি বেশ স্পর্শকাতর। কারণ দাবি সত্য, বঞ্চনা সত্য, পেশাজীবী মর্যাদাহীনতা সত্য। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে- ন্যায্য দাবি যদি রাজনৈতিক কৌশলের সময়ে আসে, তবে তা দাবি-আন্দোলন এবং রাজনৈতিক সমীকরণ- দুই-ই হয়ে ওঠে। অর্থাৎ একে সরলীকরণ করা ঠিক নয়।
আন্দোলন সত্য, আবার তাতে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার ধারণাও সত্য।
রাজনৈতিক বিস্তারের সম্ভাবনা
শেখ হাসিনার মামলার রায়- রাজনৈতিক পরিবেশে নতুন মানসিক সংবেদন তৈরি করবে, তাতে সন্দেহ নেই। এই সময়ে ক্ষমতাসীন দল রাজপথে শূন্যতা চায় না। তাই শিক্ষকদের আন্দোলন হয়ে ওঠে রাজপথে মানুষের উপস্থিতির ‘সফট মবিলাইজেশন’।
যেখানে জনসমাগম আছে, কিন্তু তা রাষ্ট্রবিরোধী নয়। মাঠ খালি নয়, আবার অগ্নিসংযোগও নেই। এটা আক্ষরিক অর্থে ‘নিয়ন্ত্রিত চাপ-নিয়ন্ত্রিত উত্তাপ’ কৌশল।
রাষ্ট্রীয় পরিণতি ও ভবিষ্যৎ সিগন্যাল
- শিক্ষকদের দাবি যদি দ্রুত সমাধানের পথে না আসে, অসন্তোষ বাড়বে।
- আওয়ামী বলয়ের দলগুলো পরিস্থিতির সুযোগ নেবে।
- সরকার চাইবে আন্দোলনটিকে সীমাবদ্ধ রাখতে।
- আন্তর্জাতিক রায়ের পর রাজনীতির উত্তাপ আরও বাড়তে পারে।
- এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ- সব পক্ষ নজর রাখছে জনমতের নীরব ভূমিকার দিকে। বাংলাদেশে রাজনীতি শুধু ঘোষণায় হয় না; হয় রাস্তাঘাটের চুপচাপ মানুষের চোখে।
শেষ পর্যায়ে যা বলতে চাই তাহলোÑ প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন ন্যায্য ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে রাজনীতির রং লেগেছে কি না- সেটা অস্বীকার করা কঠিন। আওয়ামী লীগের লকডাউন কর্মসূচি এই আন্দোলনকে আড়াল করে দেয়নি; বরং দুই ঘটনাই একে অপরকে ব্যাখ্যা করেছে। এটি কেবল দাবি ও দমন অথবা কর্মসূচি ও পাল্টা কর্মসূচির গল্প নয়। এটি সেই পুরোনো সত্যের স্মারক- বাংলাদেশে রাজনীতি কখনো শুধুই রাজনীতি নয়Ñ এতে রাষ্ট্র, সমাজ, পেশা ও কৌশল একসঙ্গে কাজ করে। আর রাজপথ- সবকিছুর কেন্দ্রস্থল। আমরা চাই না আবার রাজপথ তেঁতে উঠুক, আবার দেশ অস্থিতিশীল হোক। বরং যে রায় বা ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে এসব কর্মসূচি আবর্তিত হচ্ছে সেগুলো বন্ধ হোক। আমরা চাই- আইন তার নিজের পথেই চলুক, আইনের আওতায় সব ঘটনার বিচার হোক। সেটাই সুন্দর, তাতেই বৃহত্তর মঙ্গল। আমরা অবশ্যই মঙ্গলের পক্ষে।



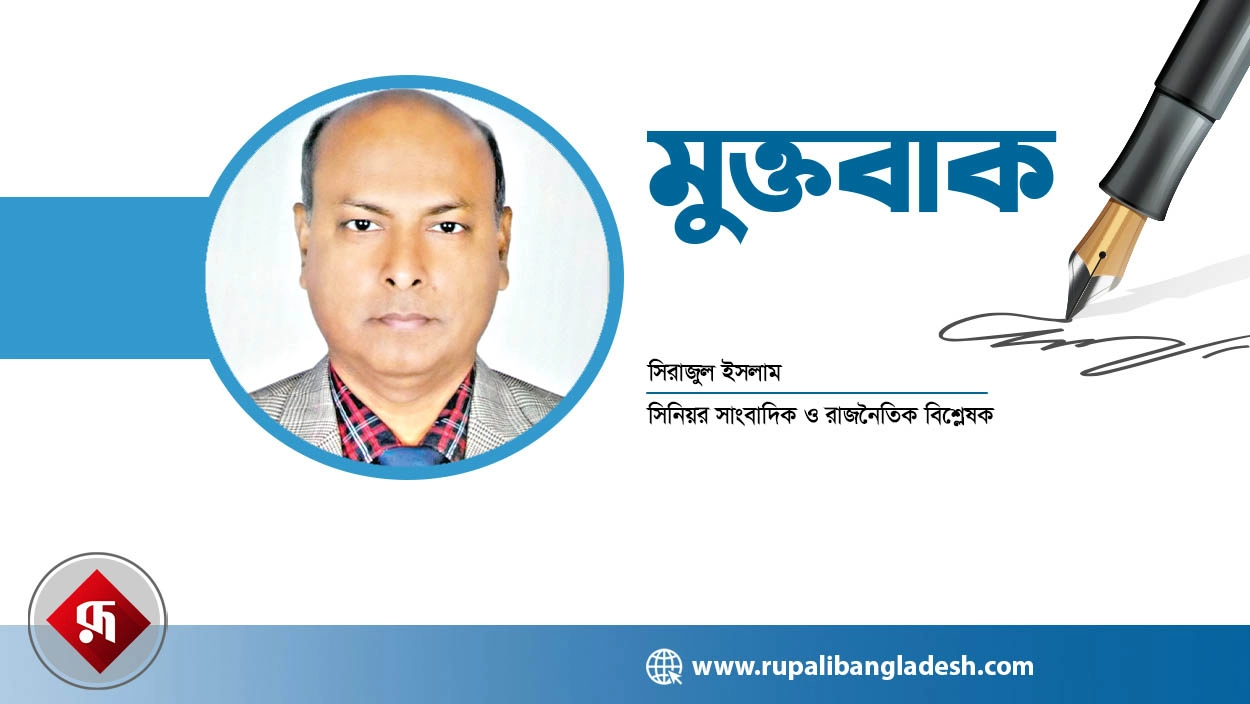
 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন


-20251114021146.webp)

-20251114020922.webp)
-20251114020830.webp)
-20251114020750.webp)
-20251113201307.webp)

-20251114020631.webp)
-20251114020528.webp)
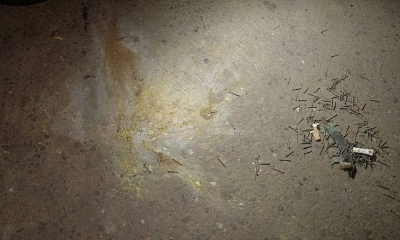
-20251114015322.webp)












-20251109011327.webp)

আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন