রক্তের কোনো বিকল্প এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তাই যখন কোনো রোগীর রক্তের প্রয়োজন হয়, তখন অন্য একজন সুস্থ মানুষের শরীর থেকে তা সংগ্রহ করে দেওয়া হয়। তবে এই রক্তদানের প্রক্রিয়া পুরোপুরি নিরাপদ নয়।
বিশেষ করে যখন নিকট আত্মীয় রক্ত দেন, তখন বিরল হলেও এক ভয়াবহ জটিলতা দেখা দিতে পারে, যার নাম Transfusion Associated Graft Versus Host Disease (TA-GvHD)।
এই জটিলতায় আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যুর হার ৯০ শতাংশ। তাই রক্তদানের পর যদি কিছু নির্দিষ্ট লক্ষণ দেখা যায়, তবে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।
বিপদের লক্ষণগুলো হলো
-শরীরে র্যাশ বা ফুসকুড়ি হওয়া, সাধারণত বুক-পিঠে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে হাত-পায়ে ছড়িয়ে পড়ে
-ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা
-জন্ডিস, যেহেতু লিভার আক্রান্ত হয়
-রক্তের উপাদান হ্রাস পায় (যেমন হিমোগ্লোবিন, শ্বেত ও লোহিত রক্তকণিকা, প্লাটিলেট ইত্যাদি)
এই উপসর্গগুলো সাধারণত রক্তগ্রহণের ৮ থেকে ১০ দিন পর থেকে শুরু হয়, কখনো কখনো ৩০ দিন পরেও দেখা যেতে পারে।
কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়
যেসব রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, তাদের ক্ষেত্রে TA-GvHD হওয়ার ঝুঁকি বেশি। তাই এদের রক্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে নিকট আত্মীয়দের এড়িয়ে চলা উচিত।
এমনকি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাভাবিক থাকলেও নিকট আত্মীয়ের রক্তে থাকা কোষসমূহ শরীরে ঢুকে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিতে পারে।
সতর্কতা হিসেবে রোগীর জন্য রেডিয়েশনযুক্ত (irradiated) রক্ত ব্যবহার করা যায়, যাতে দাতার টিস্যু কোষ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়।
কী করবেন উপসর্গ দেখা দিলে
রক্ত গ্রহণের পর যদি উপরোক্ত কোনো লক্ষণ দেখা যায়, তবে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। বিশেষ করে রক্তরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।
রক্তদান মানবতার সেবায় এক মহৎ কাজ হলেও সঠিক পদ্ধতি মেনে এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে না চললে তা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী নিরাপদ ও উপযুক্ত রক্ত নির্বাচন করাই উত্তম।






 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন



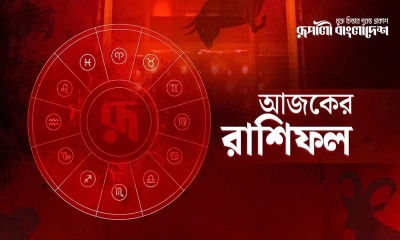
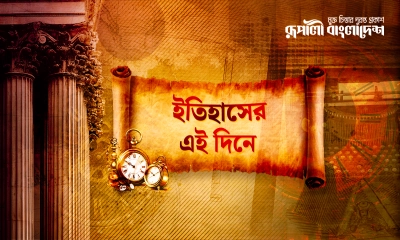






















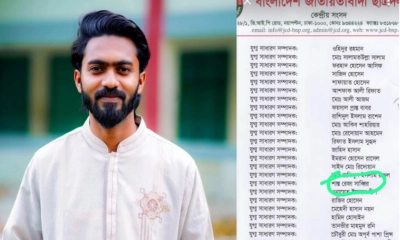


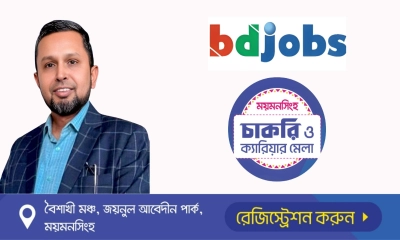







আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন