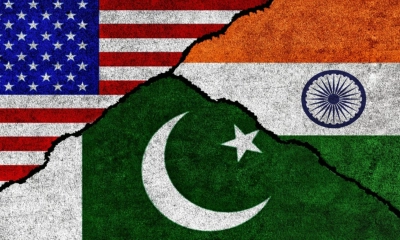তারা বুকভরা পদক আর পিঠে ঝুলানো ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে ঘোরে। নিজেদের পরিচয় দেয় মুসলিম বিশ্বের রক্ষক, ধর্মের পাহারাদার, জাতির অভিভাবক হিসেবে। তারা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে, পারমাণবিক অস্ত্রের গর্বিত অধিকারী এবং এমন একটি রাষ্ট্র চালায়, যা একসময় নিপীড়িতদের আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে উঠেছিল।
কিন্তু যখন গাজা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, যখন ফিলিস্তিনি মায়েরা রক্তাক্ত কাফনে মোড়া সেই বিছানাগুলো জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে, যেখানে একসময় তাদের সন্তানরা ঘুমাত, তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিশ্চুপ থাকে। ধর্মভাষণের পরিচিত বুলি, ‘গভীর উদ্বেগ’ ছাড়া আর কিছুই উচ্চারণ করে না। কেন?
উত্তর জটিল নয়। বরং লজ্জাজনক, ভেতর থেকে পঁচে যাওয়া বাস্তবতা। বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম সামরিক বাহিনী, পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত, ২৪ কোটি মানুষের ওপর কর্তৃত্ববাদী একটি রাষ্ট্র যাদের ক্ষমতা আছে প্রতিরোধ গড়ে তোলার, কিন্তু তারা প্রতীকী প্রতিবাদেরও সাহসটুকু দেখায় না।
কারণ একটাই— এক গভীর ‘নীরব সমঝোতা’। ইহুদিবিরোধী জনগণের আদর্শ নয়, বরং বিদেশি মিত্রদের সঙ্গে গড়ে ওঠা এক আজ্ঞাবহ, মেরুদণ্ডহীন সম্পর্ক; এমন একটি মানসিক কাঠামো, যা পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণির মাঝে প্রোথিত।
এরা উম্মাহর রক্ষক নয় বরং আমেরিকার স্বার্থের পাহারাদার। সাম্রাজ্যের ছায়ায় ঘেরা এই ক্ষমতাকাঠামো, ভণ্ডামির পোশাকে আবৃত, নিজেদের ‘কৌশলগত সংযম’ ও ‘আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা’র নাম দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে।
এই নীরবতার পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। পাকিস্তানি সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের বহু দশকের আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদে অংশগ্রহণ। সেই ষড়যন্ত্রে তাদের অংশগ্রহণ শুধুই প্রশিক্ষণ বা যুদ্ধনীতি শেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদের পাঠানো হয়েছে সামরিক একাডেমিতে, ওয়াশিংটনের আনুগত্য, তেল আবিবের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পশ্চিমা আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতি অবজ্ঞা শেখার জন্য।
তারা ফিরে এসেছে চকচকে সার্টিফিকেট, ফুলে ওঠা অহংকার এবং গাজা থেকে আসা করুণ চিৎকারের প্রতি নিখুঁত নৈর্ব্যক্তিকতা নিয়ে। তাদের চোখ গর্বে উজ্জ্বল, অথচ অন্তর গরিবের রক্তে বধির।
আর সৃষ্টিকর্তা পাকিস্তানের জনগণকে চিরন্তন ধৈর্য দিক, যেন তারা এসব ঘটনা ‘অভ্যন্তরীণ বিষয়’ বলে ভান করে ঘুমায়। তাদের বোঝানো হয়, সেনাপ্রধান নিয়োগ একটি স্থানীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া; জ্যেষ্ঠতা, আনুগত্য, এমনকি কখনও কখনও ‘ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ’ এসবই ভূমিকা রাখে। অথচ বাস্তবতা অনেক বেশি ঔপনিবেশিক। সেনাবাহিনীর প্রধান ঠিক হয় ওয়াশিংটনে, ইসলামাবাদে নয়।
ঐতিহাসিকভাবেই আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক বহাল রাখে পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালে ভারত ভেঙে দুটি রাষ্ট্র গঠন হলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চরম অত্যাচার চালাতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তান। শোষণ, নিপীড়ন, হত্যার ফল দাঁড়ায় ১৯৭১ সালের যুদ্ধে। টানা নয় মাসের যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেও তারা থেমে থাকেনি। নিরীহ বাঙালির রক্ত দিয়ে হলি খেলতে এবং আরও আগ্রাসন চালাতে মিত্র আমেরিকা থেকে পাঠানো হয় সপ্তম নৌবহর, যেখানে ছিল নয়টি যুদ্ধজাহাজ।
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবর, ২০১১ সালের ২ মে আমেরিকা ওসামা বিন লাদেনকে হত্যার জন্য পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে অবস্থিত তার কম্পাউন্ডে অভিযান চালায়। এজন্য ব্যবহার করেছিল পাকিস্তানের ভূখণ্ড। হত্যার পর মার্কিন বিশেষ বাহিনী হেলিকপ্টারে করে বিন লাদেনের মরদেহ পাকিস্তান থেকে নিয়ে যায়। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের দাবি তারা ওয়াশিংটনকে সরাসরি সহায়তা করেনি। অথচ তাদের আকাশসীমা এবং ভূখণ্ড ব্যবহার করে অভিযান চালিয়েছে আমেরিকা।
২০২২ সালের আগস্টের শেষ দিকে পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহার করে আফগানিস্তানে মার্কিন ড্রোন প্রবেশের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল রয়টার্স। সেসময় তালেবান সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রতিবেশী দেশের দিকে আঙুল তুললেও পাকিস্তান সরকার এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এর কিছুদিন পরই রাজধানী কাবুলে ড্রোন হামলা চালিয়ে আল কায়েদা নেতা আয়মান আল-জাওয়াহিরিকে হত্যা করে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী।
সম্প্রতি আরব মুসলিম রাষ্ট্র ইরানের ওপর মার্কিন-‘ইসরায়েল’ নগ্ন আক্রমণ চালালেও শক্তভাবে সহযোগিতার হাত বাড়ায়নি প্রতিবেশী পাকিস্তান। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধেও ‘আধ্যাত্মিক গুরু’ ট্রাম্পের কথায় অস্ত্রবিরতিতেও রাজি হয় ইসলামাবাদ। মসজিদে হামলা চালালেও তার সঠিক জবাব দেয়নি ইসলামাবাদের খাকি পোশাকের কর্তারা।
কিছুদিন আগেও যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন তিনি। তবে বৈঠকের আলোচ্য বিষয় কি ছিল সে বিষয়ে মুখ খোলেনি কোনো পক্ষই। তবে বিশ্লেষকদের মত, এটি যুক্তরাষ্ট্রের পুরনো কৌশল— এক হাতে শক্তি প্রদর্শন, অন্য হাতে দরজার ফাঁক রেখে আলোচনার সুযোগ। তারা প্রশ্ন তুলছেন, যুক্তরাষ্ট্র কি আবারও পাকিস্তানকে ‘আঞ্চলিক ভারসাম্য’ রক্ষার একটি কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে?
এছাড়াও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রাখে দেশটির সামরিক বাহিনী। দেশটির টেলিভিশন চ্যানেল জিও নিউজের সাক্ষাৎকারে ১৫ ফেব্রুয়ারি জমিয়তে উলেমা-ই-ইসলাম (জেইউআই–এফ) প্রধান মাওলানা ফজলুর রেহমান বলেন, পার্লামেন্টে যে অনাস্থা ভোটে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন, সেটি উত্থাপন করা হয়েছিল সাবেক সেনাপ্রধান কামার জাভেদ বাজওয়ার নির্দেশনায়।
ইমরান খান তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেন। যদিও তার ওই অভিযোগ অস্বীকার করে জো বাইডেন প্রশাসন। পরে প্রধানমন্ত্রিত্ব হারানোর জন্য সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল বাজওয়ার ওপর দোষ চাপান ইমরান। পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে ক্ষমতা হারানোর পর থেকে তিনি ধারাবাহিকভাবে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কথা বলে গেছেন। আর এর মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ এখনও জোরদার।
কিন্তু আগ বাড়িয়ে ওয়াশিংটনের পক্ষে সাফাই গান তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামরিক মুখপাত্র মেজর জেনারেল বাবর ইফতিখার। জানান, তিনি তার শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানকে সংসদে অনাস্থা ভোটের প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত হওয়া থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন। এদিকে ২০১৮ সালে ক্ষমতায় আসার আগে ইমরান খানের পরিচিতি ছিল পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ‘ডার্লিং’ বা প্রিয়ভাজন বলে। কিন্তু ক্ষমতাধর সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ইমরান খানের সম্পর্ক ভেঙ্গে গেলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।
বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানায়, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা নিজেদের অরাজনৈতিক মানুষ বলেই ভাবেন। কিন্তু তারা ইমরান খানের সমর্থকদের ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ। সেসময় অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা রাজা শাহরিয়ার বলেন, তিনি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে এত মারাত্মক অসন্তোষ এবং একে ঘিরে এরকম তীব্র রাজনৈতিক মেরুকরণ পাকিস্তানে আর দেখেননি।
পাকিস্তানে বহু দশক ধরে সরাসরি সামরিক শাসন চলেছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হওয়ার পর অন্তত তিনবার সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। যদিও ২০০৮ সালে সরাসরি সেনা-শাসনের অবসান ঘটেছে আনুষ্ঠানিকভাবে। তবে অনেকের বিশ্বাস পাকিস্তানে রাজনীতিকদের পেছনে থেকে এখনো কলকাঠি নাড়ে সামরিক বাহিনীই, ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ আসলে তাদেরই হাতে। ইমরান খান আসলে তাদেরই আশীর্বাদ-পুষ্ট, এটাও মনে করা হয়।
ক্ষমতায় আসার পর দেশীয় রাজনীতির মাঠ থেকে শুরু করে জাতিসংঘের অধিবেশন পর্যন্ত, সর্বত্র পশ্চিমা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইমরান খানের তৎপরতা বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল আমেরিকানদের। ধীরে ধীরে না দেন-দরবার নিয়ে তার সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেয়। দেশের অভ্যন্তরেই আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো। যার প্রভাব গিয়ে ঠেকে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) দেওয়ালে। ক্ষোভ জন্মে জনমনে, সুযোগ হাতিয়ে নেয় ইমরান-বিরোধীরা।
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিশ্লেষকদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণা শক্ত যে, ঐতিহাসিকভাবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে আমেরিকা প্রভাব রাখে মূলত দেশটির সেনাবাহিনীর মাধ্যমে। যেহেতু আধুনিক বিশ্বে সরাসরি কোনো দেশের রাজনীতিতে অপর দেশের হস্তক্ষেপ মেনে নেয় না জনগণ। যা ওয়াশিংটনের একটি কৌশল। আর ট্রাম্পের মুখে মিত্র রাষ্ট্র ভারতের বিপরীতে পাক সেনাপ্রধানের প্রশংসা অস্বাভাবিক, এবং সন্দেহেরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ।
মিডল ইস্ট আইয়ের এক নিবন্ধ অনুসারে, যেসব পাকিস্তানি জেনারেল নিজেদেরকে সার্বভৌমত্বের রক্ষক হিসেবে তুলে ধরেন, প্রকৃতপক্ষে তারা সাম্রাজ্যের ফ্র্যাঞ্চাইজি ম্যানেজার মাত্র। তাদের আসল কর্তা বিদেশি ভাষায় কথা বলেন, ইংরেজিতে। আর ফিলিস্তিনকে দেখেন এক ‘অপ্রয়োজনীয় বিরক্তিকর সমস্যা’ হিসেবে।
বর্তমান সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের কথাই ধরুন। এক কুশলী মিডিয়া যন্ত্র তাকে প্রায় একজন মসীহের আসনে বসিয়েছে। তাকে পবিত্র আল-কোরআনের হাফেজ হিসেবে শ্রদ্ধা জানানো হয়, বাহিনীর নৈতিক দিশারূপে তুলে ধরা হয়। কেউ স্বাভাবিকভাবে আশা করতে পারে যে, যিনি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কণ্ঠস্থ রেখেছেন, তিনি অন্তত গাজায় চলমান গণহত্যা নিয়ে কিছু বলবেন, কিছু প্রতিক্রিয়া দেখাবেন।
কিন্তু না, তিনি নীরব। স্পষ্ট, সুচিন্তিত, আত্মপরিতুষ্ট নীরব। সাম্প্রতিক কূটনৈতিক স্মৃতিতে আসিম মুনিরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ‘পররাষ্ট্র নীতিগত’ পদক্ষেপ হলো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করা।
হ্যাঁ, সেই ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি উৎসবের হাসি হেসে জেরুজালেমকে ‘ইসরায়েলের’ রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ‘শান্তির’ নামে বর্ণবাদের মধ্যস্থতা করেছিলেন। এবং গোলান মালভূমি বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন যেন সেটি কোনো ক্যাসিনোর টোকেন মাত্র। সেই ব্যক্তিই পাকিস্তানের হাফেজ-এ-কোরআন ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের প্রশংসা অর্জন করেছেন। ট্রাম্পও দেরি করেননি, গর্বভরে সেই প্রশংসা গ্রহণ করেছেন।
এটি ছিল এক অদ্ভুত পরস্পর পিঠচাপড়ানো মুহূর্ত, দুই নেতাই আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের তালিকায় থাকলেও গণহত্যার প্রতি তাদের নীরবতা যেন উচ্চ আসনে আসীন। কিন্তু আসিম মুনির কেবল লক্ষণ। রোগ আরও গভীরে, আরও গলিত। পাকিস্তানি জেনারেলদের যে ইহুদিবাদ, তা ‘ইসরায়েলি’ নয়। বরং অনেক বেশি সূক্ষ্ম, কাপুরুষোচিত এবং লোভনীয়। এটি নীরবতায় ইহুদিবাদের গোপন স্বীকৃতি, নির্লজ্জ বাস্তববাদিতা। এটি এমন এক অবস্থান, যেখানে ফিলিস্তিনিদের জীবন মূল্যহীন, কিন্তু আইএমএফের ঋণ বা পেন্টাগনের প্রশংসা অমূল্য।
যখন গাজায় আমেরিকান ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষিত হয়, পাকিস্তানের সেনা কর্মকর্তারা ক্ষুব্ধ হন না বরং কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিবৃতি শব্দচয়ন পুনর্বিবেচনা করেন। আর যখন তারা গাজার কথা বলেন, তখনও কথাগুলো আমলাতান্ত্রিক ব্যুরোক্রেসির শুকনো ভাষায় উচ্চারিত হয়। কোনো আগুন নেই, কোনো তাড়া নেই, কোনো কষ্টের চিহ্ন নেই। শুধু চিরচেনা শোকগান ‘পাকিস্তান নিন্দা করছে…’, আর এর ঠিক পরেই ওয়াশিংটনের উদ্দেশে আরেকটি অনুরোধপত্র আরও সাহায্য, আরও সহযোগিতা চেয়ে।
হাস্যকরভাবে, যখন ভারত নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে হাঁচিও দেয় তখন পাকিস্তানের জেনারেলরা বলিউডের এক্সট্রাদের মতো বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়। ৪৮ ঘণ্টার সীমান্ত উত্তেজনা, আর হঠাৎই জাতিকে উপহার দেওয়া হয় যুদ্ধবিমানের গর্জনে ভরপুর এক ‘ওয়াগনারিয়ান অপেরা’। মন্ত্রীরা পতাকা উড়িয়ে বক্তৃতা দেন, আইএসপিআর টিভি পর্দায় দেশাত্মবোধক সুরের ঢেউ তোলে। তখন বলা হয়, এই সেনারাই জাতির গর্ব, এনারাই মুসলিম সম্মানের রক্ষাকবচ।
কিন্তু যখন ‘ইসরায়েলি’ ট্যাঙ্ক গাজার বুকে ঢুকে পড়ে, হাসপাতাল ধ্বংস করে, শরণার্থী শিবিরে আগুন দেয়—তখন? নীরবতা। প্রতিরোধ তো দূরের কথা, ফিসফিস করেও কিছু বলা হয় না।
বিষয়টি উলটো পথে যেন আরও নির্মমভাবে স্পষ্ট। ফিলিস্তিনে শিশুরা ধ্বংসস্তূপের নিচে দম বন্ধ হয়ে মারা যায়, আর মুসলিম বিশ্বের স্বঘোষিত রক্ষকরা তখন পদক পালিশ করে, ট্রাম্পের উদ্দেশে অভিনন্দনপত্র লিখে। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ তখন রাস্তায় নেমে আসে, ফিলিস্তিনি পতাকা উড়িয়ে প্রতিবাদ জানায়, যা কিছু আছে তা দান করে। কিন্তু তাদের শাসক (সামরিক অভিজাত শ্রেণি) তখনও সাম্রাজ্যবাদী কোমার গভীরে নিথর।
পাকিস্তানে ভাষার বাহার আছে, কর্মের নয়। ‘কাশ্মীর বানেগা পাকিস্তান’—এই স্লোগান যেন একটি চিরস্থায়ী ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। ‘লাব্বাইক ইয়া আকসা’ এই ধ্বনি ব্যানারে চকমক করে। কিন্তু এই সব নাটকীয় ভঙ্গিমা নিজস্ব ভণ্ডামির ভারেই ধসে পড়ে।
ফিলিস্তিন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর চাষ করা পৌরাণিক মহত্ত্বকে এক নির্মম রূপকথায় রূপান্তর করে। ফিলিস্তিনের রক্ত সেই মুখোশ খুলে দেয়, প্রকাশ করে এমন এক শাসকশ্রেণিকে, যারা নিপীড়নের স্থাপত্যে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত, যতক্ষণ না সেই নিপীড়ন পশ্চিমা-অনুমোদিত এবং জায়নবাদী-পরিকল্পিত।
প্রশ্ন উঠতেই পারে গাজা সীমান্তে পাকিস্তান একটি প্রতীকী শক্তি পাঠালে আসলে কী ক্ষতি হতো? সামরিক চিকিৎসকদের একটি ইউনিট? মিশরের মাধ্যমে কূটনৈতিক সাহায্যবাহী একটি কনভয়? কিংবা ‘ইসরায়েলি’ অস্ত্র নির্মাতা কোম্পানির বিরুদ্ধে একতরফা বয়কট ঘোষণা? কিছুই না। কিন্তু তবুও কিছুই করা হয়নি। কেন?
কারণ উদ্দেশ্য কখনোই নিপীড়নের মুখোমুখি দাঁড়ানো নয়, বরং স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। জেনারেলরা জানেন, গাজার পাশে দাঁড়ানো মানে হলো আমেরিকার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া আর সেটি তাদের কল্পনারও বাইরে। পবিত্র আল-কোরআনের একটি আয়াত টুইট করা, শুক্রবার জুমার খুতবায় দুটি ছড়া উচ্চারণ করা, তারপর আবার বাহরিয়া টাউনে পরবর্তী সামরিক প্লট বরাদ্দের দিকে এগিয়ে যাওয়া—এই পথটাই নিরাপদ, আরামদায়ক এবং লাভজনক।
কিন্তু আরও অন্ধকার সম্ভাবনাও আছে, সম্ভবত পাকিস্তানি অভিজাতরা ‘ইসরায়েলে’ নিজেদের প্রতিবিম্বই দেখতে পান। যে সামরিক প্রতিষ্ঠান ঘরে বসে মতপ্রকাশ দমন করে, নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করে, সাংবাদিকদের গুম করে তারা হয়তো ‘ইসরায়েলে’র ‘দক্ষতা’র প্রতি মুগ্ধ। এক ঔপনিবেশিক ফাঁড়াকে কীভাবে নিছক সামরিকীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক শক্তিতে রূপান্তর করা যায়, এটি হয়তো তাদের জন্য ঈর্ষার উৎস। হয়তো এ কারণেই তারা যুদ্ধ কলেজের নামে অফিসারদের পাঠান সেসব ‘ইসরায়েল’-সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিচার শিখতে নয়, নিপীড়ন দক্ষভাবে চালানো শিখতে।
এজন্যই প্রহসন চলতেই থাকে। গাজা জ্বলছে। আর পাকিস্তানি জেনারেলরা পশ্চিমা কূটনীতিকদের সঙ্গে সেলফি তোলেন। একজন হাফেজ-ই-কোরআন এক যুদ্ধাপরাধীর নাম শান্তির নোবেল পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করেন। সামরিক বাজেট ফুলে ফেঁপে ওঠে, কিন্তু নৈতিক সাহস পাতালে তলিয়ে যায়। ব্যবস্থা কাজ করছে, তাদের জন্য।
কিন্তু পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ আরও ভালো কিছুর যোগ্য। তারা কাপুরুষ নয়। তারা বিশ্বাসঘাতক নয়। করাচি থেকে খাইবার পর্যন্ত তারা ফিলিস্তিনের সঙ্গে দাঁড়ায় শুধু প্রতীকীভাবে নয়, বরং এক বেদনাদায়ক সংহতির মাধ্যমে। তারা বোমার শব্দ শুনতে পায়। তারা কাঁদে শোকাহত মায়েদের সঙ্গে। তারা জানে নীরবতা মানেই সহযোগিতা।
তবে দুর্ভাগ্য এই যে, তারা শাসিত হয় এমন এক অভিজাত শ্রেণির দ্বারা, যারা ফিলিস্তিনকে দেখে বিব্রতকর একটি জনসংযোগ সমস্যা হিসেবে আর পেন্টাগনকে দেখে রাবার স্ট্যাম্পধারী অভিভাবক হিসেবে। এই জ্ঞানগত বিভ্রান্তি, এই নৈতিক দ্বিচারিতা অসহনীয়।
স্পষ্ট ভাষা, যে জাতির সেনাবাহিনী গাজার চেয়ে ওয়াশিংটনকে বেশি ভয় পায়, তারা শুধু সার্বভৌম নয় নিজের আত্মাকে ইজারা দিয়েছে।
তাই, সেই পদকগুলো ধুলোয় মিশে যাক। ধর্মভাষণের চিৎকার স্তব্ধ হোক। জেনারেলরা এবং তাদের চাটুকার পরিবৃত অভিজাতরা পশ্চিমা কূটনীতিকদের সঙ্গে তাদের নৈশভোজ উপভোগ করুন। ইতিহাস তাদের দয়াপূর্বক স্মরণ করবে না। গাজার শিশুদের হয়তো গণকবরে শুইয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু পাকিস্তানের একজন ফিল্ড মার্শালকে স্মরণ করা হবে সেই মানুষ হিসেবে, যিনি একজন গণহত্যাকারীর জন্য শান্তির নোবেল পুরস্কার প্রস্তাব করেছিলেন।
যতদিন না পাকিস্তানের সামরিক অভিজাতরা তাদের ঔপনিবেশিক আনুগত্য পরিত্যাগ করে নিপীড়কের পরিবর্তে নিপীড়িতদের পাশে দাঁড়ায়, ততদিন তাদের সব সম্মানজনক উপাধি সেনাপ্রধান, ফিল্ড মার্শাল, স্ট্র্যাটেজিক কমান্ডার—এ সবই অর্থহীন থাকবে। সেগুলো থাকবে কেবল কাপুরুষতার রাজদণ্ড হিসেবে।
আর জনগণ? তাদের উচিত হাততালি দেওয়া বন্ধ করা। ভাগ্যক্রমে এই প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। গণহত্যার সমর্থকদের নিয়ে বীরত্বের পৌরাণিক কাহিনী বলা বন্ধ করুন। ইউনিফর্মকে সম্মানের প্রতীক হিসেবে ভুল চেনা বন্ধ করুন। কারণ, পরের বার যখন আরেকটি গাজা জ্বলবে যেমনটি অনিবার্যভাবে ঘটবে তখন পাকিস্তানের ব্যারাকের নীরবতা হবে সবচেয়ে কড়া প্রতিধ্বনি, যেকোনো বোমার চেয়েও জোরালো।
আর সেই নীরবতাই হবে তাদের উত্তরাধিকার।


-20250706211132.webp)
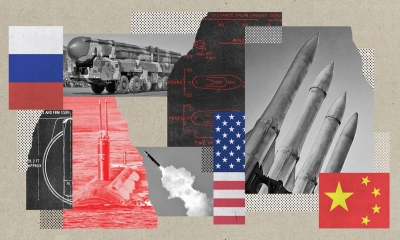



-20250616151543.webp)