বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতির উচ্চতর শিক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। এখান থেকেই জন্ম নেয় আগামী দিনের গবেষক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিল্পপতি ও নীতিনির্ধারকেরা। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান ভিত্তি হলো দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক, গবেষণার অনুকূল পরিবেশ, এবং মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রম। কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত ৫০তম বার্ষিক প্রতিবেদনটি আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার যে হতাশাজনক চিত্র তুলে ধরেছে, তা গভীর উদ্বেগের বিষয়।
সোমবার রূপালী বাংলাদেশের ‘শূন্যতায় মোড়া উচ্চশিক্ষা’ শিরোনামের বিশেষ প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দেশের প্রথম সারির অনেক পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েই পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক নেই। এমনকি অধ্যাপক পর্যায়ের শিক্ষক প্রায় অনুপস্থিত। দেশের অন্যতম পরিচিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গণ-বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী অধ্যাপক মাত্র ১২ জন, যেখানে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ১৭৮ জনের মধ্যে ৯৯ জনই প্রভাষক। অন্যদিকে, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নামকরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েও স্থায়ী অধ্যাপক আছেন মাত্র ২৯ জন। একই অবস্থা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও। গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ২ জন অধ্যাপক, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন, এমনকি বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে একজন মাত্র অধ্যাপক রয়েছেন।
এই পরিস্থিতি শুধু শিক্ষক সংখ্যা কম থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; অনেক শিক্ষকই উচ্চতর ডিগ্রিধারী নন। ইউজিসির তথ্যমতে, দেশের ৫৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ৫ হাজার ২৭৬ জন শিক্ষক ছুটিতে রয়েছেন। অন্যদিকে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র ৬ হাজার ৪০৭ জনের পিএইচডি ডিগ্রি রয়েছে, যা মোট শিক্ষকের তুলনায় খুবই কম।
প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা আরও করুণ। ১০৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশেই খ-কালীন শিক্ষকের সংখ্যাই বেশি, যা ইউজিসির নীতিমালার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। ইউজিসি বলেছে, কোনো বিভাগের খ-কালীন শিক্ষক পূর্ণকালীন শিক্ষকের এক-তৃতীয়াংশের বেশি হতে পারবে না। অথচ বাস্তবে তার উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে। এর পেছনে অন্যতম কারণ হলো- অর্থনৈতিক বিনিয়োগে উদ্যোক্তাদের অনীহা। যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগে যে অর্থ ব্যয় করতে হয়, তা এড়াতেই অনেক প্রতিষ্ঠান প্রভাষক বা খ-কালীন শিক্ষকের ওপর নির্ভর করছে।
শুধু শিক্ষক সংকটই নয়, শিক্ষার্থীর সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করেও শিক্ষক স্বল্পতার যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা আরও উদ্বেগজনক। আন্তর্জাতিক মানদ- অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হওয়া উচিত ১:২০। অথচ দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ অনুপাত ১:৪০ ছাড়িয়ে গেছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১:৪১, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১:৪২, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১:৩৯। এই অনুপাতের ফলে ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকের মানসম্পন্ন একাডেমিক সংযোগ কার্যকরভাবে গড়ে ওঠে না।
এই সবকিছুর প্রভাব পড়ছে দেশের উচ্চশিক্ষার মানে। গবেষণায় পিছিয়ে পড়ছে দেশ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক র্যাঙ্কিংয়ে স্থান পেতে ব্যর্থ হচ্ছে। বিদেশি শিক্ষার্থীও আসছেন না আগের মতো। ২০১৪ সালে যেখানে ১,৬৪৩ জন বিদেশি শিক্ষার্থী পড়তেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, সেখানে ২০২৩ সালে এসে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৮২৬ জনে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও দশ বছরে বৃদ্ধি খুবই সামান্য।
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই অবস্থার জন্য রাজনৈতিকভাবে বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেওয়া, যথাযথ পরিকল্পনা ছাড়া পাঠদান শুরু, এবং অর্থ বরাদ্দের ঘাটতি বড় ভূমিকা রাখছে। ইউজিসি চেয়ারম্যান নিজেই স্বীকার করেছেন, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা হয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনায়, যেখানে পর্যাপ্ত জনবল ও মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। এর ফলে গুণগত শিক্ষার ঘাটতি যেমন তৈরি হচ্ছে, তেমনি গবেষণায়ও পিছিয়ে পড়ছে দেশ।
আমরা মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে কিছু মূল পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে, পিএইচডিধারী, গবেষণায় অভিজ্ঞ ও মেধাবী শিক্ষকদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া; পূর্ণকালীন শিক্ষক ছাড়া পাঠদান কার্যক্রম চালু না করা; শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া; নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের আগে অবকাঠামো, জনবল ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যাচাই করা; ইউজিসিকে আরও শক্তিশালী করে বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্কিং প্রকাশ করা; এবং বিদেশি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে আন্তর্জাতিক মানের কোর্স, স্কলারশিপ ও প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
সর্বোপরি, আমাদের বুঝতে হবে যে উচ্চশিক্ষা কেবল সার্টিফিকেট বিতরণের প্রতিষ্ঠান নয়। এটি একটি দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি। শিক্ষক যদি মেরুদ- হয়, তবে সেই মেরুদ- দুর্বল থাকলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।
আমরা আশা করব, রাজনীতি ও ব্যবসায়িক চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে, উচ্চশিক্ষাকে একটি জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করবেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। কেননা শিক্ষার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে না পারলে, ভবিষ্যতে এর ভয়াবহ মূল্য আমাদেরই দিতে হবে।



 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন




-20251209052553.webp)
-20251209052326.webp)
-20251209052201.webp)
-20251209052038.webp)
-20251209051759.webp)




-20251203221210.webp)
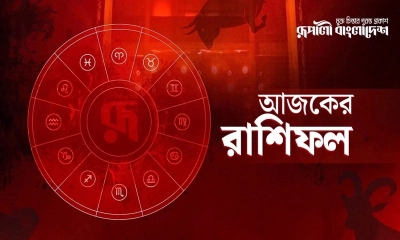






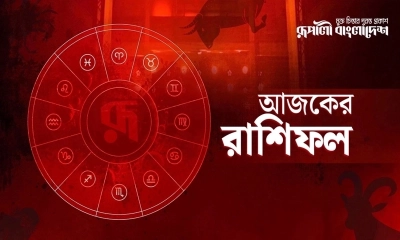


আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন