অন্তর্বর্তী সরকার আগামী জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তা বলা যায়। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গঠিত একটি সরকারের প্রতি জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি। সাধারণত নতুন কোনো সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর স্তরে স্তরে একটি পরিকল্পনা থাকে। সে-অর্থে আমরা বর্তমান সরকারের কাছ থেকে সে ধরনের কিছু জানতে পেরেছিলাম। কাজের কাজ কতটা কি হয়েছে তা সচেতনরা ভাববেন নিশ্চয়। দেশের জনগণের একটি ব্যাপক অংশ একটি পরিবর্তন প্রত্যাশা করে এবং সে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, এটা একটা স্বস্তির বিষয়। তা ছাড়া একটি দেশে দিনের পর দিন অপশাসন, গণতন্ত্রহীনতা, নির্বাচনের পরিবেশ বিনষ্ট করে রাখা ইত্যাদি কোনো বিবেচনায় মেনে নেওয়ার মতো বিষয় নয়, ফলত জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের এক চরম বহির্প্রকাশ ঘটে এবং এই সরকার মানুষের চাওয়া সেই সরকার। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো, যারা ভবিষ্যতে বাংলাদেশ শাসন করবে, রাজনৈতিক নেতারা, যারা জনগণের কাছে ভোট চাইতে যাবেন কিংবা ইতোমধ্যে তা শুরুও করেছেন, এ সবই তাদের জন্য একটা বড় শিক্ষা। দারুণভাবে নন্দিত মানুষও যে চরমভাবে নিন্দিত হতে পারেন, এর সর্বশেষ জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন।
সরকার পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে সর্বত্রই। এখন এ পরিবর্তন নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। এ পরিবর্তন কতটুকু আমাদের আশা-আকাক্সক্ষা ধারণ করতে পেরেছে, কিংবা কার পক্ষে কতটুকু কাজ করছে বা করতে সক্ষম; এসব নিয়ে চর্চা হচ্ছে। এর কারণও রয়েছে। আমাদের মনে আছে, দেশের খেটে খাওয়া যে মানুষটি জুলাই-আগস্টে ছাত্রদের আন্দোলনের সময় তাদের কাছ থেকে রিকশা ভাড়া, বাদাম কিংবা ঝালমুড়ির টাকাটা না নিয়ে আন্দোলনে নিজের অবদান রাখতে চেয়েছে, এ আন্দোলন কি তাদের প্রত্যাশারও প্রতিনিধিত্ব করেনি? ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মূলত ছাত্র, সুশীলসমাজ এবং কয়েকটি রাজনৈতিক দলের আলোচনার ভিত্তিতে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হয় সে-সরকার কি দেশের সব মানুষের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছে? উপদেষ্টা হিসেবে যারা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাদের সবাই কি সত্যিকার অর্থেই সর্বজনগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হতে পেরেছেন? বলা হয়েছিল ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সূচিত বৃহত্তর পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়া এ সরকারে ছাত্রসহ সব শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব থাকবে, তার প্রতিফলন অন্তর্বর্তী সরকারে ছাত্রপ্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে দেখাও গিয়েছে। কিন্তু সমাজের অন্যান্য মানুষ, বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষ, যারা এত বছর ধরে নির্যাতনের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে নিজেদের শরিক করে আন্দোলন সর্বজনীন করে তুললেন, সরকারের ভেতর তাদের মুখচ্ছবি কোথায় এই প্রশ্নটি উঠেছিল। দায়িত্বগ্রহণের পর প্রধান উপদেষ্টা বলেছিলেন, ‘এ সরকারের নিয়োগকর্তা ছাত্র-জনতা, তারা যখন চাইবেন তখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’ একটা দেশ এতদিন ধরে রাজনৈতিক স্বৈরতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হওয়ার পর একটি অরাজনৈতিক শক্তি, যারা সংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছে, তাদের মাধ্যমে কাক্সিক্ষত সংস্কারের পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নির্বাচিত রাজনৈতিক দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে কি সত্যিকারের সভ্যতার পথে আমাদের যাত্রা হবে? এটাই বা কতটুকু নিশ্চিত করে বলা যায়?
আমাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে ১/১১ সরকারের কথা। সে সময়কার সরকারও কিছু সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল, ধারণা করা হয়েছিল এর মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর চরিত্রের পরিবর্তন ঘটবে, দেশে দুর্নীতি এবং অপশাসন কমে আসবে। একটা পর্যায়ে তাদেরও নির্বাচন দিতে হয়েছিল এবং নির্বাচনের পর দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গঠিত একটি সরকার কতটা দানব হয়ে উঠেছিল তা আমরা দেখেছি। কাজেই আজকের সংস্কারের মধ্য দিয়ে আমরা ভবিষ্যতের জন্য সবাই শুদ্ধ হয়ে যাব, এটা কী করে ভাবা যায়? সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সংসদ যখন বহাল নেই, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর যখন কোনো অস্তিত্ব নেই, অথচ ভবিষ্যতের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গঠিত সংসদকে বর্তমান সরকারের সমস্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত বৈধতা দিতে হবে এটা নিয়ে কীভাবে আগাম নিশ্চিত হওয়া যায়? যুক্তি হিসেবে বলা হতে পারে যে এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সরকারের আলোচনা চলমান। এর আলোকে এও বলা সঙ্গত যে, এখানে কি সত্যিই সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে? সেই সঙ্গে এমন শঙ্কারও কি কারণ নেই যে, সরকার গঠনের পর ভবিষ্যতের রাজনৈতিক দলগুলো এগুলো এড়িয়ে যাবে না? এ নিয়ে দ্বিধা নেই যে, বর্তমানের যে বিষয়গুলো সংস্কারের জন্য বিবেচিত হচ্ছে এর সবই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দাবি। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবি বাস্তবে কতটুকু আমাদের তথাকথিত গণতন্ত্রচর্চায় প্রতিভাত হয়েছে, সেসব নিয়ে বিতর্কের ইয়ত্তা নেই। এ বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা চলছে, এরই মধ্যে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল আনুপাতিক হারে সংসদে প্রতিনিধিত্বের কথা বলছে। যারা এর সপক্ষে কথা বলছেন তাদের যুক্তিÑ এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে। তবে বিষয়টি পরিষ্কার নয়। সর্বোপরি সাংবিধানিক সংস্কার ছাড়া নির্বাচনব্যবস্থায় এ ধরনের সংস্কারের কোনো আইনি ভিত্তিও নেই। একই সঙ্গে যেসব কমিশন করা হয়েছে, এর মধ্যে অন্যতম সংবিধান সংস্কার কমিশন। একটি অরাজনৈতিক সরকারের অধীনে একটি কমিশনের সুপারিশের আলোকে দেশের সংবিধান সংস্কার বা পুনর্লিখন হয়ে গেল, বিষয়টা কি আদতে এতটাই সহজ?
এ কথা ঠিক, একটি স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের পতনের পর নতুন সরকারের দায়িত্ব পালনে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয় এবং রাষ্ট্রযন্ত্র স্থিতিশীল করতে বেশ বেগ পেতে হয়। তবে এও মানতে হবে যে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে মানুষের আপৎকালীন চাহিদাকেই এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং খাদ্যের মতো মৌলিক চাহিদাগুলোর জায়গায় মানুষকে আগে স্বস্তি দিতে হবে। এসব মনোযোগের জায়গা সরকারের সংস্কার কর্মসূচি দ্বারা বিঘিœত হচ্ছে কি না তা ভেবে দেখা জরুরি।
বলা হয়েছে, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফসল এ সরকার। খুবই ভালো কথা। তবে কথায় কথায় এবং দফায় দফায় আন্দোলন; বিভিন্ন দাবিনামা পেশ করে অস্থিরতা সৃষ্টির প্রয়াস এবং এর অনেক বিষয়ে নিয়ে সরকারের তরফ থেকে আন্দোলনরত কিছু কিছু পক্ষকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা কোনোভাবেই ছাত্র-জনতার আন্দোলনের চেতনা মহিমান্বিত করে না। এর মধ্যে অনেক বিষয় আছে, যা নীতিগত এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। বছরের পর বছর ধরে রাজনৈতিক সরকারগুলো এ ধরনের অনেক স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে যখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছে, সে ক্ষেত্রে একটি অরাজনৈতিক সরকার এসে সহসাই এর সমাধান দিতে চাইলে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক সরকারব্যবস্থা আরও ভঙ্গুর হয়ে পড়বে। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ এবং অবসরের বয়স বৃদ্ধি, আইন এবং বিচারিক কার্যক্রমে ইতোমধ্যে সাধিত কিছু সংস্কার, অঘোষিতভাবে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা ইত্যাদি। সরকারপ্রধান তার দায়িত্ব নিয়ে প্রথমেই বলেছিলেন, ‘আগে মানুষ সাহস করে কথা বলতে ভয় পেত, এখন নির্ভয়ে কথা বলতে পারবে।’ বাস্তবে কি এমনটা ঘটছে এমন প্রশ্ন আছে। হামলা-মামলার ঘটনাগুলো কি একপাক্ষিক হচ্ছে কিনা তা নিয়েও কথা হয়েছে। মানুষ কি অন্যায়ের প্রতিকার পাচ্ছে? একটি সরকারকে স্বৈরাচার বা ফ্যাসিস্ট, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, সেই দলের সমর্থক যারা তারা কি সবাই সরকারপ্রধান এবং তার সহচরদের অপরাধে সমান অপরাধী? আইন কি সবার জন্য সমানভাবে কাজ করছে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর মানুষ বুঝবে বরাবরই।
দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে হলে নিজস্ব চিন্তা-চেতনা দিয়েই তা করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা দেশগুলোর হনানা ভূমিকার অন্য রকম ভাষা রয়েছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি কিন্তু দিনশেষে প্রশ্ন দাঁড় করে। অনেক কথাই বলতে ইচ্ছা করে। একটু একটু করেই বলতে চাই। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো যতই স্বেচ্ছাচারী বা স্বৈরাচারী হোক না কেন, দিনশেষে রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের ওপরই আস্থা রাখতে হয়। রাজনীতিকদেরও এখন বড় দায়িত্ব পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট থেকে তারা যেন শিক্ষা নেন। নির্বাচন হোক কাক্সিক্ষত সময়ের মধ্যে। প্রশ্নমুক্ত নির্বাচন করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন, সরকার ও প্রশাসনের। রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বও কম নয়। এই নির্বাচন অতীতের যে কোনো নির্বাচনের চেয়ে একটু হলেও ভিন্ন মাত্রার। নির্বাচন কমিশন, সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সামনে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে এর সফলতার জন্য তাতে বিন্দুমাত্র ঢিলেমির অবকাশ নেই। নির্বাচনব্যবস্থার ঔজ্বল্য ফিরিয়ে আনা দেশ, জাতি ও গণতন্ত্রের স্বার্থে খুব জরুরি। এর কোনো বিকল্প নেই। মানুষের প্রত্যাশা যেন পূর্ণ হয়।
লেখক : রাজনীতি-কূটনীতি বিশ্লেষক। অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন


-20251126011429.webp)





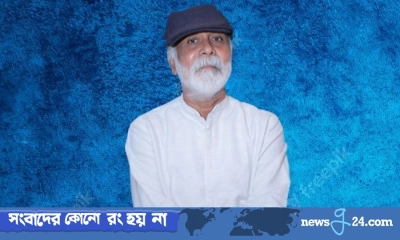








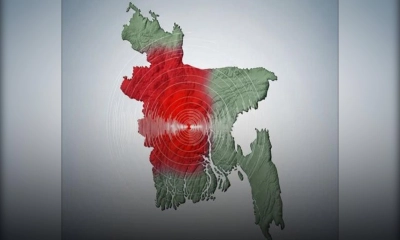
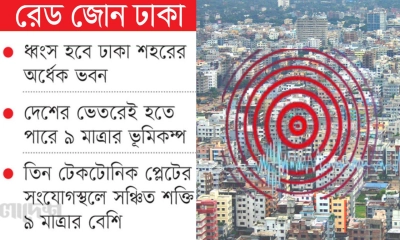


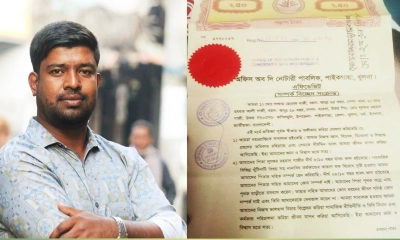




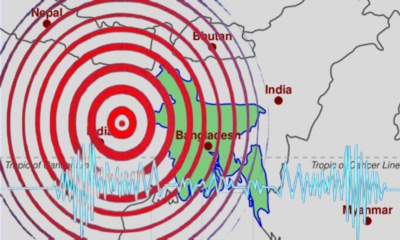



আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন