সরকারি মিডিয়া তালিকাভুক্ত সংবাদপত্র বা সাময়িকীর বিজ্ঞাপনহার সর্বশেষ ২০১৯ সালে বৃদ্ধি করা হয়েছিল। দীর্ঘ ৬ বছর পেরিয়ে গেলেও এ হার পুনর্নির্ধারণ করা হয়নি। এ সময়ে পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কাগজ, মুদ্রণ, সংবাদকর্মীর সম্মানীসহ অন্য সব ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।
একই সঙ্গে সার্বিক মূল্যস্ফীতির কারণে পত্রিকা পরিচালনার ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। বেসরকারি খাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার কয়েক দফা বাড়লেও সরকারি বিজ্ঞাপনহার বাড়েনি।
এ ছাড়া বর্তমানে অনলাইন পত্রিকার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিকাংশ পত্রিকার মুদ্রিত প্রচারসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। ফলে আর্থিক সংকটে ধুঁকছে ঐতিহ্যবাহী সংবাদপত্র শিল্প। তাই প্রচারসংখ্যা না বাড়িয়েই বিজ্ঞাপনের মূল্য বাড়ানোর তাগিদ এ শিল্প সংশ্লিষ্টদের।
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) ২০২৪ সালের তথ্য মতে, এখন দেশে শুধু মিডিয়া তালিকাভুক্ত দৈনিক পত্রিকা আছে ৫৮৪টি। এর মধ্যে ২৮৪টি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।
এদের মধ্যে আবার এমন কিছু পত্রিকা রয়েছে, যেগুলোর নাম পাঠকেরা কখনো শোনেনইনি। বাজারে নামসর্বস্ব এসব পত্রিকা খুঁজে পাওয়াটাও দুঃসাধ্য। কারণ, ঢাকার হকাররা বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে বিলি করেন কমবেশি ৫৪টি দৈনিক পত্রিকা। এই ৫৪টির সব কটিও সব সময় পাওয়া যায় না। কিছু পত্রিকার দেখা পাওয়া যায় শুধু নগরের কিছু দেয়ালে।
ডিএফপির হিসাবে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে ৫৭টি দৈনিক পত্রিকা প্রতিদিন ১ লাখ বা তার চেয়ে বেশি কপি ছাপা হয়। যদিও এই পত্রিকাগুলোর বেশির ভাগই ঢাকার হকারদের দুই সমিতির তালিকায় নেই। অর্থাৎ এগুলো ঢাকার বাজারে পাওয়া যায় না।
তবুও তারা সরকারি মূল্যে বিজ্ঞাপন পায়, যা সম্পূর্ণ অন্যায্য দাবি করে সিনিয়র সাংবাদিক এম এ আজিজ রূপালী বাংলাদেশকে বলেন, একটি সংবাদপত্রের সঙ্গে অনেক হিসাব-নিকাশ জড়িত। ওয়েজ বোর্ড এবং মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে এর সরকারি বিজ্ঞাপনের মূল্য নির্ধারণ করা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে এটি হচ্ছে না।
অনেকে পত্রিকা বের করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায়। তারা ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন তো দূরে থাক, ঠিকমতো বেতনই দেয় না। শুধু বিজ্ঞাপনের মূল্য বাড়ানো নিয়ে চিন্তিত। এতে মূল ধারার পত্রিকাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
তাই সরকারের উচিত হবে মূল ধারার পত্রিকাগুলো যথাযথভাবে অডিটের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের মূল্য নির্ধারণ করা। যেহেতু জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে, আগের তুলনায় স্বাভাবিক হারেই বেড়েছে পত্রিকা প্রকাশের খরচও। তাই বিষয়টি সরকারের বিবেচনা করা উচিত বলে আমি মনে করি।
জানা গেছে, একটি প্রথম সারির পত্রিকার দৈনিক খরচের হিসাবগুলো দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এর একটি হলো প্রচলিত খরচ। এগুলো হলো দৈনন্দিন কার্যক্রম চালাতে যা যা খরচ হয় যেমন-সম্পাদনা ও সংবাদ সংগ্রহে নিয়োজিত সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার ও সম্পাদকদের বেতন, ফিল্ড রিপোর্টিংয়ের জন্য যাতায়াত ও আবাসন খরচ, সংবাদ সংস্থা (যেমন : এএফপি, রয়টার্স) থেকে সাবস্ক্রিপশন ফি, তথ্য যাচাই ও গবেষণা ব্যয়।
এরপর রয়েছে প্রোডাকশন বা ছাপার খরচ, কাগজ (নিউজপ্রিন্ট) কেনা, প্রিন্টিং মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ, কালির খরচ, ছাপাখানার কর্মীদের বেতন। বিতরণ খরচের মধ্যে রয়েছে পরিবহন ব্যয় (গাড়ি, বাইক, রিকশা), হকার বা বিক্রেতাদের কমিশন, স্টোর বা নিউজস্টল ভাড়া ও লজিস্টিকস খরচ।
এ ছাড়া রয়েছে ব্যবসা ও প্রশাসনিক খরচ যেমন অফিসভাড়া, ইউটিলিটি বিল (বিদ্যুৎ, পানি, ইন্টারনেট), মানবসম্পদ বিভাগ, হিসাব বিভাগ, আইন ও প্রশাসন বিভাগ, সফটওয়্যার বা কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, ট্যাক্স ও লাইসেন্স ফি। এর বাইরেও রয়েছে বিজ্ঞাপন ও মার্কেটিং খরচ, যেমন-বিজ্ঞাপন প্রচার, প্রচারমূলক উপহার বা ইভেন্ট ও মার্কেটিং টিমের বেতন।
একটি সংবাদপত্রের জন্য রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের বিষয়ও। যেমন- ছাপাখানার যন্ত্রপাতি (মেশিনারিজ) কেনা, জমি বা ভবন কেনা, কম্পিউটার ও আইটি অবকাঠামো, সফটওয়্যার বা লাইসেন্স কেনা (যেমন-ডিজাইন টুলস, সিএমএস)। এর বাইরেও অতিরিক্ত কিছু খরচ রয়েছে, যেমন-ডিজিটাল সংস্করণ পরিচালনা, ওয়েবসাইট হোস্টিং, অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, এসইও, সাইবার সিকিউরিটি ইত্যাদি।
রয়েছে আইনসংক্রান্ত কিছু ব্যয়ও, যেমন-মামলা-মোকদ্দমা, কপিরাইট ইস্যু, সংবাদসংক্রান্ত অভিযোগ মোকাবিলা। বিমা ও সুরক্ষা খরচও রয়েছে এসবের মধ্যে।
ওয়েজ বোর্ড অনুসারে রিপোর্টারদের বেতনসহ প্রথম সারির পত্রিকার মাসিক ব্যয় অন্তত ৬০ লাখ টাকা। পত্রিকার জন্য কাগজ কেনার দাম পড়ে মাসে ৪০ থেকে ৫০ লাখ টাকা। সার্কুলেশন খরচ রয়েছে ৮ থেকে ১০ লাখ টাকা।
এর বিপরীতে সরকারি-বেসরকারি বিজ্ঞাপন থেকে আয়ের পরিমাণ মাত্র ৪০ থেকে ৬০ লাখ টাকা। দু-একটি পত্রিকার আয়-ব্যয় সমান সমান হলেও বেশির ভাগ পত্রিকাকেই মাসের পর মাস ভর্তুকি দিয়ে চালাতে হচ্ছে। ডিএফপির বাড়তি দাম পাওয়ার জন্য সার্কুলেশনের হিসাবেও নিতে হয় কৌশলের আশ্রয়।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এর থেকে বের হয়ে আসার একমাত্র উপায় সরকারি বিজ্ঞাপনের দাম বাড়ানো। আর সার্কুলেশনের সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য পত্রিকার সার্কুলেশনের সংখ্যা কমিয়ে বিজ্ঞাপনের মূল্য বাড়ানোর তাগিদ সংবাদপত্র শিল্পের সংশ্লিষ্টদের।
দেশে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িকীর মিডিয়া তালিকাভুক্তি, নিরীক্ষা এবং প্রচারসংখ্যা নির্ধারণ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা ডিএফপি।
কিন্তু ডিএফপির নির্ধারণ করা পত্রিকার প্রচারসংখ্যায় রয়েছে বিস্ময়কর তথ্য। সরকারি হিসাব বলছে, ১৭ কোটি মানুষের দেশে প্রতিদিন সব মিলিয়ে ১ কোটি ৮৫ লাখ কপির বেশি পত্রিকা ছাপা হচ্ছে! অর্থাৎ প্রতি ৯ জনের বিপরীতে এক কপি পত্রিকা ছাপা হচ্ছে। বেশির ভাগ পত্রিকার মিডিয়া তালিকাভুক্তি এবং প্রচারসংখ্যা নির্ধারণে বড় ধরনের জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া হয়।
এর সঙ্গে জড়িত ডিএফপির কিছু অসাধু কর্মচারী। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপও কাজ করে। দেশে বাস্তবে এক কপি পত্রিকা একাধিক মানুষ পড়ে থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে একটি পত্রিকা ৮-১০ জনও পড়ে থাকেন। এই হিসাবে দেশে ছাপা পত্রিকার মোট পাঠক ১ কোটি ৮৬ লাখ বলে ২০২৩ সালে বহুজাতিক গবেষণা ও জরিপ প্রতিষ্ঠান কান্তার এমআরবি পরিচালিত জরিপে উঠে এসেছে।
মিডিয়া তালিকাভুক্তি বলতে সরকারের তালিকাভুক্ত সংবাদপত্র হিসেবে স্বীকৃত হওয়া এবং সরকারি ও আধা সরকারি সংস্থাগুলোর বিজ্ঞাপন প্রচারের যোগ্যতা অর্জন করাকে বোঝায়। এই তালিকা অনুযায়ী সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। যা বছরের পর বছর একই রয়ে যাচ্ছে।
বেশির ভাগ পত্রিকার মিডিয়া তালিকাভুক্তি এবং প্রচারসংখ্যা নির্ধারণে বড় ধরনের জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া হয়। মূলত সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়া আর রেয়াতি হারে (নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে কর) শুল্ককর দিয়ে নিউজপ্রিন্ট আমদানি সুবিধার জন্য পত্রিকার প্রচারসংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেখানো হয়। পত্রিকার প্রচারসংখ্যার ওপর সরকারি বিজ্ঞাপনের দর এবং নিউজপ্রিন্টের প্রাপ্যতা নির্ভর করে।
ডিএফপির হিসাবে যেসব বাংলা দৈনিক পত্রিকার প্রচারসংখ্যা ১ লাখ ৪১ হাজার বা এর চেয়ে বেশি (সর্বোচ্চ ৫ লাখ ২১ হাজার ২১১), সেসব পত্রিকার জন্য সরকারি বিজ্ঞাপনের দর প্রতি কলাম-ইঞ্চি ৯০০ টাকা।
প্রচারসংখ্যা কম হলে সরকারি বিজ্ঞাপনের দরও কমে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিকের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের সর্বনিম্ন দর প্রতি কলাম-ইঞ্চি ৩৫০ টাকা। এই দর বাড়ানোর এখন সময় এসেছে বলে দাবি করছেন সাংবাদিক নেতারা। না হলে এ ধরনের দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে না।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে উল্লেখ করে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী রূপালী বাংলাদেশকে বলেন, আমরা বরাবরই এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলে আসছি। সম্প্রতি তথ্য উপদেষ্টার সঙ্গে আমাদের বৈঠক ছিল।
সে বৈঠকেও আমরা সংবাদপত্রের সরকারি বিজ্ঞাপনের দর বাড়ানোর প্রস্তাব তুলে ধরেছি যুক্তিসহ। শুধু বাংলা পত্রিকা নয়, ইংরেজি পত্রিকারও একই হারে বিজ্ঞাপনের দর বাড়ানোর কথা আমরা বলেছি। জানতে পেরেছি এ বিষয়ে কাজ চলছে। একটি শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে এর বিকল্প নেই বলে আমি মনে করি।
একই কথা বলেন সংগঠনটির আরেক নেতা দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত চিফ রিপোর্টার বাছির জামাল।
বিএফইউজের সিনিয়র এই সহকারী মহাসচিব রূপালী বাংলাদেশকে বলেন, অবশ্যই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবাদপত্রের সরকারি বিজ্ঞাপনের মূল্য বাড়াতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পত্রিকার ব্যয় বেড়েছে। কাগজের দাম বেড়েছে। পত্রিকার পরিচালন ব্যয় বেড়েছে। কিছু কিছু নামসর্বস্ব পত্রিকা এসব কিছুর তোয়াক্কা না করেই সর্বোচ্চ মূল্য পাচ্ছে।
আর যারা সত্যিকার অর্থেই বাজারে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে চাচ্ছে তাদের দর সর্বনিম্ন। এই ধারা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে এবং অবশ্যই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিজ্ঞাপনের দর ২ হাজার থেকে ২১শ টাকা করা উচিত বলে আমি মনে করি।
জানা যায়, ছাপা পত্রিকার বড় অংশই বিক্রি হয় রাজধানী ঢাকায়। আর ঢাকার মোট জনসংখ্যা এখন ২ কোটি ১০ লাখ। পাঠকের কাছে পত্রিকা পৌঁছে দেওয়ার প্রধান মাধ্যম হকার। ঢাকা মহানগর ও এর আশপাশের (সাভার, নবীনগর, সিংগাইর, গাজীপুর, দাউদকান্দি, মুন্সীগঞ্জ পর্যন্ত) এলাকায় সংবাদপত্র বিলি করে থাকে হকারদের দুটি সংগঠন। এর একটি ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স বহুমুখী সমবায় সমিতি।
আরেকটি হলো সংবাদপত্র হকার্স কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি। সমিতি দুটির নেতারা জানিয়েছেন, এই দুই সমিতির বাইরে আর কেউ ঢাকা মহানগরে সংবাদপত্র বিলি করে না। ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স বহুমুখী সমিতির কাছ থেকে জানা যায়, তারা নিয়মিত ৫২টি পত্রিকা বিলি করেন। তারা প্রতিদিন আনুমানিক সাড়ে তিন লাখ কপি পত্রিকা বিলি করেন।
আর হকার্স কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি বলছে, তারা দৈনিক ৪৪টি পত্রিকার ৭০-৭৫ হাজার কপি বিলি করে। এই দুই সমিতি যেসব পত্রিকা বিলি করে, তার নির্দিষ্ট তালিকা আছে। তালিকা দুটি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, হকার্স কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি যে ৪৪টি পত্রিকা বিলি করে, ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স বহুমুখী সমিতির তালিকায়ও তার ৪২টি আছে।
অর্থাৎ এই দুটি সমিতি ঢাকায় বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে মোট ৫৪টি দৈনিক সংবাদপত্র বিক্রি করে। সব মিলিয়ে প্রতিদিন গড়ে সোয়া চার লাখ কপি পত্রিকা বিক্রি হয়। সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় প্রথম আলো ও বাংলাদেশ প্রতিদিন। ১০-১৫টি পত্রিকা বাদে অন্যগুলোর বিক্রির সংখ্যা ১০০ থেকে ৫০০ কপির মতো।
এর বাইরে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় দেয়ালে কিছু পত্রিকা দেখা যায়। আর কিছু পত্রিকা বের হয় সরকারি বিজ্ঞাপন বা ক্রোড়পত্র পেলে। যখন যে প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দেয়, সে প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারি কিছু দপ্তরে এসব পত্রিকার কপি পৌঁছে দেওয়া হয় নিজেদের উদ্যোগে।
আর কিছু পত্রিকা হাতে গোনা কয়েক কপি ছাপা হয়, যেগুলো কিছু নির্দিষ্ট সরকারি দপ্তর এবং যাদের নিয়ে বিশেষ সংবাদ করা হয়, তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই পত্রিকাগুলো ‘দেয়াল পেস্টিং’ পত্রিকা এবং ‘আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা’ হিসেবে পরিচিত।
এ ব্যাপারে সম্পাদক পরিষদের কোনো নেতার বক্তব্য পাওয়া না গেলেও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (একাংশ)-এর সাধারণ সম্পাদক খুরশীদ আলম রূপালী বাংলাদেশকে বলেন, সংবাদপত্র শিল্প একটা কঠিন সময় পার করছে। আমরা এর বিকাশে কাজ করে যাচ্ছি। বিজ্ঞাপনের হার, সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা নিশ্চিত করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কাজ করে যাচ্ছি।
বিজ্ঞাপনের হার বাড়ানোও এর মধ্যে অন্যতম। একটি পত্রিকা তখনই ভালো করবে, যখন এর আয়ের নিশ্চয়তা থাকবে। আর আয়ের অন্যতম উৎস সরকারি বিজ্ঞাপন। যেসব নামকাওয়াস্তে সংবাদপত্র রয়েছে, সেগুলোকেও খুঁজে বের করতে হবে। সরকার যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে ব্যাপারটাও আমাদের দেখতে হবে।
প্রায় একই কথা বলেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি আবু সালেহ আকন। রূপালী বাংলাদেশকে তিনি বলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর ব্যয় বেড়েছে।
মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক পত্রিকার পরিচালন ব্যয়ও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। আগে কাগজের মূল্য কেজিতে ছিল ৪০ থেকে ৫০ টাকা, যা এখন ৭০ থেকে ৮০ টাকা হয়ে গেছে। ইউটিলিটি খরচ, বেতন-ভাতা সব বেড়েছে; কিন্তু সেই তুলনায় বাড়েনি সরকারি বিজ্ঞাপনের মূল্য।
বেসরকারি বিজ্ঞাপনের তো কোনো সুনির্দিষ্ট হিসাব নেই। সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপরই মূলত একটি পত্রিকার ভিত তৈরি হয়। তাই আমি মনে করি, এখন সময় এসেছে সরকারি বিজ্ঞাপনের মূল্য বাড়ানোর।


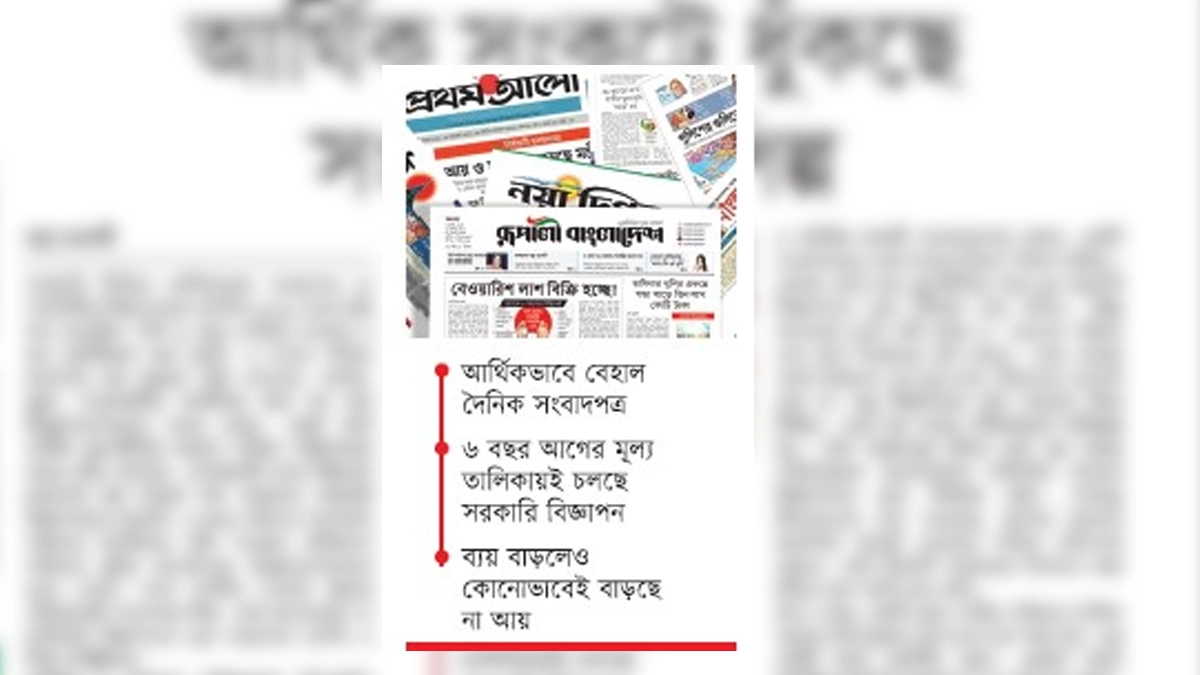
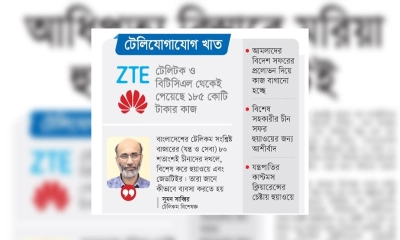
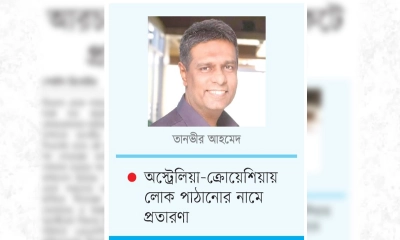

 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন




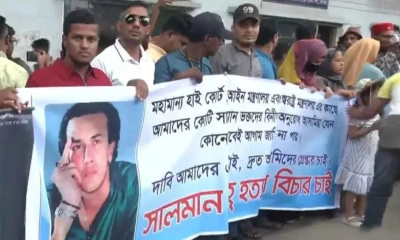




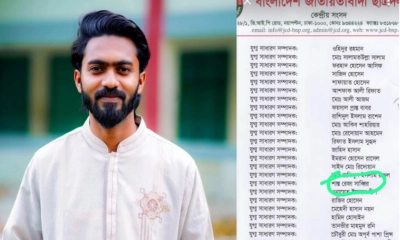

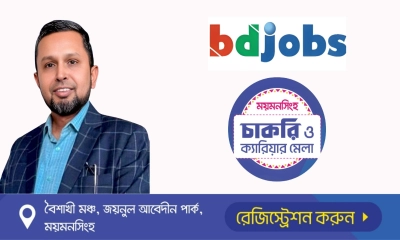








আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন