গণতন্ত্র এমন একটি শাসনব্যবস্থা, যেখানে শাসনের ক্ষমতা জনগণের হাতে নিহিত থাকে। এই ব্যবস্থায় জনগণ নিজেরাই শাসনের উৎস, কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রক। তবে গণতন্ত্রের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করে জনগণের সচেতনতা, অংশগ্রহণ, দায়িত্ববোধ ও যুক্তিবোধের ওপর। আর এই গুণাবলি একমাত্র অর্জন করা সম্ভব শিক্ষা, বিশেষত রাজনৈতিক ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে। তাই বলা চলে, গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখার পূর্বশর্ত হলো শিক্ষিত, সচেতন, যুক্তিনির্ভর ও মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলা। একবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্র বিশ্বের বহুল প্রচলিত ও সমাদৃত শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। পূর্বে উপনিবেশ শাসিত ও সামরিক শাসনে বন্দি বহু দেশ এখন নিজেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু গণতন্ত্রের বাহ্যিক রূপ অর্থাৎ নির্বাচন, ভোটাধিকার ও সংসদ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই এর আত্মা অনুপস্থিত। কারণ গণতন্ত্র কেবল কাঠামোগত বিষয় নয়, এটি একটি মানসিকতা, একটি মূল্যবোধ, একটি চর্চা। এই চর্চা গড়ে উঠে শিক্ষা ও চিন্তাচর্চার মাধ্যমে। বর্তমান বিশ্বে আমরা এমন একটি সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি, যেখানে গণতন্ত্রের নামে অনেক জায়গায় সংখ্যাগরিষ্ঠের দমন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, নির্বাচনী অনিয়ম ও রাজনৈতিক মিথ্যাচার ঘটছে। তথাকথিত জনপ্রিয়তাবাদী শাসকেরা গণতন্ত্রের রূপ ধরে রেখে তার মর্মবস্তুকে বিকৃত করছেন। প্রপাগান্ডা, তথ্য বিকৃতি, বিভ্রান্তিকর বক্তব্য ও জাতিগত বিদ্বেষের মাধ্যমে ভোটারদের প্রভাবিত করে তারা ক্ষমতায় আসছেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগেÑ কেন জনগণ এসব অসৎ, অযোগ্য, কিংবা একনায়ক প্রবণ নেতাকে ভোট দেয়? উত্তরটি সহজÑশিক্ষার অভাব। জন স্টুয়ার্ট মিল তার প্রখ্যাত গ্রন্থ ঈড়হংরফবৎধঃরড়হং ড়হ জবঢ়ৎবংবহঃধঃরাব এড়াবৎহসবহঃ এ গণতন্ত্রের সাফল্যের দুটি প্রধান শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেনÑসার্বজনীন ভোটাধিকার এবং সার্বজনীন শিক্ষা। মিল মনে করেন, ভোটাধিকার তখনই অর্থবহ হয় যখন নাগরিক সেই অধিকারের সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হন। একজন অশিক্ষিত, অচিন্তাশীল কিংবা আবেগতাড়িত ভোটার যেমন- একজন দুর্নীতিবাজ বা গোঁড়াচিন্তাধারার নেতাকে নির্বাচিত করতে পারেন, তেমনি সেই ভোটার রাষ্ট্রের দুর্নীতি, অনিয়ম ও অবিচারের বিরুদ্ধে সচেতন প্রতিরোধ গড়তে অক্ষম হন। এভাবেই গণতন্ত্র কেবল একটি সংখ্যার খেলা হয়ে দাঁড়ায়Ñ যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঠিক নয়, বরং প্রবল। একটি সত্যিকারের গণতন্ত্র গড়ে ওঠে তখনই, যখন নাগরিকরা তথ্য ও মতের বৈচিত্র্য গ্রহণে সক্ষম হয়, যখন তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে, বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণার ফাঁদে না পড়ে যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ করতে পারে। এই বিশ্লেষণক্ষমতা গড়ে ওঠে শিক্ষা থেকে। শিক্ষা কেবল তথ্য দেয় না; এটি ন্যায়বোধ, সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ, সহিষ্ণুতা, রাষ্ট্রচিন্তা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার চর্চা শেখায়। এসবই গণতান্ত্রিক আচরণের অবিচ্ছেদ্য উপাদান। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গণতন্ত্র এখনো একটি পদ্ধতির বেশি কিছু নয়। একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্বাচন হচ্ছে, জনগণ ভোট দিচ্ছেÑকিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের জবাবদিহিতা, প্রশাসনের নিরপেক্ষতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সংবিধানের বাস্তব প্রয়োগ এখনো সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এসব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন এমন এক নাগরিক সমাজ, যারা চিন্তাশীল, দায়িত্বশীল এবং রাষ্ট্রের ওপর সদা নজরদারি রাখতে সক্ষম। এই নাগরিক সমাজ গড়ে তোলার একমাত্র উপায় হলো নৈতিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা। শুধু সাধারণ শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, দরকার গণতান্ত্রিক শিক্ষা। স্কুলপর্যায়ে গণিত, বিজ্ঞানের পাশাপাশি শেখাতে হবে সহিষ্ণুতা, যুক্তিচর্চা, মানবাধিকার, ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আলোচনা ও বিতর্কের সৌন্দর্য, এবং আইন মেনে চলার অভ্যাস। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সচেতন প্রতিযোগিতা, বিরোধী দলের প্রতি সহনশীলতা এবং জনগণের অধিকার সংরক্ষণে সদিচ্ছা যদি নাগরিক সমাজে প্রতিফলিত না হয়, তাহলে নির্বাচন যতই নিয়মিত হোক, গণতন্ত্র হবে খোলস মাত্র। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উদাহরণ বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, কানাডা, জার্মানিÑ এসব দেশ গণতন্ত্রের সূচকে শীর্ষে রয়েছে। কেন? কারণ সেখানে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ছোটবেলা থেকেই গড়ে ওঠে। শিক্ষার্থীরা শেখে কীভাবে যুক্তির ভিত্তিতে মত প্রকাশ করতে হয়, অন্যের মতকে সম্মান করতে হয় এবং সমাজে সক্রিয় নাগরিক হিসেবে অংশ নিতে হয়। সেখানে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, পাঠ্যক্রমে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়। বাংলাদেশে এর উল্টো চিত্র লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষা ও সার্টিফিকেটমুখী। পাঠ্যবইতে কিছু তথ্যগত সংজ্ঞা থাকলেও রাজনৈতিক চিন্তাচর্চার সুযোগ খুবই সীমিত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বিতর্ক, মতবিনিময় কিংবা চিন্তার স্বাধীনতা চর্চা প্রায় অনুপস্থিত। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাবশালী হস্তক্ষেপ শিক্ষার পরিবেশকেই কলুষিত করে তুলছে। ফলে শিক্ষা যেমন মুক্ত চিন্তার অনুশীলন হতে পারছে না, তেমনি নাগরিকদের মধ্যেও গড়ে উঠছে না গণতন্ত্রের আত্মিক চেতনা। সচেতনতা ছাড়া অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে। একজন নাগরিক যদি বুঝতেই না পারে তার অধিকার কী, কীভাবে তা রক্ষা করতে হয়, তাহলে তার ভোটাধিকার কিংবা বাকস্বাধীনতা থাকবে শুধু কাগজে। শিক্ষা ছাড়া সচেতনতা জন্ম নেয় না। তাই গণতন্ত্রে শিক্ষা শুধু সহায়ক নয়Ñঅবিচ্ছেদ্য। গণতন্ত্রের সংকট অনেক সময় ‘গণতন্ত্র’ শব্দটিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে। ব্যর্থতা, দুর্নীতি কিংবা একনায়কতন্ত্রের অভিযোগ উঠলে বলা হয়, গণতন্ত্র কাজ করছে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দোষ গণতন্ত্রের নয়, দোষ সেই সমাজের, যে সমাজে শিক্ষা ও চিন্তার কাঠামো সঠিকভাবে গড়ে ওঠেনি। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে আগে সেই কাঠামো নির্মাণ করতে হবে। এই বাস্তবতায় শিক্ষা খাতকে জাতীয় অগ্রাধিকার দিতে হবে। পাঠ্যক্রমে যুক্তিবাদ, মানবিকতা ও সমসাময়িক রাজনীতিচর্চার জায়গা দিতে হবে। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে গণতন্ত্র, নাগরিক অধিকার, নৈতিকতা এবং অংশগ্রহণমূলক শাসনের ধারণা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। শিক্ষক সমাজকে করতে হবে স্বাধীন ও প্রজ্ঞাবান। শিক্ষা হতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবিক ও যুক্তিনিষ্ঠ। পরিশেষে বলা যায়, গণতন্ত্রের টিকে থাকার জন্য শুধু একটি সংবিধান, একটি নির্বাচন কমিশন কিংবা একটি সংসদ যথেষ্ট নয়। গণতন্ত্র টিকে থাকে জনগণের অন্তরের ভেতরে, তাদের বিশ্বাস, নৈতিকতা ও সচেতনতায়। এই ভিত নির্মাণের কাজ করে শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া গণতন্ত্র এক খাঁচাবন্দি পাখিÑযার গলা আছে, কিন্তু সুর নেই। তাই গণতন্ত্রকে জীবন্ত রাখতে হলে শিক্ষা হতে হবে আলো, যা প্রতিটি নাগরিকের চিন্তায় জ্বলে উঠবে। তবেই সম্ভব হবে এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলা, যেখানে সত্যিকারের জনগণের শাসন কেবল কাগজে নয়Ñ বাস্তবেও প্রতিষ্ঠিত হবে।
মো. শামীম মিয়া
প্রাবন্ধিক ও
শিক্ষার্থী, ফুলছড়ি সরকারি কলেজ
জুমারবাড়ী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।
shamim.writer2025@gmail.com



















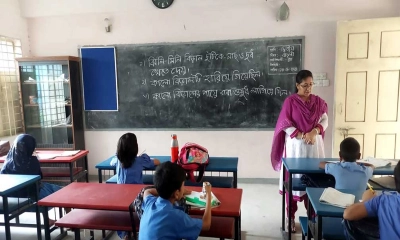







আপনার মতামত লিখুন :