কারফিউ হলো এমন একটি আদেশ, যা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা বা জনগোষ্ঠীর ওপর চলাফেরার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।
সাধারণত কারফিউর আওতায় থাকা ব্যক্তিদের সন্ধ্যা ও রাতের নির্দিষ্ট সময় ঘরের ভেতরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। এ আদেশ প্রায়ই সরকার বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার পক্ষ থেকে জারি করা হয়।
অপরদিকে, ১৪৪ ধারা বাংলাদেশের ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা, যা ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারার অনুরূপ ও অভিন্ন। এই ধারার আওতায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সভা-সমাবেশ, মিছিল, জমায়েত বা আগ্নেয়াস্ত্র বহনের মতো কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করতে পারেন।
কারফিউ কখন ও কেন জারি করা হয়?
কারফিউ জারি করা হয় জননিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে যখন পরিস্থিতি চরমভাবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এটি একটি কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট এলাকা বা গোটা শহরে সাধারণ জনগণের চলাচল সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়।
কারফিউর সময় লোকজনকে ঘরে অবস্থান করতে বলা হয় এবং বাইরে বের হলে গ্রেপ্তার, জরিমানা এমনকি গুলিবর্ষণের মতো কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, বিশেষ করে সামরিক কারফিউর ক্ষেত্রে।
ধারণত দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, সন্ত্রাসী হামলা, মহামারি বা রাজনৈতিক সহিংসতার মতো সংকটের মুহূর্তে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যাতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।
কারফিউর মূল উদ্দেশ্য হলো—সহিংসতা রোধ, মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করা। এটি সরকারের একটি জরুরি প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ, যাতে নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং সমাজে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে কারফিউ তুলে নেওয়া হয়।
১৪৪ ধারা কেন ও কখন জারি হয়?
১৪৪ ধারা সাধারণত জনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জরুরি ভিত্তিতে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জারি করা হয়, যখন কোনো এলাকায় সম্ভাব্য সংঘর্ষ, সহিংসতা, বা বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা দেখা দেয়। এটি মূলত জনসমাবেশ, মিছিল, বিক্ষোভ বা বড় ধরনের জমায়েতকে সীমাবদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যাতে সামাজিক অস্থিরতা ও অশান্তি সৃষ্টি না হয়।
যেমন- রাজনৈতিক উত্তেজনা, ধর্মীয় বা সম্প্রদায়ভিত্তিক সংঘাত, কিংবা কোনো ধরনের অসাধু কার্যকলাপের আশঙ্কা থাকলে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এই ধারার আওতায় চার বা তার বেশি ব্যক্তির একসঙ্গে জমায়েত করা নিষিদ্ধ থাকে এবং যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে।
১৪৪ ধারার সময়সীমা সাধারণত সীমিত, যেমন কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত হতে পারে, যা পরিস্থিতির প্রকারভেদে বাড়ানো বা কমানো হয়। এর মাধ্যমে শান্তি বজায় রেখে জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এই ধারা তুলে নেওয়া হয়।
কারফিউ ও ১৪৪ ধারার মধ্যে পার্থক্য
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রশাসন কখনো ১৪৪ ধারা, কখনো কারফিউ জারি করা হয়। তবে এই দুইয়ের মধ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য।
১৪৪ ধারা মূলত সাময়িকভাবে জনসমাবেশ, সভা, মিছিল ও বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করার আইনি ব্যবস্থা। এতে একসঙ্গে চার বা ততোধিক ব্যক্তি জমায়েত হতে পারেন না। সাধারণত রাজনৈতিক উত্তেজনা, ধর্মীয় সংঘাত বা বড় সমাবেশে সহিংসতার আশঙ্কা দেখা দিলে স্থানীয় প্রশাসন নির্দিষ্ট এলাকা ও সময়ের জন্য এই ধারা জারি করে। এটি অমান্য করলে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে ও মামলাও হতে পারে।
অন্যদিকে, কারফিউ হলো আরও কঠোর ব্যবস্থা, যেখানে একটি নির্দিষ্ট এলাকা সম্পূর্ণভাবে লকডাউনের আওতায় আনা হয়। এতে সব ধরনের জনচলাচল, দোকানপাট ও যানবাহন বন্ধ থাকে। লোকজন ঘরের বাইরে বের হতে পারে না। সাধারণত কারফিউ জারি করা হয় গণদাঙ্গা, বড় সন্ত্রাসী হামলা, যুদ্ধাবস্থা বা জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির সময়। এর প্রয়োগে মিলিটারি বা পুলিশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। আদেশ লঙ্ঘন করলে গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড এমনকি প্রয়োজনে গুলির ঘটনাও ঘটতে পারে।
জরুরি অবস্থার উদাহরণ
বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা ও অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে একাধিকবার ১৪৪ ধারা, কারফিউ এবং জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। এসব পদক্ষেপ সাধারণত তখনই নেওয়া হয়, যখন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও নাশকতা পরিস্থিতিকে চরমে পৌঁছে দেয়। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো ২০০৭ সালের জরুরি অবস্থা, যা তৎকালীন সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জারি করা হয়েছিল।
সংকটের সূচনা ঘটে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী এবং কে এম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে। আওয়ামী লীগসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর অভিযোগ ছিল, এই সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারকদের বয়সসীমা বাড়িয়ে ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বিচারকদের জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করা হয়েছে। যদিও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এই দাবিগুলো আমলে নেননি।
২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হলে বিচারপতি কে এম হাসান দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন আহমেদ নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন, যা বিরোধী দল এবং কূটনৈতিক মহলে সমালোচিত হয়। রাজপথে আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে, অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সেনাবাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন ফখরউদ্দিন আহমেদ। এর পেছনে সেনাপ্রধান মঈন ইউ আহমেদের সরাসরি ভূমিকা ছিল। ক্ষমতা গ্রহণের পরই দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই সরকারের আমলে কারফিউ, সান্ধ্য আইন ও ১৪৪ ধারা একাধিকবার জারি করা হয় ‘স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার’ নামে।










 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন











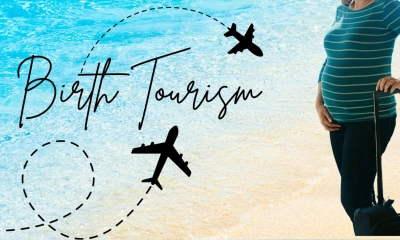




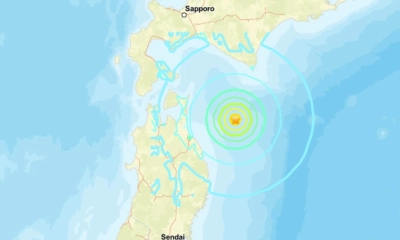






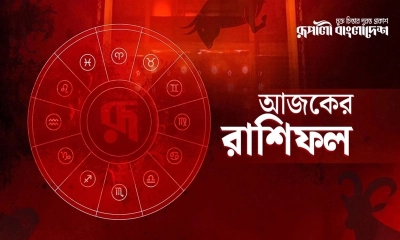
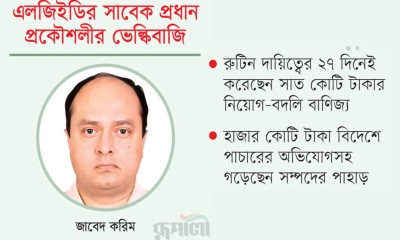
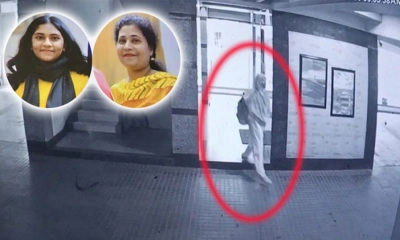


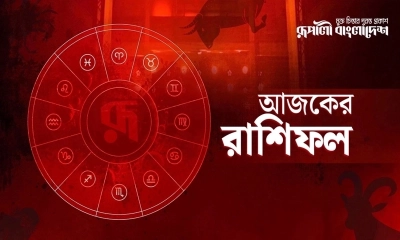





-20251208133054.webp)


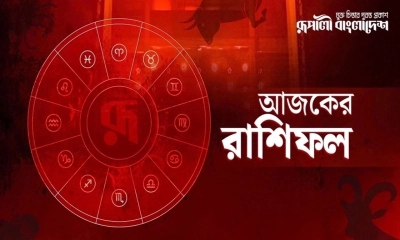
আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন