বাংলাদেশের গণতন্ত্র অর্ধেক নয়, পূর্ণ হতে হবে। সংসদে নারীর কণ্ঠ অলঙ্কার নয়, হতে হবে শক্তির প্রতীক। স্বাধীনতার ইতিহাসে নারী শুধু সহযাত্রী নয়, বরং নেতৃত্বের সারিতে থেকেও আজও পিছিয়ে আছে রাজনৈতিক বাস্তবতায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ থেকে ২০২৪ সালের সংসদ পর্যন্ত- নারীর সংগ্রাম অব্যাহত, কিন্তু ক্ষমতার কেন্দ্র এখনো তাদের নাগালের বাইরে।
প্রশ্ন একটাই সংরক্ষিত আসনে বসা নারীরা কি দেশের প্রকৃত রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে পারছেন? উত্তর ‘না’। প্রকৃত নেতৃত্ব গড়ে উঠবে তখনই, যখন নারী-পুরুষ উভয়ই সমানভাবে সরাসরি ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। কোটার অলঙ্কার নয়, প্রয়োজন ভোটের বৈধতা, জনগণের আস্থা, ও দায়িত্বের অঙ্গীকার। কেন নারী নেতৃত্বকে সংরক্ষণের গ-ি পেরিয়ে জনগণের ভোটের ময়দানে নামতেই হবে? আজ তাই ১৫টি বিস্তৃত দিক থেকে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাক।
১. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশের ইতিহাসে নারী কখনোই নিস্তব্ধ দর্শক ছিলেন না। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে তারা শুধু যোদ্ধা নন, ছিলেন চিকিৎসক, গুপ্তসংযোগ রক্ষাকারী, আশ্রয়দাত্রী,ও সর্বোপরি মনোবল জোগানো প্রতীক। বিপ্লবের প্রতিটি ধাপে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন সকল আন্দোলনে নারীরা রাজপথে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও এই নারীরা সংসদে সংখ্যায় সীমিত। গণতন্ত্রের প্রতিটি ধাপে যেখানে নারীরা জীবন দিয়েছেন, সেখানে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান আজও প্রান্তিক। এই বৈপরীত্য প্রমাণ করে যে, ইতিহাস নারীর ত্যাগকে সম্মান দিয়েছে, কিন্তু রাজনীতি তাকে ক্ষমতায় আসীন করতে ব্যর্থ হয়েছে। রাজনীতির অন্দরমহলে এখনো পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবশালী। নারীকে ক্ষমতার প্রতীক নয়, বরং পারিবারিক ঐতিহ্যের ‘সহচরী’ হিসেবে দেখা হয়। অতএব, বাংলাদেশের ইতিহাসে নারীর ভূমিকা যত গৌরবময়, বর্তমান রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ ততই অসম্পূর্ণ। ইতিহাস তাদের দিয়েছে মর্যাদা; রাজনীতি দিয়েছে প্রতীক, নেতৃত্ব নয়।
২. সংরক্ষিত আসনের সীমাবদ্ধতা: ১৯৭২ সালে সংবিধানে নারী প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত আসনের ধারণা যুক্ত হয়। প্রথমে এর মেয়াদ ছিল ১০ বছর, পরে তা বারবার বাড়ানো হয়, আজ তা দাঁড়িয়েছে ৫০টি আসনে। কিন্তু সমস্যা একটাই, এই আসনগুলো জনগণের ভোটে নির্ধারিত নয়। রাজনৈতিক দলগুলোই নির্ধারণ করে কে সংসদে যাবে। ফলে এসব নারী এমপি জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন না, বরং দলীয় নেতার প্রতি অনুগত থাকেন।
এই প্রক্রিয়া নারী রাজনীতিকদের ক্ষমতাহীন করে তোলে। অনেক সময় তারা বলেন, ‘আমরা সংসদে বসি, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেই না।’ প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বহীন এই প্রথা নারীর কণ্ঠকে করুণায় পরিণত করেছে। সংরক্ষিত আসন তাই নারীর ক্ষমতায়ন নয়, বরং রাজনৈতিক দলের প্রতীকী অনুগ্রহের প্রকাশ। যখন নেতৃত্ব করুণায় নির্ধারিত হয়, তখন তার মধ্যে স্বতন্ত্রতা থাকে না। এ কারণেই নারীর অনেকেই সংসদে থেকেও প্রভাবশালী ভূমিকা রাখতে পারেন না। কোটার সংস্কার নয়, প্রয়োজন সরাসরি প্রতিযোগিতার সুযোগ, যেখানে নারী নিজের যোগ্যতা দিয়ে নেতৃত্ব প্রমাণ করবেন।
৩. সরাসরি ভোটের প্রয়োজনীয়তা: গণতন্ত্রের মূল শক্তি হলো ‘ভোট’। ভোট ছাড়া কোনো প্রতিনিধিত্বের মূল্য নেই। সংরক্ষিত আসনে বসা নারী এমপিরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত নন; তাই তাদের রাজনৈতিক ভিত্তি দুর্বল। সত্যিকারের নেতৃত্ব তখনই গড়ে ওঠে, যখন জনগণ নিজ হাতে কাউকে বেছে নেয়। যে নারী সরাসরি ভোটে জয়ী হন, তার আত্মবিশ্বাস, জনসংযোগ ও নেতৃত্বের পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়। তিনি জানেন, তার অবস্থান করুণায় নয়, নির্বাচনের বৈধতায় প্রতিষ্ঠিত। এই গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি তাকে নীতিনির্ধারণের টেবিলে স্বাধীন কণ্ঠ দেয়। অন্যদিকে, সংরক্ষিত আসনের নারীরা অনেক সময় দলীয় নির্দেশেই ভোট দেন, নিজস্ব মতপ্রকাশের সুযোগ কম পান। তাই নারী নেতৃত্বকে প্রকৃত শক্তিতে রূপ দিতে হলে তাদেরও পুরুষদের মতো সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হবে। নারী প্রার্থীদের ভোটের ময়দানে নামার মানেই হবে নারীর আত্মমর্যাদার জয়যাত্রা।
৪. রাজনৈতিক দলগুলোর দায়: রাজনৈতিক দলগুলো নারী নেতৃত্বের প্রশংসা করলেও বাস্তবে তারা নারীদের সুযোগ দিতে কুণ্ঠিত। মনোনয়ন বণ্টনে নারীদের প্রাপ্য অংশ প্রায় শূন্য। অনেক সময় দলগুলো নারীদের মনোনয়ন দেয় কেবল পরিবারিক পরিচয় বা প্রভাবশালী নেতার স্ত্রীর ‘কৃতিত্বে’। এই সংস্কৃতি নারীদের যোগ্যতাকে অবমূল্যায়ন করে। একজন নারী যিনি নিজের রাজনৈতিক জীবনে মাঠে কাজ করেছেন, ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তুলেছেন, তার জায়গা অনেক সময় দখল করে নেন এমন কেউ যিনি কেবল কোনো নেতার আত্মীয়। ফলে নারীরা নিজের প্রতিভায় নয়, পুরুষতন্ত্রের ছায়ায় রাজনীতি করেন।
দলগুলো যদি সত্যিই নারী নেতৃত্ব চায়, তবে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও স্বচ্ছ মনোনয়ন প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। দলের প্রতিটি পর্যায়ে নারীর নেতৃত্ব নিশ্চিত না করলে নারী নেতৃত্ব কাগজে থাকবে, বাস্তবে নয়।
৫. নেতৃত্ব বনাম অলঙ্কার: আজকের প্রশ্ন, সংসদে নারীরা আছেন, কিন্তু তারা কি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, নাকি কেবল অলঙ্কার? সংসদে ৫০ জন নারী সদস্য থাকলেও তাদের মধ্যে কয়জন গুরুত্বপূর্ণ কমিটি বা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন? খুব কম। কারণ তাদের আসন দলীয় কোটায় নির্ধারিত, ভোটের মাঠে নয়।
ফলে নারী এমপিরা সংসদে থেকেও জনআস্থার নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারেন না। জনগণ তাদের ভোট দেয়নি, তাই তাদের মনে রাখেও না। তাদের বক্তব্য সংসদের প্রটোকলে থাকে, কিন্তু সমাজে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায় না।
নেতৃত্ব মানে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা, নীতি নির্ধারণে প্রভাব, ও জনগণের সঙ্গে জবাবদিহিতা। সংরক্ষিত আসনের নারীরা এই তিনটি ক্ষেত্রেই পিছিয়ে। তাই নারী নেতৃত্বকে অলঙ্কার নয়, নীতিনির্ধারণের চালিকাশক্তিতে পরিণত করতে হলে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে বৈধতা দিতে হবে।
৬. নারীর নিরাপত্তা ও অংশগ্রহণ: ভোটের মাঠে নারীরা এখনো ভয় ও অনিরাপত্তার মুখোমুখি। নির্বাচনি সহিংসতা, কেন্দ্র দখল, হুমকি, এসব পুরুষ প্রার্থীদের মতো সামলানো তাদের পক্ষে সবসময় সম্ভব নয়। অনেক সময় রাজনৈতিক সহিংসতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, নারীরা প্রার্থী হওয়াতেই আগ্রহ হারান। এই বাস্তবতা বদলাতে হলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে বিশেষভাবে দায়িত্ব নিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকেও অঙ্গীকার করতে হবে যে, নারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ভয়ভীতি বা সহিংসতা বরদাশত করা হবে না। যখন সমাজ নারীর নিরাপত্তাকে নিশ্চয়তা দেবে, তখনই নারীরা মাঠে নামবেন আত্মবিশ্বাস নিয়ে। নিরাপত্তা হলো নারী নেতৃত্বের ভিত্তি, যা ছাড়া অংশগ্রহণ অসম্ভব।
৭. সমান সুযোগের দাবি: রাজনীতিতে নারীরা প্রতিনিয়ত বৈষম্যের শিকার। মনোনয়ন থেকে শুরু করে গণমাধ্যমের কাভারেজ পর্যন্ত, সবখানেই তাদের ব্যক্তিত্ব নয়, পোশাক বা চেহারা নিয়ে মন্তব্য হয়। পুরুষ প্রার্থীরা এসব সমালোচনা থেকে মুক্ত থাকেন। এই সংস্কৃতি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ক্ষুণœ করে। প্রকৃত যোগ্যতা আড়ালে পড়ে যায়, দৃশ্যমান হয় ‘লিঙ্গ’। তাই রাষ্ট্র, গণমাধ্যম ও দলীয় কাঠামো, সবখানেই নারী প্রার্থীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সমতার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।
নারীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক প্রচার বন্ধ না হলে, তারা রাজনীতির ময়দানে টিকতে পারবেন না। সমান সুযোগ মানেই সমান মর্যাদা, এটাই নেতৃত্বের প্রথম শর্ত।
৮. আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট: বিশ্বজুড়ে নারী নেতৃত্ব আজ এক নতুন বাস্তবতা। ভারত নারী সংরক্ষণ বিল পাস করে সংসদে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেছে, তাও সরাসরি ভোটের মাধ্যমে। নেপাল সংবিধানে নারীদের জন্য ৩৩ শতাংশ বাধ্যতামূলক করেছে, পাকিস্তানে নারীরা নির্বাচনে জিতে সংসদে প্রবেশ করছেন।
কিন্তু বাংলাদেশ, যেখানে প্রধান দুই দলই নারী নেতৃত্বে পরিচালিত, সেখানে সংসদে নারীরা এখনো কোটার সীমায় বন্দি, এ এক অদ্ভুত বৈপরীত্য।
বাংলাদেশ যদি সত্যিই নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণে বিশ্বমান বজায় রাখতে চায়, তবে কোটার সংস্কার নয়, প্রত্যক্ষ ভোটের ব্যবস্থাই হতে হবে। আন্তর্জাতিক উদাহরণ আমাদের শেখায়, ক্ষমতায় যেতে হলে নারীদেরও ভোটযুদ্ধের ময়দানে নামতেই হবে।
৯. ৩৩ শতাংশ বাধ্যবাধকতা: আন্তর্জাতিক মানদ- বলছে, প্রতিটি সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ হতে হবে। বাংলাদেশে এ নিয়ে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে রাজনৈতিক দলগুলো নারী প্রার্থীদের প্রায় উপেক্ষা করতে পারে। প্রয়োজন আইনি সংস্কার, যাতে রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য হয় অন্তত এক-তৃতীয়াংশ মনোনয়ন নারীদের দিতে। এটি কেবল ন্যায্যতা নয়, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতারও শর্ত।
যখন দলগুলো নারীদের মনোনয়ন দেবে বাধ্যতামূলকভাবে, তখন রাজনীতির মাঠে নতুন প্রজন্মের নারী নেতৃত্ব বিকশিত হবে।
১০. সংসদ আসন সংখ্যা দ্বিগুণের প্রস্তাব: নারী নেত্রীরা প্রস্তাব করেছেন, সংসদ আসন ৩০০ থেকে বাড়িয়ে ৬০০ করা হোক; ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কেবল নারীরা। প্রথমে এটি অদ্ভুত শোনাতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এটি গণতন্ত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হতে পারে। যদি ৩০০ নারী সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে সংসদে প্রবেশ করেন, তবে নারীর নেতৃত্ব কাগজে নয়, বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে সংসদে ভারসাম্য, নীতিনির্ধারণে বৈচিত্র্য ও প্রতিনিধিত্বের ন্যায্যতা নিশ্চিত হবে।
১১. উন্নয়ন ও নারীর অংশগ্রহণ: গবেষণা প্রমাণ করে, যেসব দেশে সংসদে নারীর উপস্থিতি বেশি, সেখানে মানব উন্নয়ন সূচক দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুকল্যাণ, সব খাতে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি নতুন মাত্রা আনে।
নারী নেত্রীরা সাধারণত জনগণের কল্যাণকেন্দ্রিক নীতি প্রণয়ন করেন, যা উন্নয়নকে টেকসই করে। বাংলাদেশের উন্নয়ন এখন বিশ্বে উদাহরণ হতে পারে, যদি এই উন্নয়নের অর্ধেক ভাগিদার নারীও সমানভাবে সিদ্ধান্তে অংশ নেন।
১২. শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর ভূমিকা: আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বলে, যেখানে শান্তি আলোচনায় নারী অংশ নেন, সেখানে যুদ্ধবিরতি ও সমঝোতা টেকসই হয়। নারীরা আপসহীন নয়, কিন্তু তারা আপসহীনতার পরিবর্তে স্থিতিশীলতার সন্ধান করে।
বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিভাজন ও সহিংসতার যে বাস্তবতা, সেখানে নারী নেতৃত্ব হতে পারে সমঝোতার নতুন সেতু। সংসদে ও দলীয় সিদ্ধান্তে যদি নারীরা সক্রিয়ভাবে থাকেন, তবে বিরোধিতাও মানবিক রূপ পাবে।
১৩. তরুণ প্রজন্মের আকাক্সক্ষা: আজকের তরুণ সমাজ নারী-পুরুষ সমতা চায়। তারা চায় নেতৃত্বে বৈচিত্র্য ও যোগ্যতার স্বীকৃতি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখা যায়, তরুণরা নারী প্রার্থীদের সফলতা উদযাপন করে।
যদি রাজনৈতিক দলগুলো নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না আনে, তরুণ ভোটাররা ক্রমে হতাশ হবে। ভবিষ্যতের রাজনীতি তরুণদের, আর তারা আর ‘পুরুষতন্ত্রের ছায়া রাজনীতি’ মেনে নেবে না।
১৪. নাগরিক সমাজের আহ্বান: নারীর রাজনৈতিক অধিকার ফোরাম, মানবাধিকার সংগঠন, ও এনজিওগুলো এক সুরে বলছে, সংরক্ষিত আসনের যুগ শেষ। এখন সময় সরাসরি নির্বাচনের। নাগরিক সমাজের এই দাবি আসলে একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইঙ্গিত, যেখানে নারীরা কোটার অনুগ্রহ নয়, জনগণের আস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবেন।
১৫. নারীর ক্ষমতায়ন মানে দেশের ক্ষমতায়ন: নারীকে ক্ষমতার বাইরে রেখে কোনো জাতি টেকসই উন্নয়নের পথে যেতে পারে না। সংরক্ষণ ব্যবস্থা একটি অস্থায়ী সোপান হতে পারে, কিন্তু স্থায়ী সমাধান নয়। প্রকৃত সমাধান হলো সরাসরি ভোটে নির্বাচিত নারী নেতৃত্ব। নারীর ক্ষমতায়ন মানে দেশের ক্ষমতায়ন, কারণ যখন নারী নেতৃত্বে থাকে, তখন সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। তবেই গণতন্ত্র পূর্ণতা পায়, তবেই দেশ শক্তিশালী হয়।
উপসংহার: বাংলাদেশের গণতন্ত্র এখনো অসম্পূর্ণ, কারণ সংসদে নারীর কণ্ঠ আছে, কিন্তু নেতৃত্ব নেই। সংরক্ষিত আসনের প্রথা নারীদের কণ্ঠস্বরকে প্রতীকী করেছে, কার্যকর নয়। এখন সময় এসেছে নারীদের প্রকৃত প্রতিযোগিতার ময়দানে আনার সরাসরি ভোট, নিরাপত্তা, সমান সুযোগ ও বাধ্যতামূলক মনোনয়ন, এই চার স্তম্ভেই গড়ে উঠবে নারী নেতৃত্বের নতুন দিগন্ত। গণতন্ত্রের অর্ধেক বাদ দিলে কোনো রাষ্ট্র টেকসই হয় না।
দেশ এগোয়, যদি নারী এগোয়।
সংসদ শক্তিশালী হয়, যদি নারীর কণ্ঠ শোনা যায়।
সংরক্ষিত আসন যথেষ্ট নয়, সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হতে হবে নারী প্রার্থীদের। এটাই হোক টেকসই গণতন্ত্রের শর্ত।
মীর আব্দুল আলীম, সাংবাদিক, সমাজ গবেষক
মহাসচিব, কলামিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ


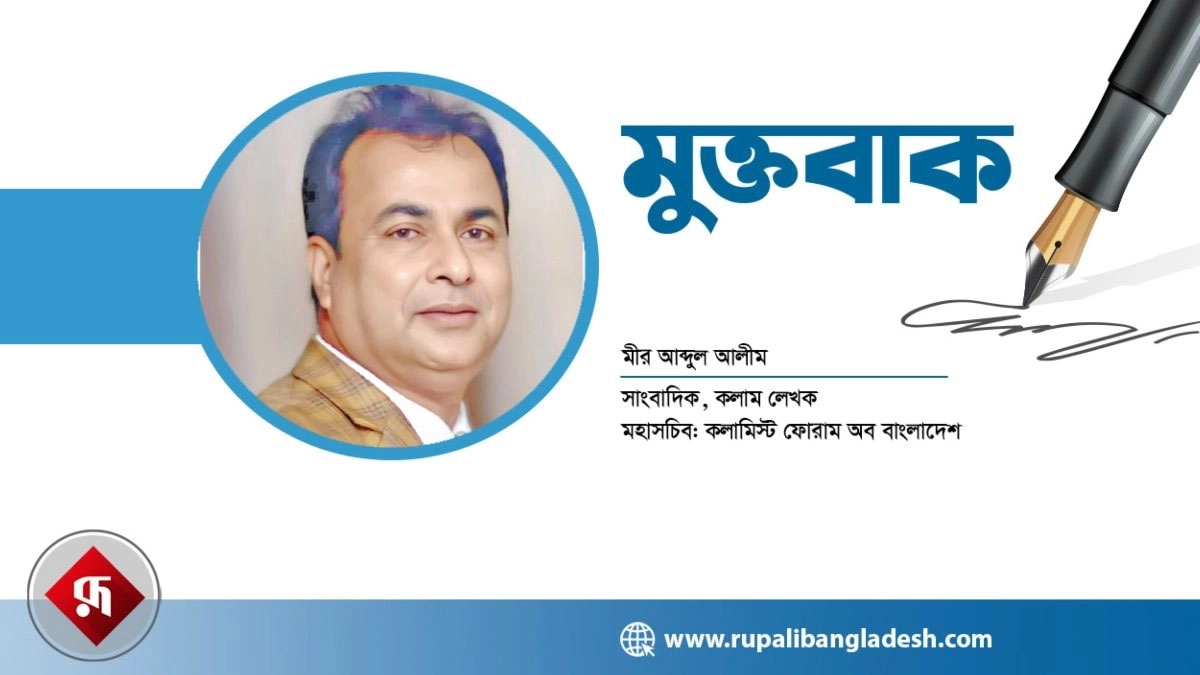
 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন



-20251011015415.webp)
-20251011015146.webp)
-20251011014940.webp)





-20251011014811.webp)





-20251007164446.webp)






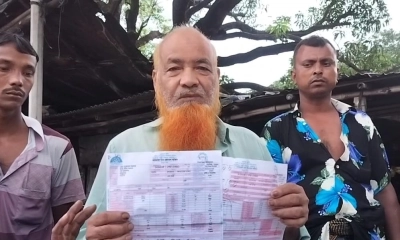

-20251006183518.webp)
আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন