সম্প্রতি আমাদের দেশ একটি জাতীয় নির্বাচনের পথে এগিয়ে চলেছে এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বেশ জোরালোভাবে ঘোষণা করেছেন যে আগামী বছরের শুরুতে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আমরা আশাবাদী হতে পারি। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়ায় বড় পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছে, যার মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হচ্ছে ‘না ভোট’ বিধানের পুনঃপ্রবর্তন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচন রোধ করার অভিপ্রায় হিসেবে নির্বাচন কমিশন এই বিধান সংযোজন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। তবে শুধুমাত্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোধে এই ‘না ভোটের’ বিধান চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেটা কতটুকু ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তবে সব আসনে ‘না ভোট’ থাকা অবশ্যই সাধারণ ভোটারদের সামনে নতুন একটা সুযোগ এনে দেবে। যার ফলে আমাদের দেশের মৌলিক গণতন্ত্র আরও মজবুত হবে।
সর্বশেষ খসড়া অনুসারে, যদি শুধু একজন প্রার্থী সকল প্রকার যাচাই-বাছাই বা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকেন, তবে সেই প্রার্থীকে তাদের নির্বাচনী এলাকায় ‘না ভোট’ বিকল্পের বিরুদ্ধে ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতা’ করতে হবে। কোনো প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট যদি ব্যালটে ‘না ভোট’ থেকে কম হয় তাহলে আবার নতুন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে। তবে প্রার্থী যদি বেশি ভোট পান তবে তাকে নির্বাচিত অবিশ্যম্ভাবীভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।
এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ২০০৮ সালে জাতীয় নির্বাচনের আগে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে প্রথম ‘না ভোট’ বিধান প্রবর্তিত হয়েছিল। সেই নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের হিসেবে অংশগ্রহণকারী সব দলের মধ্যে প্রাপ্ত ভোটের হিসেবে ষষ্ঠ অবস্থানে ছিল ‘না ভোট’। যদিও বিধানটি ২০০৯ সালের শুরুর দিকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরপরই এই ভোট বাতিল করা হয়েছিল। ভারত ২০১৩ সালে হাইকোর্টের রায় অনুসরণ করে ‘না ভোটের’ বিধান চালু করার পক্ষে রায় প্রদান করে এবং সে দেশের বিভিন্ন প্রদেশে এখনো এই ভোটের বিধান চালু রয়েছে।
স্বাভাবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে ধরে নেওয়া যায় সাধারণত কোনো আসনে না ভোট বিজয়ী হবে না। তবে প্রাপ্ত ‘না ভোট’-এর সংখ্যার হার অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য অংশগ্রহণদের আস্থা অথবা অনাস্থার নির্ণায়ক হিসাবে গৃহীত হবে।
প্রকৃতপক্ষে, এটি খুব ক্ষুদ্র বিষয় হলেও বৃহত্তর কিছুর সঙ্গে কথা বলে গণতন্ত্রে সাধারণ জনগণের প্রত্যাখ্যানের শক্তি। অল্প কিছু শব্দ যতটা সংক্ষিপ্ত তবুও না যতটা শক্তিশালী। এটা প্রতিবাদের, প্রতিরোধের, স্বাধীনতার শব্দ। পরিবর্তনের দরজা খোলার জন্য ‘না’ শব্দটির গুরুত্ব বর্ণনাতীত।
বাংলাদেশের নিজস্ব ইতিহাস প্রত্যাখ্যানের শক্তি দেখিয়ে। প্রকৃতপক্ষে, এ জাতি একটি সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে জন্ম লাভ করেছিল। নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য, অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিবাদ স্বরূপ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশিরা তাদের প্রতিবাদ প্রকাশ করেছিল। আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে, অগ্রগতি কখনো নিষ্ক্রিয় গ্রহণযোগ্যতা থেকে নয় বরং যা অন্যায় ছিল তার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রত্যাখ্যান থেকে এসেছে। ভোট বুথের ভেতরে সাধারণ মানুষের সেই অধিকার অস্বীকার করা অবশ্যই সেই গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা।
দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের দেশে নির্বাচন প্রায়শই নাগরিকদের পছন্দের সার্বজনীন বহির্প্রকাশ ছাড়াই চলমান রয়েছে। ভোটারদের রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে বেছে নিতে বলা হয় যারা প্রায়শই জনসম্পৃক্ত নয় এবং তারা নির্বাচিত হওয়ার পড়ে জনস্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করায় মনোযোগী হয়। আমাদের দেশে ভোটারদের অনুপস্থিতিকে সাধারণ মানুষের উদাসীনতা হিসেবেও দেখা হয় এবং এখানে ব্যালট নষ্ট হওয়াকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়। কিন্তু এখানে আসল সমস্যা সাধারণ ভোটারদের নয়; সমস্যা মূলত আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর; যারা তাদের ক্ষুদ্রস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মানুষের গণদাবিকে সম্মান জানাতে নারাজ।
‘না ভোট’ মূলত ভিন্নমত পোষণকারীদের জন্য একটি বিকল্প। এর ফলে সাধারণ ভোটারদের হতাশাকে পরিমাপযোগ্য রায়ে পরিণত করতে ব্যাপক একটা ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। একজন নাগরিক যিনি ‘না ভোট’-কে চিহ্নিত করেছেন তিনি বিশেষত গণতন্ত্রকে ত্যাগ করছেন না; বরং গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পথকে সুগম করছেন। ‘না ভোট’ দেওয়ার মাধ্যমে সেইসব সাধারণ ভোটার জানান দেওয়ার সুযোগ পায় যে, আমরা বিদ্যমান গণতান্ত্রিক মেকানিজমে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর চাপিয়ে দেওয়া ব্যক্তিকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করি না।
সমালোচকরা যুক্তি দেন যে না ভোট প্রতীকী হতে পারে। সর্বোপরি, শীর্ষস্থানীয় প্রার্থী সবসময়ই বিজয়ী। কিন্তু রাজনীতি কখনোই একসূত্রে কোনো গাণিতিক নিয়ম দিয়ে চালিত সূত্র নয়। বেশি ভোট যিনি পাবেন তিনিই বিজয়ী কিন্তু এখানে একটা কিন্তু থেকেই যাবে! এমন একটি নির্বাচনের কথা কল্পনা করুন যেখানে না ভোটের সংখ্যা এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১০০ ভোটের মধ্যে ২৫টি। তাহলে কোনো বিজয়ী ব্যক্তি কি জাতির সামনে দাঁড়িয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে কথা বলার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাবি করতে পারে? এই ধরনের ফলাফল নির্বাচনের মধ্যেই একটি গণভোট হবে যা পরিগণিত হবে রাজনৈতিক সংস্কৃতির আয়না যা প্রায়শই জড়তা এবং এনটাইটেলমেন্টের ওপর নির্ভর করে।
রাজনৈতিক দলগুলোর দলীয় প্রতীকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর মাধ্যমে দলকে একটা নিজস্বতা দিয়ে থাকে। যেমন একটি পতাকা শুধু কাপড়মাত্র, তবুও তা একটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে যথেষ্ট। একটি স্লোগান শুধুমাত্র শব্দ, তবুও তা অপশাসনকে উচ্ছেদ করতে পারে।
একইভাবে, কোনো ভোট রাজনৈতিক দলগুলোর আত্মতুষ্টিকে নিরস্ত করতে পারে না। ব্যালটে একটি ‘না ভোটের’ মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য প্রত্যাখ্যান দলগুলোকে কীভাবে তারা প্রার্থী বাছাই করে, কীভাবে তারা ইশতেহার লেখে এবং কীভাবে তারা নাগরিকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে তা পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করতে পারে। এটি তাদের মনে করিয়ে দিতে পারে যে, শুধু ভোটে বিজয়ী হওয়া নয়, সব জনগণের মন জয় করা আবশ্যক।
তাই অকপটে বলা যায়, ‘না ভোট’ও মর্যাদার বিষয়। ভোট দেওয়া নিছক পছন্দের কাজ নয়, অবশ্যই আত্মপরিচয়ের নিষ্কণ্টক একটা ঘোষণাও। প্রত্যাখ্যানের বিকল্প ছাড়া, সেই পরিচয়টি অসম্পূর্ণ। ‘না ভোট’ ছাড়া একটি ব্যালট শাসক এবং শাসিতদের মধ্যে আলাপন নয় বরঞ্চ উপর থেকে আরোপিত একটি অপলাপ এবং তা নিশ্চিত করা যে নাগরিকরা সার্বভৌম, শোভাময় নয়।
এই স্বীকৃতি বাংলাদেশে বিশেষভাবে জরুরি যেখানে ভোটারদের মর্যাদা বরাবরই আপস করা হয়েছে। ভোটকেন্দ্রে সহিংসতা, প্রতিযোগিতাহীনতা এবং নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করেছে। ‘না ভোট’ আবার চালু করা হলে এই কাঠামোগত ত্রুটিগুলোকে পুরোপুরি সমাধান করবে না, তবে এটি পুনরায় দাবি জানাবে যে ভিন্নমতকে সম্মতির সঙ্গেই গণ্য করা হবে।
সম্প্রতি বেশ কিছু জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে এখনো উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভোটার ভোট দেওয়া নিয়ে দ্বিধান্বিত দেখা গেছে। যেখানে উপস্থাপিত সাধারণ জনগণের মর্জি আমাদের গণতান্ত্রিক উত্তরণ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, এমনকি সংশয়বাদও দৃশ্যমান হয়েছে। একটি সমীক্ষায় প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা বলেছেন যে তারা আসন্ন নির্বাচনে কাকে সমর্থন করবেন তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেই। এই নাগরিকরা উদাসীন নয়; তারা অপেক্ষা করছে, পরিমাপ করছে, এবং অনুসন্ধান করছে। প্রত্যাখ্যানের এই অধিকারকে উপেক্ষা করা অবশ্যই সামাজিক বিভাজনকে আমন্ত্রণ জানায়। ভিন্নমত নিয়ে অবশ্যই বিতর্ক হতে পারে, এমনকি সাধারণ জনগণকে রাজি করানো যেতে পারে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ খুব বেশি যুক্তি নয়, খুব কম বিশ্বাস। কোনো ভোটই মোহগ্রস্তদের গণতান্ত্রিক ভাঁজে ফিরিয়ে আনার উপায় দেয় না, যাতে তারা প্রক্রিয়াটি পরিত্যাগ না করে অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারে।
নির্বাচন কমিশনের বৃহত্তর সংস্কার পরিকল্পনার গুরুত্ব অবশ্যই নগণ্য নয়। ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) বিধান বাতিল করা, সশস্ত্র বাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞা সম্প্রসারণ করা এবং কমিশনের কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ সবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু কেউই ‘না ভোট’কে পুনরুজ্জীবিত করার নৈতিক ও প্রতীকী ওজন বহন করে না। প্রার্থীদের না বলার অর্থ নির্বাচনী প্রক্রিয়া ব্যাহত করা নয়, বরং আরও ভালো প্রার্থী দাবি করা। এটা জোর দিয়ে বলা যে আরও উন্নত মানের রাজনীতি সম্ভব এবং তা আমাদের সবার কাম্য।
শেখ শামীম ইকবাল
কলাম লেখক


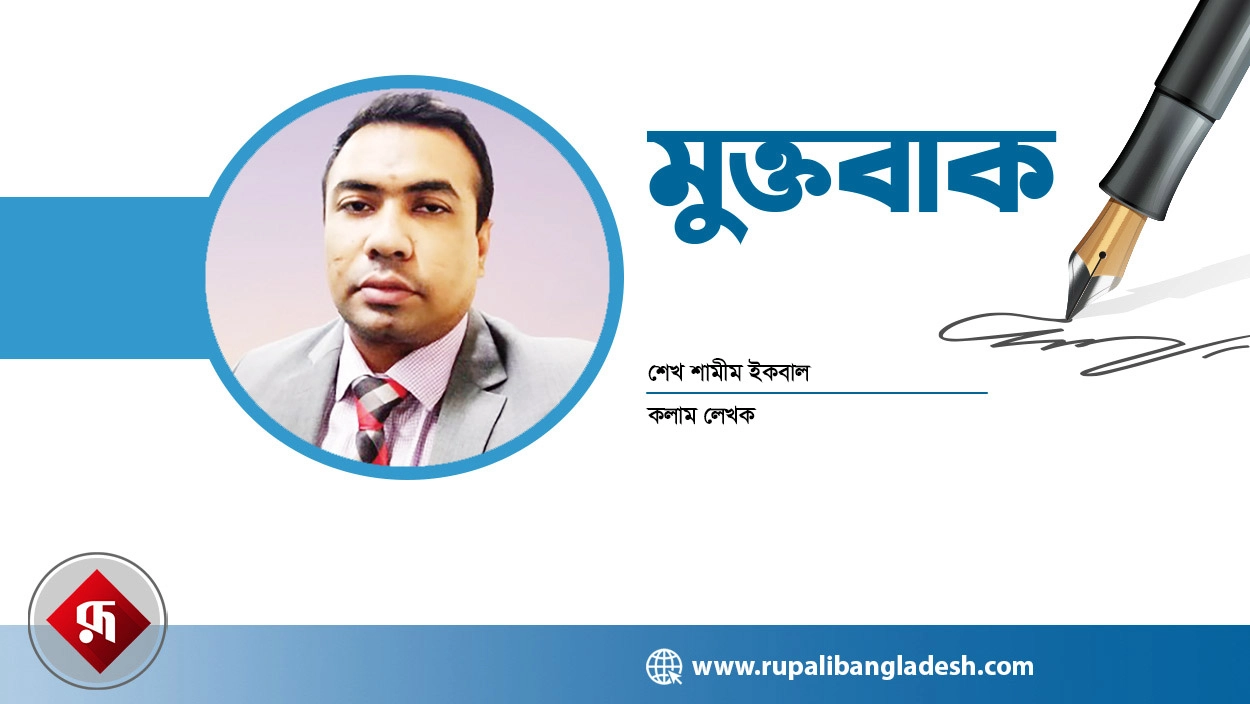
 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন



-20251031020255.webp)


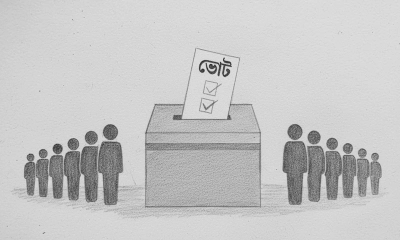




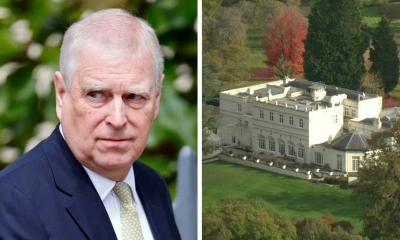
















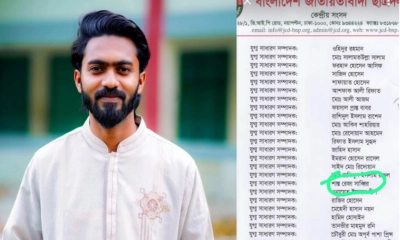
-20251025002118.webp)
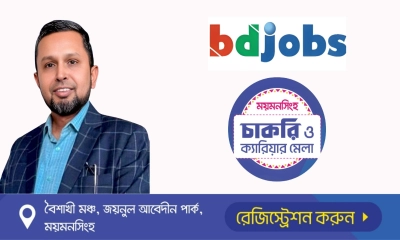




আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন