সারা বিশ্বে ২০২৪ সালেও যা চলছে, সেটা বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে কম কিছু নয়। মানচিত্রের যেকোনো একটি ভূখণ্ডে আপনি পেনসিল ধরুন, দেখবেন সেখানেই সংঘাত-সহিংসতা অথবা রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান। যে দেশগুলোর সঙ্গে ভিন্ন দেশের যুদ্ধ নেই, সেই দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ সংঘাত চরমে এবং সেখানেও বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর প্রক্সি ওয়ার চলছে। আর এই যুদ্ধ-সংঘাত-সহিংসতার সম্মুখে যতই আদর্শিক সংঘাত বা অন্যায় অবিচারের কথা বলা হোক না কেন, অর্থনৈতিকভাবে এসব যুদ্ধ অশান্তির ফায়দা চলে যাচ্ছে কয়েকটি বড় দেশের পেটে, যারা যুদ্ধ যুদ্ধ ‘খেলছে’। এর প্রধান কারণ তাদের অস্ত্র ব্যবসা ও স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারেস্ট।
জানেন নিশ্চয়ই, কোভিড এবং ইউক্রেন যুদ্ধের পরও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে দিন দিন, মুদ্রার, অর্থাৎ ইউএস ডলারের মান বাড়ছে। এত বড় যুদ্ধে জড়িয়েও এবং আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও রাশিয়ার মুদ্রা রুবলের দাম বেড়েছে-বাড়ছে। চীনের সঙ্গে পশ্চিমা দেশগুলোর চরম উত্তপ্ত অবস্থাতেও চীনের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে পাল্টে গেছে। লক্ষ করলেই দেখা যাবে, ইউরোপীয় পণ্য বিক্রয় বিশ্বব্যাপী মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। সেল ফোন থেকে শুরু করে কৃষি সরঞ্জাম বা ইন্ডাস্ট্রি মেশিনারিজ সবকিছুর বিক্রি অনেক নিচে নেমে গেছে। অথচ ইউরোপের অর্থনীতি অনেকটাই স্থির রয়েছে। এর কারণ ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, চেক রিপাবলিক সবাই আধুনিক অস্ত্র তৈরি করে। ফ্রান্সের রাফায়েল, মিরেজ যুদ্ধ বিমান, জার্মানির লিওপার্ড ট্যাঙ্ক, চেল রিপাবলিকের সাব মেশিনগান, গ্রেনেড থেকে শুরু করে অটোমেটিক পিস্তল বিক্রয় হয় বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারে। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদন ও বিক্রয়ের ফিরিস্তি আর নাইবা দিলাম।
এসব অস্ত্রের প্রধান ক্রেতা ভারত, পাকিস্তান, সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, জাপানের মতো দেশগুলো। এ ছাড়া রয়েছে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার ছোট-বড় অনেক দেশ। এখন লক্ষ করুন, মধ্যপ্রাচ্যে যদি শান্তি বজায় থাকে তাহলে ভারী ভারী অস্ত্র বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দিয়ে তারা কেন কিনবে? ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যদি একটি স্থায়ী শান্তিচুক্তি হয় এবং দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি হয় তাহলে মানুষের নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা না করে, জনগণের স্যানিটেশনের ব্যবস্থা না করে তারা কেন প্রতিরক্ষা খাতে মূল্যবান বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে? তাই সুপরিকল্পিত কৌশল হলো এসব অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা বজায় রাখা। তা না হলে হঠাৎ করে বিনা উসকানিতে, কোনো অঘটন না ঘটা সত্ত্বেও আচমকা হামাস কেন ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালাবে? এই হামলার বিষয়ে বলতে গেলে আস্ত একটি পুস্তক হয়ে যাবে। যে ইসরায়েলের অভ্যন্তরে দেশটির প্রতিরক্ষা বাহিনীর চোখ এড়িয়ে একটি বিড়াল প্রবেশ করতে পারে না, সেখানে বুলডোজার দিয়ে শক্ত বেড়া ভেঙে শত শত হামাস ও গাজার যোদ্ধারা ঢুকে পড়ল এবং ৬ ঘণ্টাব্যাপী তাণ্ডব চালিয়ে ১ হাজার ২৪০ জনকে হত্যা করল এবং দুই শতাধিক মানুষকে বন্দী করে গাজায় নিয়ে এলো! ইসরায়েলের আয়তন ৮ হাজার বর্গমাইল, অর্থাৎ বাংলাদেশের ৭ ভাগের একভাগ, তাও আবার সমুদ্র এলাকাসহ। দেশটিতে বিমানঘাঁটিসহ ৭০টি মিলিটারি ক্যাম্প রয়েছে আধুনিক অস্ত্র, আধুনিক সামরিক যানবাহনসহ। ইসরায়েলের যেকোনো সেনাক্যাম্প থেকে যেকোনো নিকটবর্তী ঘটনাস্থলে পৌঁছতে ১৫ মিনিট সময় লাগে না। অথচ প্রায় ৮ ঘণ্টা হামাস তাণ্ডব চালালো! এ ঘটনা নিয়ে একটি ধারণা আছে, এ হামলা হতে দেওয়া হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে, যাতে হামাস নিয়ে সমস্যা ইসরায়েলের পক্ষ থেকে চিরদিনের জন্য মুছে ফেলা যায়। আর যেহেতু গাজায় হামলা করলে জড়িয়ে পড়বে অনেক পক্ষ, সেহেতু মধ্যপ্রাচ্য অশান্ত হয়ে উঠবে এবং প্রতিটি পেট্রোডলারের দেশের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বাড়াতে হবে।
ইউক্রেন তো ভালোই ছিল, কী প্রয়োজন পড়েছিল ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ার? ন্যাটোতে যোগ দিলেই তো একমাত্র যুদ্ধ ছাড়া ক্রিমিয়া ফেরত পাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না ইউক্রেনের। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলো জানত, ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দিতে চাইলেই রাশিয়া দেশটিতে হামলা চালাবে। ন্যাটোতে যোগদান নিয়ে ৯০ দশক থেকেই একটি বোঝাপড়া হয়েছিল রাশিয়ার সঙ্গে। ন্যাটোর সঙ্গে ইউক্রেনের একটি ভালো সম্পর্ক ছিল। কিন্তু ন্যাটো দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে ন্যাটো অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে বিশেষ করে যখন বুঝতে পারে, ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ার একচ্ছত্র নেতা বনে গেছেন। যুক্তরাষ্ট্র বহু আগে থেকেই পুতিনকে কমিউনিস্ট মনে করে এবং ভবিষ্যৎ দেখতে পায়, পুতিন শক্তিশালী হলে বিশে^র বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিকরা শক্তিশালী হয়ে উঠবে। বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ইউক্রেনকে ন্যাটো জোটে নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ২০১০ সালে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট হয়েই ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ এই ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, রাশিয়ার মতো একটি শক্তিশালী বড় দেশকে ঘাড়ের ওপর রেখে ন্যাটোতে যোগ দিলে পদে পদে রাশিয়ার অসহযোগিতা ভোগ করতে হবে। এ ছাড়া তিনি নিজেও রাশিয়াপন্থী ছিলেন। কিন্তু ইয়ানুকোভিচের বিরুদ্ধে প্লট তৈরি হয়ে যায় তাকে উৎখাতের।
মেইডেন বিপ্লব নামে একটি আপরাইজিং দেখা দেয় যাতে ৭৭ জন মানুষ নিহত হয়। এরপর তাকে ইমপিচমেন্টের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অপসারণ করা হয়। ২০১৪ সালে এই ৭৭ জনের রক্তের বিনিময়ে ইউক্রেনকে ইউনুকোভিচ মুক্ত করা হয়। তিনি পদত্যাগ করে রাশিয়ায় পালিয়ে যান। এর পর পরই রাশিয়া ক্রিমিয়া অঞ্চল দখল করে নেয়। পুতিন দাবি করেন, এটি রাশিয়ারই অংশ, এখানকার মানুষ রাশিয়ার সঙ্গে একত্রিত হতে চায়। তিনি বিশ্বাস করেন, অথবা দাবি করেন যে ইউনুকোভিচকে কিছু চরম যুক্তরাষ্ট্রপন্থী আপরাইজিং ঘটিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করেছে।
ওদিকে ইউক্রেনে ক্ষমতায় আসেন পেট্রো পেরেশেঙ্কো। তিনি ইউনুকোভিচের অধীনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ইউক্রেনকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নমুখী করতে চেয়েছিলেন। পেরেশেঙ্কো দোনবাস অঞ্চলে রাশিয়াপন্থীদের দমন করেছিলেন। কিন্তু ন্যাটোতে যোগ দেওয়াতে তার অনীহা ছিল। বলেছিলেন, ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার জন্য জনগণের মধ্যে সমর্থন সীমিত। তখনই তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। ২০১৯ সালের নির্বাচনে পুরোপুরি যুক্তরাষ্ট্রের ভক্ত টিভি অভিনেতা ভলোদোমির জেলেনেস্কির কাছে পরাজিত হন। জেলেনেস্কি ক্ষমতায় এসে ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে পার্লমেন্টে বিল পাস করিয়ে নেন। ব্যাস, প্লট তৈরি হয়ে যায় পুতিনের ইউক্রেইন আক্রমণের।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে বসে। যে যুদ্ধ তীব্রভাবে চলমান। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ও কৌশলগত সহায়তা দিচ্ছে ন্যাটো জোট ইউক্রেনকে এ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। রাশিয়ার ঘাম ঝরে যাচ্ছে।
বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, এই যুদ্ধে ইতোমধ্যে দুপক্ষের পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের জীবননাশ হয়েছে।
শুধু ইসরায়েল বা ইউক্রেন নয়, বহু দেশে এখন গৃহযুদ্ধ এবং রাজনৈতিক যুদ্ধ চলছে ন্যাটো রাশিয়া বা যুক্তরাষ্ট্র চীনের মধ্যে, যাকে আমরা প্রক্সি যুদ্ধ বলতে পারি। তাইওয়ান নিয়ে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে সামরিক মহড়া চলছে তা যেকোনো সময় যুদ্ধে রূপ নিতে পারে। ভারত ও চীনের মধ্যে যে বৈরী সম্পর্ক তা যুদ্ধে রূপ নিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বির সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই দুটি দেশ কোনোভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে লাখ লাখ মানুষকে জীবন দিতে হবে। আফ্রিকার অনেক দেশে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং চীন হাত বাড়িয়ে আছে। কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠী রাশিয়ার পক্ষে তো কোনোটা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অস্ত্র হাতে যুদ্ধরত। প্রাণ দিচ্ছে সাধারণ দরিদ্র আফ্রিকান। চীন অনেক সরকারকে আয়ত্তে নিয়ে নিয়েছে তার বাণিজ্য প্রসারে।
আরও শঙ্কার কথা, এই পরিস্থিতির কোনো সমাধানের পথ কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। জাতিসংঘের মতো প্রতিষ্ঠান অনেকটা অকার্যকর হয়ে আছে। কোনোপক্ষই জাতিসংঘের কোনো কথা গায়ে মাখছে না। ফলে আগামী দু-চার বছরে কোনো শান্তির সম্ভাবনা আছে বলে কেউ মনে করেন না। বিভিন্ন দেশের সংঘাতের চরিত্র কোন দিকে মোড় নেয় তা অনেকটাই নির্ভর করছে ২০২৪ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ওপর। তবে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে যুদ্ধের চরিত্র পাল্টাতে পারে, কিন্তু শান্তি আনতে পারবেন সে কথা কেউ মনে করেন না। যদিও ওই নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের ফিরে আসার সম্ভাবনাই বেশি। আর ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটরা আবার সরকারে এলে যুদ্ধের তীব্রতা কমবে তারও কোনো ইঙ্গিত নেই। সুতরাং আমরা জানি না, আগামীর পৃথিবী আমাদের জন্য কতটা বসবাসের জন্য স্বস্তির হবে।
সাহিত্যিক ও সাংবাদিক



















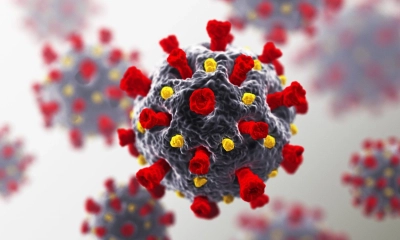
-20250803040400.webp)

-20250803025403.webp)









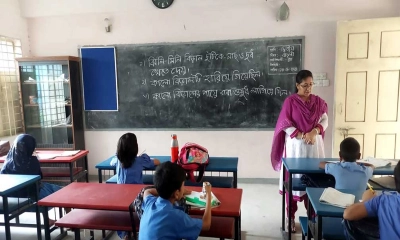




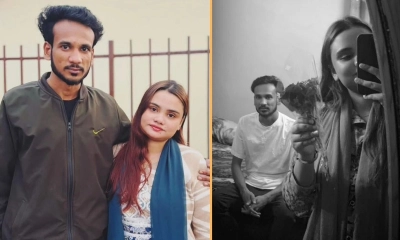
আপনার মতামত লিখুন :