বর্তমানে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরীয় সামুদ্রিক অঞ্চলে অতিমাত্রায় প্লাস্টিক-পলিথিনের দূষণ হচ্ছে। তা ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। মারাত্মক এই দূষণ মূল্যবান মৎস্যসম্পদসহ প্রায় ৭০০ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণীর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এমনকি বেশ কিছু প্রাণী এই প্লাস্টিক দূষণের ফলে এখন প্রায় বিপন্ন। ব্যবহৃত প্লাস্টিকের মধ্যে ৪০ শতাংশ মাত্র একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া হয়। এসব প্লাস্টিক মাটির ক্ষতি করে নদী হয়ে সর্বশেষ ঠিকানা হয় সাগর বা মহাসাগর।
পরিবেশবিজ্ঞানীরা বলছেন, পলিথিন পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। প্লাস্টিকের সর্বশেষ অণু ভেঙে শেষ করা যায় না। যদি প্লাস্টিক মাটি চাপা দেওয়া হয়, তাতে চারপাশের মাটিকে বিষাক্ত করে তোলে। আবার প্লাস্টিক একটি মারাত্মক পানিদূষক। এসব প্লাস্টিক প্রাণীর মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে ক্যান্সারসহ প্রাণঘাতী রোগ হচ্ছে। যার শেষ পরিণতি মৃত্যু।
পরিবেশবিজ্ঞানী ও ফেনী ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. এম জামালউদ্দীন আহমদ রূপালী বাংলাদেশকে বলেন, ২০ মাইক্রোনের নিচের প্লাস্টিক বা পলিথিন সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। এগুলো কৃষিজমির ঊর্বরতা নষ্ট করে জলাশয়, নদী হয়ে সাগর বা মহাসাগরে পৌঁছে যায়। কারণ, প্লাস্টিক ৫০০ থেকে ১০০০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। ফলে ভূমি থেকে সাগর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে জলবায়ু পরিবর্তনে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, পলিথিন বা প্লাস্টিক একেবারে বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে ২০ মাইক্রোনের ওপরের প্লাস্টিক ব্যবহার করা যাবে। কারণ এগুলো পুনরায় ব্যবহারযোগ্য।
গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকাসহ প্রত্যেকটি জেলা শহরে একটি পরিবার প্রতিদিন গড়ে পাঁচটি পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করে। সে হিসেবে শুধু ঢাকা শহরে প্রতিদিন আড়াই কোটির বেশি প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যাগ একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া হয়। এ ছাড়া দেশে প্রতিদিন ৩৫ লাখের বেশি টিস্যু ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাত হচ্ছে। এসব ব্যাগ পলিথিনের হলেও কাপড়ের ব্যাগ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পচনশীল পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যাগ, পরিবেশবান্ধব পাটজাতদ্রব্য, কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙা, কাপড়ের ব্যাগ ইত্যাদি বিকল্প থাকা সত্তে¡ও আইন অমান্য করে নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন ও ব্যবহার করা হচ্ছে জানান জামালউদ্দীন আহমদ।
জামালউদ্দীন আহমদ বলেন, প্লাস্টিকের ব্যবহার বাড়লেও এটি রিসাইকেল ও রি-ইউজের পরিমাণ না বাড়ায় এসব প্লাস্টিকের অধিকাংশই সরাসরি চলে যাচ্ছে পরিবেশে। গত ৫০ বছরে পুরো বিশ্বে মাথাপিছু এক টনের বেশি প্লাস্টিকের বিভিন্ন পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। যার ৯০ শতাংশের বেশি পৃথিবীর পরিবেশকে নানাভাবে বিপন্ন করে তুলেছে। ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি এবং ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। আবার প্লাস্টিক পোড়ালেও টক্সিস গ্যাস হবে। এটিও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক।
সমুদ্রবিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদরা গভীর উদ্বেগের সাথে বলছেন, বঙ্গোপসাগরে ক্রমাগত দূষণ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। বিশেষত প্লাস্টিক ও পলিথিন সামগ্রীর দূষণ গ্রাস করছে সমুদ্রের পরিবেশ-প্রকৃতিকে। অপচনশীল প্লাস্টিক ও পলিথিনের আগ্রাসনে মূল্যবান মাছ-চিংড়িসহ প্রাণিকুল বিপন্ন প্রায়। ক্রমবর্ধমান দূষণের ফলে সমুদ্রের তলদেশে প্লাস্টিক-পলিথিনের পুরো আস্তর পড়ে যাচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিজগতের বিচরণ ও প্রজননপ্রক্রিয় হচ্ছে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত। এর পরিণতিতে দেশের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের আধার বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে ‘ব্লু-ইকোনমি’ বা ‘নীল অর্থনীতির’ সুফল অর্জন ব্যাহত হচ্ছে।
সমুদ্র ও এর সংলগ্ন উপক‚লজুড়ে পলিথিন, প্লাস্টিকজাতীয় সামগ্রীর এখন অবাধ ছড়াছড়ি। বোতল, বক্স, শপিংব্যাগ থেকে শুরু করে নানা ধরনের এসব উপকরণ সাগরের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। যা সমুদ্রজগতের ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে নীরব ঘাতকের মতোই।
সমুদ্র ও পরিবেশবিশেষজ্ঞরা জানান, বঙ্গোপসাগরে দৈনিক হাজারো টন প্লাস্টিক, রাবার ও পলিথিনের সামগ্রী বা এসবের বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। আর সেই প্লাস্টিক, রাবার ও পলিথিনের বর্জ্যকণা (মাইক্রোপ্লাস্টিক) খাবারের সঙ্গে গিলে ফেলছে নানা প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ ও প্রাণী। সেখান থেকে খাদ্য চেইনে খাবার হিসেবে মাছের সাথে অজান্তেই মানুষের পেটে ঢুকে যাচ্ছে। এই মাছে যুক্ত থাকা প্লাস্টিক ও পলিথিনের কণা বা বর্জ্যাংশ ক্যান্সার, কিডনি বিকল, পাকস্থলীর সংক্রমণসহ বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক রোগ-ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
জাতিসংঘের পরিবেশবিষয়ক অঙ্গসংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বার্ষিক ৮০ লাখ মেট্রিক টনেরও বেশি পরিমাণ প্লাস্টিক ও পলিথিন দ্রব্য সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। বাস্তব পরিমাণ আরো বেশিও হতে পারে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে বঙ্গোপসাগরে কী পরিমাণ প্লাস্টিক-পলিথিন নিক্ষিপ্ত হচ্ছে এর সঠিক তথ্য নেই। এ অবস্থা চললে ২০৫০ সাল নাগাদ সাগর-মহাসাগরে মাছের চেয়ে প্লাস্টিক বর্জ্যরে পরিমাণই বেশি হবে বলে সতর্ক করেছে জাতিসংঘ। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কমপক্ষে ৬০০ প্রাণী। এ ক্ষেত্রে ভয়াবহ ঝুঁকিতে আছে বাংলাদেশ এবং এর সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল। কেননা মাছসহ সামুদ্রিক প্রাণী গলা ও পেটে প্লাস্টিক, পলিথিন বর্জ্য আটকে মারা পড়ছে। ব্যাহত হচ্ছে বংশবৃদ্ধি। সি-গালসহ সমুদ্রে বিচরণশীল পাখিরাও হচ্ছে বিপন্ন। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন সাগর-উপসাগরের মতো বঙ্গোপসাগর মাছশূন্য হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা আর্থ ডে নেটওয়ার্ক-এর প্রতিবেদন বলছে, বিশ্বের শীর্ষ প্লাস্টিক-পলিথিন দূষণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দশম। অবাধে ব্যবহার করা হচ্ছে প্লাস্টিক-পলিথিনসামগ্রী। এতে মাছের স্বাভাবিক মজুদ ও বংশবিস্তারে বিপর্যয় ঘটছে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্রবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এবং ইনস্টিটিউট অব ফিশারিজের সাবেক পরিচালক সমুদ্রবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. হোসেন জামাল বলেন, বঙ্গোপসাগরে প্লাস্টিক, রাবার ও পলিথিন বর্জ্যদূষণ সারা বিশ্বে আলোচিত এবং আশঙ্কাজনক বিপদের কারণ। সাগরে নিক্ষিপ্ত প্লাস্টিক ও পলিথিন দ্রব্যসামগ্রী প্রথমে বড় বড় টুকরা হিসেবে ভাসে বা পানির মধ্যে ঝুলে থাকে। এরপর সামুদ্রিক আবহাওয়ায় ভেঙে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা (মাইক্রোপ্লাস্টিক) হিসেবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এসব সামগ্রী ক্রমাগত ছোট হতে হতে প্রসারিত হতে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মাছসহ সামুদ্রিক প্রাণীর খাদ্যচক্রে মাইক্রো-প্লাস্টিকগুলো পেটের পাকস্থলীতে ঢুকে যায়। প্লাস্টিক-পলিথিন বড় সাইজ হলে গলায় আটকে মারা যায়। ক্ষুদ্র হলে মাছেরা গিলে ফেলে। সবচেয়ে বিপদের দিকটি হচ্ছে, আমরা যখন সেই মাছ বা সামুদ্রিক প্রাণীগুলো খাচ্ছি, তখন খাবারের সঙ্গে প্লাস্টিক-পলিথিন মানবদেহে এসে যাচ্ছে। ঘটছে নানাবিধ রোগব্যাধির কারণ।
তিনি বলেন, সমুদ্রের পানির প্রথম, দ্বিতীয়সহ সব লেয়ারেই প্লাস্টিক-পলিথিন বর্জ্যরে দূষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতে করে সামুদ্রিক মাছসহ প্রাণীর জন্য প্লাস্টিক-পলিথিন বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা মারাত্মক বিপদ ডেকে আনছে। এর সমাধান হলো অবিলম্বে যাবতীয় প্লাস্টিক-পলিথিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে বিকল্প হিসেবে পাটজাতসামগ্রীর ব্যবহার এবং তার ব্যাপক প্রচলন।
জানা গেছে, ১৯৮৯ সালের বেসেল কনভেনশন অনুসারে বাংলাদেশে পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যাগ এবং সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় প্রণীত ‘মাল্টিসেক্টোরাল অ্যাকশন প্ল্যান ফর সাসটেইনেবল প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ’-এ ২০৩০ সাল নাগাদ ৫০ শতাংশ ভার্জিন ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার হ্রাস করা, ২০২৬ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যা কাগজে-কলমেই লেখা আছে, বাস্তবে বিগত ১৬ বছরেও এর কোনো প্রয়োগ নেই। ফলে এর কার্যকারিতা এখনো দেখা যাচ্ছে না।



 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন



-20251031020255.webp)















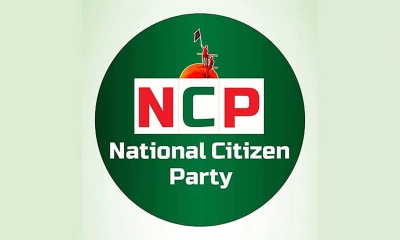






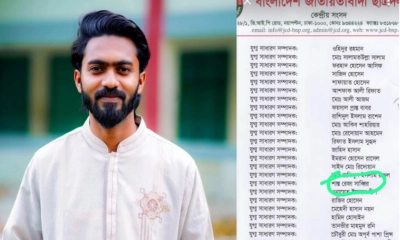
-20251025002118.webp)
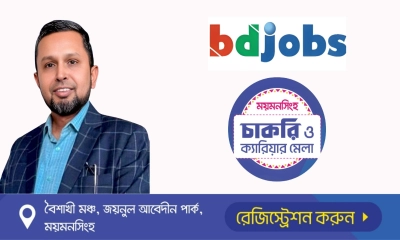




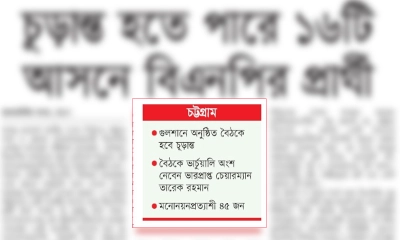

আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন