বাংলাদেশের যুবসমাজ আজ এক ভয়াবহ সংকটে নিমজ্জিত। মাদকাসক্তির ক্রমবর্ধমান প্রবণতা কেবল ব্যক্তি নয়, পরিবার ও সমাজকে ভেঙে দিচ্ছে নিঃশব্দে। এই দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের দায়িত্ব এখন শুধুই নীতিপত্র প্রণয়নে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, প্রয়োজন বাস্তবভিত্তিক ও জোরালো কর্মকৌশল। কেননা, মাদকের থাবা শুধু শহরেই নয়, গ্রামগঞ্জেও বিষের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।
আর এর প্রভাবে বাড়ছে বেওয়ারিশ লাশের মিছিল। মাত্র ৪৫ দিনেই উদ্ধার করা হয়েছে ২৮টি মরদেহ। যাদের মৃত্যু নিয়ে আক্ষেপ নেই কারো, কাঁদে না কেউ। হায় রে মৃত্যু! বিদায়ের সময় কপালে জোটে না প্রিয়জনের স্পর্শ। মৃত্যু ঘিরে চারপাশে নেই কোনো আহাজারি। দুফোঁটা চোখের জল ফেলার জন্যও নেই কোনো আপনজন। এসব মৃত্যুর ঘটনার নেপথ্য খুঁজতে রূপালী বাংলাদেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বিভিন্ন ফুটপাত এবং ঢামেকের পাশর্^বর্তী এলাকায় সরেজমিন অনুসন্ধান চালিয়েছে। অনুসন্ধানে উঠে এসেছে এক ভয়াবহ চিত্র।
সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এসব এলাকায় ভবঘুরে, ভাসমান পতিতা, অসামাজিক কাজে লিপ্ত তৃতীয় লিঙ্গ বেশধারী হিজড়া, ছিনতাইকারী আর মাদকাসক্তদের অনেকটা জমজমাট মেলা বসে। বিশেষ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের পাশে পুলিশ ক্যাম্পের অদূরের অন্ধকার গলি, হাসপাতালের বহির্বিভাগের চারপাশের খোলা জায়গা, চানখাঁরপুল, দোয়েল চত্বর থেকে শুরু করে শহিদ মিনারের চারপাশ এবং শিববাড়ি এলাকা।
দিনভর তো চলেই সন্ধ্যার পর থেকে এসব এলাকায় প্রকাশ্যে চলে মাদক (বিশেষ করে হেরোইন, পেথিডিন ইনজেকশন, ইয়াবা এবং ফেনসিডিল) বেচাকেনা। আর এসব মাদকের নিরাপদ সেবনের জায়গা হচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকার অভ্যন্তরে চারপাশের খোলা জায়গা।
সার্বক্ষণিক হাসপাতালের ক্যাম্প পুলিশ ও আনসার মোতায়েন থাকলেও তাদের ম্যানেজ করেই চলে এদের আনাগোনা। আর একের পর এক যে অজ্ঞাত মরদেহ উদ্ধার হচ্ছে, সেগুলোর অধিকাংশই এসব মাদকসেবীর।
একাধিক মাদকসেবীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এই এলাকায় তারা সংখ্যায় ৫০-৬০ জনের মতো। সবারই পেশা ছোটখাটো চুরি আর সুযোগ পেলে ছিনতাই। শুধু দুবেলা খাবার আর নেশার টাকা জোগাতেই তারা এসব অপরাধ করে। তবে খাবারের চেয়ে নেশাই তাদের কাছে মুখ্য। তারা আসলে কেউ কাউকে চেনেন না। পানির ওপর ভাসমান কচুরিপানার মতো ভাসতে ভাসতে তারা এক হয়েছেন। বাবা-মা থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজন কেউ আছেন কি না সেটা জানার প্রয়োজনও তারা মনে করেন না।
মাদকসেবীদের মধ্যে যারা মারা যায়, তারা অধিকাংশই একে অপরের পরিচিত, তবে আসল নাম-ঠিকানা কেউ জানেন না এবং জানলেও ঝামেলা মনে করে কাউকে বলেন না।
সম্প্রতি বছরগুলোতে দেখা যায়, কিশোরদের মাঝে ইয়াবা, গাঁজা, ফেনসিডিলের মতো মাদকের ব্যবহার উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। মাদকের উৎস এবং এর পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান থাকলেও, পুনর্বাসন ও সচেতনতা কার্যক্রমে ঘাটতি রয়ে গেছে। সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের অধীনে যে মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রগুলো রয়েছে, সেগুলোর সেবার মান ও সক্ষমতা প্রশ্নবিদ্ধ। অধিকাংশ কেন্দ্রেই নেই পর্যাপ্ত পরামর্শদাতা, মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ কিংবা কর্মসংস্থানভিত্তিক পুনর্বাসন ব্যবস্থা।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন-২০১১, ১০(২) বিধি অনুযায়ী এদের আটক করে সমাজসেবা অধিদপ্তরের হেফাজতে দেওয়ার কথা। প্রকৃত নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও উল্লেখ আছে এ আইনে। আইনে বলা আছে, পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিচে নয় এমন কর্মকর্তা অথবা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, কোনো ব্যক্তিকে ভবঘুরে বলে গণ্য হলে ওই ব্যক্তিকে যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো সময় আটক করে ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে ভবঘুরে আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠাবেন। কিন্তু বাস্তবে এই সেবা ক’জনার ভাগ্যে জুটছে। মাঝেমধ্যে ভিক্ষুকদের এই আইনের আওতায় আটক করা হলেও এই মাদকাসক্ত ভবঘুরেরা থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। সরকার ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যদি সঠিকভাবে কাজ করতে না পারে তাহলে এই বেওয়ারিশ লাশের মিছিল বাড়বে বৈ কমবে না।
একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দেশের প্রতি ১০০ জন মাদকাসক্তের মধ্যে মাত্র ৫-৭ জন চিকিৎসা বা কাউন্সেলিংয়ের আওতায় আসেন। বাকিরা থেকে যান অন্ধকারে, অপরাধে জড়িয়ে পড়েন, অথবা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অথচ সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর চাইলে জেলা পর্যায়ে মাদক প্রতিরোধ সেল গঠন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরিবার ও কমিউনিটির সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে।
এ ছাড়া, যেসব যুবক নিরাময় কেন্দ্রে এসে সুস্থ হন, তাদের কর্মজীবনে ফেরানোর জন্য সরকারের ‘সোশ্যাল রিইনটেগ্রেশন’ কর্মসূচি থাকা জরুরি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ থাকলেও, তার সঠিক বাস্তবায়ন বা তদারকি নেই বললেই চলে।
শুধু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান দিয়ে মাদক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এটি একটি সামাজিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক ইস্যু। যার সমাধান চাই বহুমাত্রিক কৌশলে। সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরকে শুধু পুনর্বাসন কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিরোধমূলক শিক্ষা, সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন এবং পরিবারকেন্দ্রিক কাউন্সেলিং কার্যক্রম চালাতে হবে। এনজিও ও তরুণ স্বেচ্ছাসেবীদের সম্পৃক্ত করে একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করতে হবে মাদকবিরোধী প্রচেষ্টাকে।
আমরা আশা করব সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর কার্যকর ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা, আধুনিক কাউন্সেলিং ব্যবস্থা ও পুনর্বাসনভিত্তিক সামাজিক সহযোগিতা দিয়ে এই মহামারি রুখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তা না হলে, অদৃশ্য কিন্তু ভয়ঙ্কর মাদকের থাবা একদিন পুরো জাতিকে পঙ্গু করে দেবে।
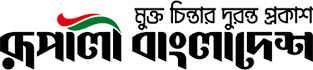







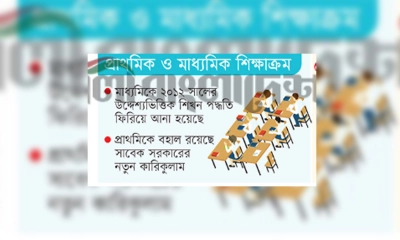




















-20250712142006.webp)











আপনার মতামত লিখুন :