প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক চিরন্তন। প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যেই মানুষের বসবাস। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অস্তিত্ব এক সুতায় বাঁধা। নিজের অস্তিত্বের জন্যই মানুষকে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হয়। বলা হয়ে থাকে, মানুষ হচ্ছে প্রকৃতির সন্তান। এ আপ্তবাক্য কতটা সত্য, সেটা প্রমাণের জন্য মানবজাতির উৎপত্তিসংক্রান্ত বহু প্রাচীন বিতর্কে যেতে হবে না; বরং সাধারণ কা-জ্ঞান থেকেই প্রমাণিত, প্রাকৃতিক ব্যবস্থা সুষ্ঠু না থাকলে মানুষ বাঁচবে না। যেমন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অনিবার্য উপাদান অক্সিজেন দেয় প্রকৃতি।
আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে গাছপালা থেকেই। মানুষ যতই ‘স্মার্ট টেকনোলজি’ আবিষ্কার করুক না কেন, খাদ্য ও পানীয় কিন্তু প্রকৃতি থেকেই আহরণ করতে হয়। এমনকি অন্যান্য মৌলিক চাহিদা যেমন- বস্ত্র, বাসস্থান সবই এখনো ব্যাপকভাবে প্রকৃতিনির্ভর। মোদ্দাকথা, জন্ম থেকে মৃত্যু-মানবজাতির অস্তিত্ব নির্ভর করছে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা, তথা জীববৈচিত্র্যের টিকে থাকা ও সুস্থতার ওপর।
তবে দুই শতক ধরে ঘটছে উল্টোটা। সম্প্রতি এক গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, উনিশ শতকের শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংযোগ কমেছে ৬০ শতাংশেরও বেশি। এমনকি এ সময়ের মধ্যে দিন যত গড়িয়েছে বইয়ের পাতা থেকে নদী, শ্যাওলা ও ফুলের মতো প্রাকৃতিক শব্দগুলোর ব্যবহারও তত কমেছে। বইয়ের পাতায় এসব শব্দের ব্যবহার কমে যাওয়ার বিষয়টি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংযোগ কমে যাওয়ারই প্রতিফলন বলে এক গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।
‘মডেলিং নেচার কানেক্টেডনেস উইদিন এনভায়রনমেন্টাল সিস্টেমস: হিউম্যান-নেচার রিলেশনশিপস ফ্রম ১৮০০ টু ২০২০ অ্যান্ড বিয়ন্ড’ শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধটি গত সপ্তাহেই ‘আর্থ’ জার্নালে প্রকাশ হয়েছে। গবেষণাটিতে কম্পিউটার মডেলিংয়ের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, যদি সামাজিক সংস্কৃতিতে ও নীতিগতভাবে ব্যাপক পরিবর্তন না আসে (যেমন অল্প বয়সে শিশুদের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং শহুরে পরিবেশের আমূল সবুজায়ন), তাহলে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংযোগের মাত্রা সামনের দিনগুলোয় আরও কমতে থাকবে। এ দুই পদক্ষেপই সবচেয়ে কার্যকর।
যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইউনিভার্সিটি অব ডার্বির নেচার কানেক্টেডনেস বিষয়ের অধ্যাপক মাইলস রিচার্ডসনের এ গবেষণায় নগরায়ণ, জনবসতির আশপাশের বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাস এবং পিতা-মাতার প্রকৃতির সঙ্গে সন্তানের সংযোগ তৈরি না করার মতো সামাজিক আচরণের তথ্য ব্যবহার করে গত সোয়া দুই শতাব্দীতে জনজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির বিচ্ছিন্নতা বেড়ে যাওয়ার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ গবেষণা চালাতে গিয়ে মাইলস রিচার্ডসন ১৮০০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত বইগুলোয় সময়ের পরিক্রমায় প্রকৃতিসংশ্লিষ্ট শব্দের ব্যবহার কমে যাওয়ার প্রবণতাকে শনাক্ত করেছেন। এ কমে যাওয়ার হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে ১৯৯০ সালে। ওই বছর প্রকাশিত বইয়ে এ ধরনের শব্দের ব্যবহার কমেছিল ৬০ দশমিক ৬ শতাংশ।
রিচার্ডসন নির্মিত মডেল থেকে পাওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে প্রকৃতি সচেতনতা ক্রমাগত হারিয়ে যাবে। ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ ও তা থেকে প্রকৃতির উপস্থিতি ক্রমেই হারিয়ে যাওয়ার কারণে এক ধরনের ‘অভিজ্ঞতার বিলোপ’ চলছে। পিতা-মাতারাও আর সন্তানদের প্রকৃতি অভিমুখী করছেন না। অন্যান্য সমীক্ষায়ও দেখা গেছে, শিশুরা প্রকৃতির কতটা কাছাকাছি হবে তা এর সঙ্গে পিতা-মাতার সংযোগের ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে।
রিচার্ডসন বলেন, ‘প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগের অভাবকে এখন পরিবেশগত সংকটের একটি প্রধান কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এটি আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণকে সাধারণ একটি জায়গায় নিয়ে আসে। প্রকৃতির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বদলাতে গেলে ব্যাপক মাত্রায় রূপান্তরগত পরিবর্তনের প্রয়োজন।’
সাধারণ একটি শহরে জীববৈচিত্র্যপূর্ণ সবুজ স্থানের পরিমাণ ৩০ শতাংশ বাড়ানো গেলেই সেটিকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও জনজীবনে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হিসেবে দেখা হয়। যদিও রিচার্ডসনের গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংযোগ কমে যাওয়ার ধারাটিকে বদলে দিতে হলে একেকটি শহরকে এখনকার চেয়ে ১০ গুণ বেশি সবুজ করতে হতে পারে।
গবেষণায় দেখা গেছে, প্রকৃতির সঙ্গে জনসাধারণের সম্পৃক্ততা বাড়াতে নেওয়া প্রচলিত উদ্যোগগুলো দীর্ঘমেয়াদে খুব একটা কার্যকর নয়। এ নিয়ে বিভিন্ন দাতব্য সংস্থার নানা প্রকল্প প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মানসিক সংযোগের উন্নতিতে এখনো গুরুত্বপূর্ণ। তবে রিচার্ডসনের মডেলিং বলছে, এগুলো প্রজন্মান্তরে মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সংযোগের অবক্ষয় ঠেকানোয় কার্যকর নয়। এর চেয়ে ফরেস্ট স্কুল নার্সারির মতো প্রকল্পগুলো শিশু ও তার পরিবারের মধ্যে প্রকৃতি সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা গড়ে তোলায় অনেক বেশি কার্যকর।






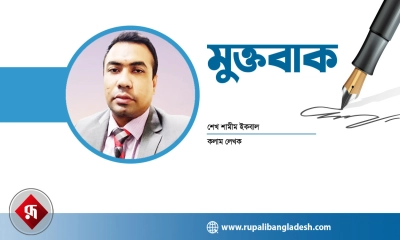
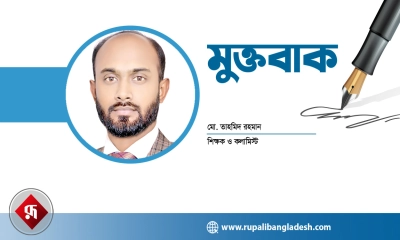
-20250829032810.webp)
-20250829033015.webp)


-20250830044100.webp)





-20250830020350.webp)










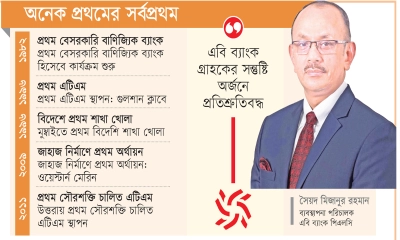






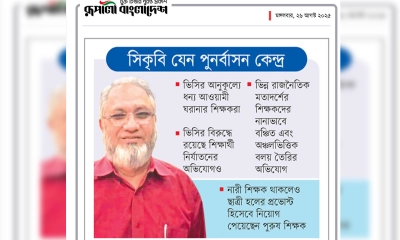



-20250828003001.webp)
আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন