কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা কৃত্রিম মেধা (কেএম) একসময় ছিল শুধুই বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির অংশ। কিন্তু আজ এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা হয়ে উঠেছে। মোবাইল ফোনের সহকারী থেকে শুরু করে রোগ নির্ণয়ে সাহায্যকারী প্রযুক্তি, এমনকি স্বয়ংচালিত গাড়ি- সবখানেই এর প্রয়োগ দেখা যায়।
তবে এই প্রযুক্তির যাত্রা শুরু হয়েছিল বহু বছর আগে, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের কল্পনা এবং গবেষণার মধ্য দিয়ে।
প্রাচীন ভাবনা ও স্বপ্ন
কৃত্রিম মেধার ধারণা একেবারে নতুন নয়। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল যুক্তির একটি পদ্ধতি প্রস্তাব করেছিলেন, যাকে আজকের লজিক বা যুক্তিতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। এমনকি বহু প্রাচীন কালে চিন্তাবিদেরা এমন যন্ত্রের কথা কল্পনা করেছিলেন, যা মানুষের মতো চিন্তা করতে পারবে। তবে সেটি ছিল কেবল কল্পনার জগতে সীমাবদ্ধ।
আধুনিক কালের সূচনা: ১৯৪০-এর দশক
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আধুনিক ইতিহাস শুরু হয় বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ১৯৪৩ সালে, ওয়্যারেন ম্যাককালক এবং ওয়াল্টার পিট নামক দুই বিজ্ঞানী প্রথমবারের মতো একটি গাণিতিক মডেল তৈরি করেন, যা মানুষের মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালী অনুকরণ করতে পারে। এটি ছিল নিউরনের প্রাথমিক ধারণা।
এরপর ১৯৫০ সালে বিখ্যাত ব্রিটিশ গণিতবিদ অ্যালান টিউরিং একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন: ‘যন্ত্র কি চিন্তা করতে পারে?’
তিনি একটি পরীক্ষা প্রস্তাব করেন, যা আজ টিউরিং পরীক্ষা নামে পরিচিত। এটি আজও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মান যাচাইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ শব্দটির জন্ম
১৯৫৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ডার্টমাউথ কলেজে এক সম্মেলনে ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ শব্দটির আনুষ্ঠানিক ব্যবহার শুরু হয়। এই সম্মেলনে জন ম্যাককার্থি, মারভিন মিনস্কি, ক্লড শ্যানন ও অ্যালেন নিউয়েল সহ একদল বিজ্ঞানী অংশ নেন। এখান থেকেই কৃত্রিম মেধা একটি স্বতন্ত্র গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে গড়ে ওঠে।
প্রথম স্বর্ণযুগ: ১৯৫৬–১৯৭৪
এই সময়ে বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের প্রোগ্রাম তৈরি করেন যা সমস্যার সমাধান করতে পারে, গাণিতিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, এমনকি যুক্তি বিশ্লেষণ করতেও সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, ‘এলিজা’ নামক একটি প্রাথমিক কম্পিউটার প্রোগ্রাম মানুষের মতো কথোপকথন চালাতে পারত।
মন্দার সময়: ১৯৭৪–১৯৮০
প্রাথমিক অগ্রগতির পর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণায় একটি ধীরগতি আসে। উচ্চ প্রত্যাশার বিপরীতে ফলাফল ছিল সীমিত, এবং যন্ত্রগুলো খুব সহজ সমস্যা সমাধানেই ব্যর্থ হচ্ছিল। ফলে সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা কমে যায়, যাকে বলা হয় ‘কৃত্রিম মেধার শীতল যুগ’।
পুনরুত্থান: ১৯৮০–১৯৯০
১৯৮০-র দশকে ‘বিশেষজ্ঞ পদ্ধতি’ বা এক্সপার্ট সিস্টেম নামক একটি নতুন ধারার আবির্ভাব ঘটে। এটি এমন একধরনের প্রোগ্রাম যা কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই প্রযুক্তি ব্যবসা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।
আধুনিক যুগে প্রবেশ: ২০০০-এর দশক থেকে শুরু
বিগত দুই দশকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করেছে। এর পেছনে ছিল তথ্য সংগ্রহের বিপুল পরিমাণ, উন্নত গাণিতিক মডেল, এবং শক্তিশালী যন্ত্রাংশ। বিশেষ করে ‘গভীর শিক্ষণ’ বা ডিপ লার্নিং ও ‘যন্ত্র শিক্ষণ’ বা মেশিন লার্নিং-এর মাধ্যমে কৃত্রিম মেধা অনেক বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে।
২০১০ সালের পর থেকে কৃত্রিম মেধা ব্যবহার করে ভাষা অনুবাদ, মুখ চিনে নেওয়া, চিত্র বিশ্লেষণ, এমনকি গল্প লেখার মতো কাজও করা সম্ভব হচ্ছে।
চ্যাটযন্ত্র ও স্বয়ংক্রিয় সহকারী
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক কথোপকথনের যন্ত্র বা চ্যাটবট ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এছাড়াও গৃহস্থালি কাজে সাহায্যকারী যন্ত্র, রোবট, কণ্ঠস্বর চিনে নেওয়া বা স্বয়ংক্রিয় সুপারিশ প্রযুক্তি সবই কৃত্রিম মেধার বাস্তব প্রয়োগ।
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ
যদিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অনেক সুবিধা নিয়ে এসেছে, তবু এটি নিয়ে কিছু আশঙ্কাও রয়েছে। যেমন- মানুষের কর্মসংস্থান হ্রাস, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন, এবং যন্ত্রের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা। অনেক বিশেষজ্ঞই বলছেন, কৃত্রিম মেধার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে নৈতিকতা, নিয়ন্ত্রণ ও মানবিক মূল্যবোধ বজায় রাখার ওপর।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতিহাস এক দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় যাত্রা। এটি কখনও শূন্য থেকে আকাশে উঠেছে, আবার কখনও ব্যর্থতার গহ্বরে পড়েছে। তবে আজ আমরা এমন এক যুগে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে এই প্রযুক্তি আমাদের সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা ও প্রতিদিনের জীবনকে আমূল বদলে দিচ্ছে। এখন সময়, এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গিয়ে মানবকল্যাণের দিকে এগিয়ে চলার।


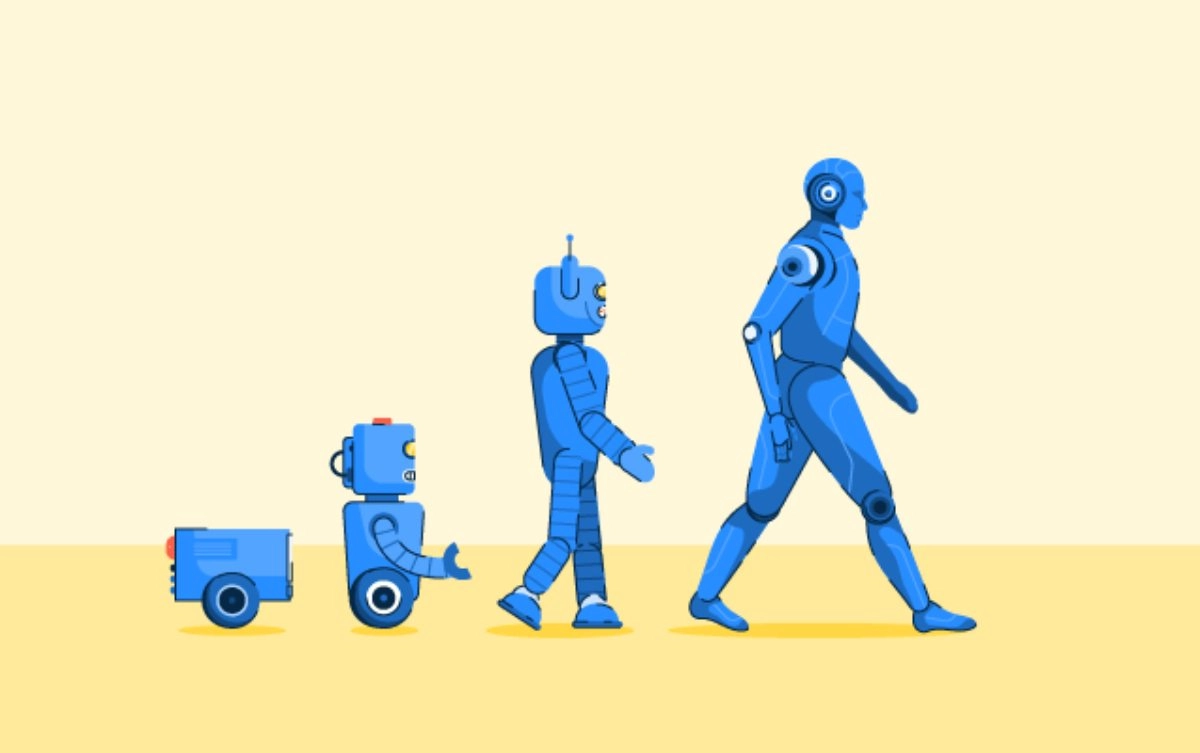
 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন



























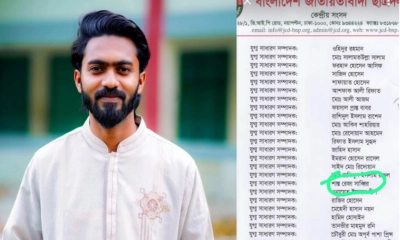
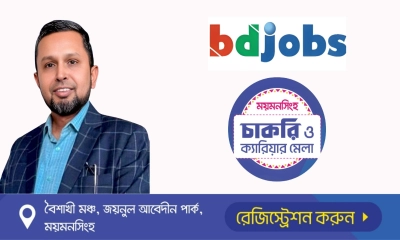

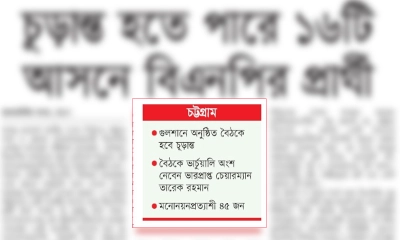






আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন