কাঁচামাল তৈরি হচ্ছে চীনে। আর শিল্পের চাকা ঘুরছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের উন্নয়নে এই চাকা ঘুরছে বহু বছর ধরে। বিষয়টি আরও সহজ করে বলা যাক, দেশের অর্থনীতি শিল্পের চাকা ঘুরানোর যে শক্তি সঞ্চয় করছে তার বড় অংশই চীনের পণ্য দিয়ে। অর্থাৎ কাঁচামাল আর যন্ত্রপাতির অবদান। চট্টগ্রাম বন্দরে প্রতিদিন যেসব কনটেইনারবাহী ট্রাক ঢাকার দিকে দিকে ছুটে চলে, তার অনেকগুলোর ভেতরে থাকে ‘মেড ইন চায়না’ লেখা যন্ত্রাংশ, পোশাক, ইলেকট্রনিক-সামগ্রীসহ বিভিন্ন কাঁচামাল। অপরদিকে কনটেইনার ভরে বন্দরের গেট পেরিয়ে ইউরোপ-আমেরিকায় যাচ্ছে ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ পণ্য। এই যাওয়া-আসার গল্পের উন্নয়নের বন্ধন তৈরি করেছে চীন। যেমন সুই-সুতা থেকে যুদ্ধবিমানÑ সবই আসছে চীন থেকে। সাবমেরিন থেকে মোবাইল ফোনের স্ক্রিন প্রোটেক্টরÑকী নেই দেশটির পণ্যতালিকায়! এত বিশাল পণ্যসম্ভারে ভর করে বাংলাদেশের একজন স্বল্প পুঁজির সম্ভাবনাময় তরুণও উদ্যোক্তা হতে পারছেন। কিন্তু চীনে শুল্কমুক্ত ট্যারিফ সুবিধা থাকার পরও বিশাল বাজার ধরতে পুরোপুরি ব্যর্থ বাংলাদেশ। অথচ একই সুবিধা নিয়ে দেশটিতে দারুণ ব্যবসা করছে ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চীনের বাজার বিবেচনায় আমাদের উৎপাদন কৌশল ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে হবে। একই সঙ্গে বাণিজ্য সহায়ক নীতিমালা এবং লজিস্টিক সুবিধা বাড়ানোর মাধ্যমে চীনের বাজারে আমাদের অবস্থান শক্তিশালী করতে হবে।
চীনের পণ্য কীভাবে স্থানীয় উৎপাদন বাড়াচ্ছে, তার একটি সহজ সমীকরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যখন বাংলাদেশের একজন উদ্যোক্তা সুলভ মূল্যে চীনের সেরা মানের যন্ত্রপাতি বা টেক্সটাইল কাঁচামাল আমদানি করতে পারেন, তখন তাঁর উৎপাদন খরচ কমে আসে। এই কম উৎপাদন খরচ দেশীয় পণ্যের দাম বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতামূলক করে তোলে। চীন বাংলাদেশের পোশাক খাতের জন্য কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী। এর মধ্যে রয়েছে বিপুল পরিমাণ সুতা, ফ্যাব্রিকস। ওভেন কাপড়ের প্রায় ৮০ শতাংশ এবং নিট কাপড়ের ১৫-২০ শতাংশ, রং, ডাইস, কেমিক্যাল এবং বিভিন্ন অ্যাকসেসরিজ। শুধু পোশাকশিল্প নয়, প্লাস্টিক, চামড়া, ইলেকট্রনিকস এবং হালকা প্রকৌশল খাতেও চীনের প্রযুক্তিনির্ভর কাঁচামাল ব্যবহার করে স্থানীয় উদ্যোক্তারা সফলভাবে দেশীয় পণ্য উৎপাদন করছেন। এটি শিল্পের বৈচিত্র্য বাড়াতে সাহায্য করছে। চীন থেকে আমদানি করা কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদিত পণ্যই মূলত বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের মূল ভিত্তি।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সর্বশেষ তথ্য বলছে, আগের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে মাত্র এক বছরের ব্যবধানে চীন থেকে পণ্যের আমদানি বেড়েছে প্রায় ১৪ লাখ ৩২ হাজার টন। আর এর পেছনে খরচ বেড়েছে ৪৫ হাজার ৫২৮ কোটি টাকা। এনবিআরের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় আরো জানা যায়, সর্বশেষ অর্থবছরে কয়েক হাজার পণ্য আমদানি হয়েছে। উল্লেখযোগ্য পণ্যের মধ্যে সুতা আসে ৯ হাজার ৩০৭ কোটি টাকার, কৃত্রিম সুতা ছয় হাজার ৪৪৩ কোটি টাকা, রঙিন জিন্সের কাপড় ছয় হাজার ১৯০ কোটি টাকা, সিনথেটিক ফাইবার পাঁচ হাজার ১৩০ কোটি টাকা, পলিয়েস্টার সুতা চার হাজার ৪০৭ কোটি টাকা, ইলেকট্রনিক সার্কিট তিন হাজার ৭৯১ কোটি টাকা, পলিপ্রোপাইলিন তিন হাজার ৪৮৯ কোটি টাকা, ওভেন ফ্যাব্রিকস তিন হাজার ১৪২ কোটি টাকা, রসুন দুই হাজার ৪০২ কোটি টাকার। এ ছাড়া খনিজ জ্বালানি দুই হাজার ২২৭ কোটি টাকা, লোহা ও স্টিল উৎপাদনের উপকরণ দুই হাজার ৮০ কোটি টাকা, প্রাথমিক পলিপ্রোপাইলিন দুই হাজার ৬০ কোটি টাকা, ডিসপ্লে মডিউলস ও টাচ সেনসিটিভ স্ক্রিন এক হাজার ৮৫৫ কোটি টাকা, পেপার ও পেপারবোর্ড এক হাজার ৭৬৮ কোটি টাকার আমদানি হয়েছে। চলতি বছরের এপ্রিলে চীনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে জে-১০সি মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান কেনার আলোচনা করেছিল সরকার। পরে ২২০ কোটি ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২৭ হাজার ৬০ কোটি টাকা) ব্যয়ে চীনের তৈরি ২০টি জে-১০সি মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান কেনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই ব্যয়ের মধ্যে এয়ারক্রাফট কেনা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য খরচ অন্তর্ভুক্ত। এই বিমান দেশের বিমানবাহিনীর বহরে যুক্ত হলে দেশের আকাশে প্রবেশ করা শত্রুর জন্য বিপজ্জনক হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি দেশের সামরিক খাতেও সহায়তা করছে চীন।
চীনা পণ্যের দাপট বাংলাদেশে
বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনবিআরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, পণ্য আমদানির উৎস হিসেবে একসময় বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের প্রথম পছন্দের দেশ ছিল ভারত। এক যুগ আগে তা পাল্টে গেছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে চীনা পণ্যের দাপট চলছে বাংলাদেশের বাজারে। এখনো তা বজায় আছে। অর্থাৎ পণ্য আমদানিতে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের প্রথম পছন্দের দেশ এখন চীন। এরপর ভারতের অবস্থান। বিগত কয়েক দশকের আমদানির কিছু পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরে ১১ কোটি ডলারের পণ্য আসে চীন থেকে। সেখানে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে আসে প্রায় ২০৮ কোটি ডলারের পণ্য। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯-১০ অর্থবছরে চীন থেকে আমদানি হয় প্রায় ৩৮২ কোটি ডলারের পণ্য। এভাবে চলতে চলতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এসে চীন থেকে আসে ১ হাজার ৫৫৮ কোটি ২০ লাখ ডলারের পণ্য। কোভিড-১৯ মহামারি শুরু হলে পণ্য আমদানি আগের অর্থবছরের তুলনায় কমে যায়। ওই বছর চীন থেকে আমদানি হয় ১ হাজার ৪৩৬ কোটি ডলারের পণ্য। তবে কোভিড একটু দুর্বল হয়ে এলে চীন থেকে ব্যাপকভাবে বাড়ে পণ্য আমদানি। ২০২১-২২ অর্থবছরে চীন থেকে আমদানি হয় ২ হাজার ৪২৫ কোটি ডলারের পণ্য। চীন থেকে বাংলাদেশে ৫ হাজারের বেশি ধরনের পণ্য আমদানি হয়ে থাকে। যার মধ্যে মূলধনী যন্ত্রপাতি, তৈরি পোশাকের বিভিন্ন কাঁচামাল, প্লাস্টিক পণ্য, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, প্রায় সব ধরনের তুলা, লোহা ও ইস্পাত, রাবার সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র, কমলাজাতীয় ফল, কাগজ ও কাগজের বোর্ড, অস্ত্র ও গোলাবারুদের যন্ত্রাংশ, সৌর প্যানেলের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও ব্যাটারি রয়েছে।
চীনা পণ্যের আমদানি বৃদ্ধির বিষয়ে সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশে চীনা পণ্য আমদানির অধিকাংশই বেসরকারি খাতের মাধ্যমে হয়। আমদানি বেশি হচ্ছে, এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। ভোক্তা কিংবা অর্থনৈতিক কল্যাণে বেশি আমদানি হতেই পারে। আগে অন্যান্য দেশ থেকে হতো। এখন চীনা পণ্য দাম ও মান হিসাবে তুলনামূলক সস্তায় পাওয়া যায়। সেই কারণে আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে মূল বিষয় হলোÑ ওই সব দেশে কেন রপ্তানি বৃদ্ধি করতে পারছি না। আসলে আমাদের বিনিয়োগ আকর্ষণ করার দিকে নজর দিতে হবে। এটা শুধু চীনের জন্য প্রযোজ্য নয়, আমার তো অন্যান্য দেশ থেকেও বিনিয়োগ আসছে না।’
সম্ভাবনাময় চীনা বাজারে বড় সুযোগ বাংলাদেশের
চীনের ১৪০ কোটির বেশি ভোক্তার বিশাল বাজার বাংলাদেশের জন্য এখনো প্রায় শতভাগ পণ্যে শুল্কমুক্ত। এক ঐতিহাসিক সুযোগের দুয়ার খুলে দিয়েছে বেইজিং। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ‘কাগজে-কলমে শতভাগ সুবিধা, বাস্তবে শূন্যতার হাহাকার।’ গত এক দশকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য তিন গুণ বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু এর প্রায় পুরোটা জুড়ে রয়েছে শুধু আমদানি। রপ্তানির পরিমাণ এখনো এক বিলিয়ন ডলারের (১০০ কোটি ডলার) গ-ি পেরোতে পারেনি। বরং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি দুই হাজার ৪৪ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে, যা দেশের মোট বাণিজ্য ঘাটতির এক-তৃতীয়াংশের বেশি। বড় অঙ্কের এই বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে বাংলাদেশের পাশেও দাঁড়িয়েছে চীন। ২০২০ সালে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া ৯৭ শতাংশ পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয় দেশটি। ২০২২ সালে এসে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যসহ ৯৮ শতাংশ বাংলাদেশি পণ্যকে দেওয়া হয় এই সুবিধা। পরের বছর যুক্ত হয় আরো ৩৮৩টি পণ্য। ২০২৩ সালের আগস্টে নতুন করে ১ শতাংশ আর গত ডিসেম্বর থেকে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের শতভাগ পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয় চীনা সরকার। এই সুবিধা ২০২৮ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। ধাপে ধাপে শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতা বাড়ালেও এই সুবিধার সুফল ঘরে তুলতে পারছে না বাংলাদেশ। বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিআই) সাবেক সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা বলেন, ‘চীনে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের পরিধি সীমিত হওয়ায় বাজার সম্প্রসারণে নতুন খাত শনাক্ত করতে হবে। গার্মেন্টস, টেক্সটাইল ও ফার্মাসিউটিক্যালস এই তিনটি খাতে চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা বাংলাদেশের পক্ষে কঠিন। চীন পোশাকশিল্পে তাদের মেশিনারি, দক্ষতা ও কাঁচামাল দিয়ে বিশ্ববাজারে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। আমাদের ব্যাকোয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড লিংকেজ, বাণিজ্য অবকাঠামো ও লজিস্টিক সেবা এখনো চীনের পর্যায়ে পৌঁছায়নি।’ বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জ অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাশরুর রিয়াজ বলেন, ‘পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বাজার চীন আমাদের ৯৮ শতাংশ শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার পরও চীনে রপ্তানি বাড়াতে পারিনি। আমাদের রপ্তানি ঝুড়ি এখনো একটি বা দুটি পণ্যের ওপর নির্ভরশীল। চীন আমাদের তৈরি পোশাক খুব বেশি নেবে না, কারণ তারা নিজেরাই এ খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাদের উৎপাদন সক্ষমতা আরও লাভজনক জায়গায় ব্যস্ত রেখে তারা কিছু পণ্য আমদানি করে থাকে। তারা যেসব পণ্য আমদানি করে সেগুলো আমাদের রপ্তানি ঝুড়িতে নেই, কিছু থাকলেও সেটা তাদের যথেষ্ট পরিমাণ চাহিদামতো বাড়ানো হচ্ছে না। যার ফলে আমাদের রপ্তানিযোগ্য পণ্যে তাদের তেমন চাহিদা নেই।’ বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জ অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাশরুর রিয়াজ বলেন, ‘পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বাজার চীন আমাদের ৯৮ শতাংশ শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার পরও চীনে রপ্তানি বাড়াতে পারিনি। আমাদের রপ্তানি ঝুড়ি এখনো একটি বা দুটি পণ্যের ওপর নির্ভরশীল। চীন আমাদের তৈরি পোশাক খুব বেশি নেবে না, কারণ তারা নিজেরাই এ খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাদের উৎপাদন সক্ষমতা আরো লাভজনক জায়গায় ব্যস্ত রেখে তারা কিছু পণ্য আমদানি করে থাকে। তারা যেসব পণ্য আমদানি করে সেগুলো আমাদের রপ্তানি ঝুড়িতে নেই, কিছু থাকলেও সেটা তাদের যথেষ্ট পরিমাণ চাহিদামতো বাড়ানো হচ্ছে না। যার ফলে আমাদের রপ্তানিযোগ্য পণ্যে তাদের তেমন চাহিদা নেই।’
চীনে অর্থ পরিশোধে দুর্ভোগ ব্যবসায়ীদের
চীনা মুদ্রায় এলসি (ঋণপত্র) খুলতে হিমশিম খাচ্ছেন বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা। ইউয়ানের পর্যাপ্ত জোগান না থাকায় থমকে গেছে বিকল্প মুদ্রায় লেনদেনের উদ্যোগ। অন্যদিকে চীনা ব্যাংকগুলো বাংলাদেশে শাখা খোলার অনুমতি পেতে এক দশকের বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করছে। দুই দেশের ব্যাংকব্যবস্থার সরাসরি সংযোগহীনতা বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বিশাল লেনদেনের মূল অন্তরায় হিসেবে দেখছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। ব্যবসায়ীরা বলছেন, তাঁরা ইউয়ানে এলসি খোলার অনুমতি পেলেও দেশীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো চাহিদামতো ইউয়ান পাচ্ছে না। যেহেতু ইউয়ানের ফ্লো নেই, তাই বিকল্প মুদ্রায় লেনদেনের এই সুযোগটি কাগজে সীমাবদ্ধ থাকছে এবং লেনদেন গতিহীন হয়ে পড়ছে। ইউয়ান সংগ্রহ করার জন্য স্থানীয় ব্যাংকগুলো প্রথমে টাকা দিয়ে ডলার কেনে, সেই ডলার আবার ইউয়ানে রূপান্তর করতে বাধ্য হচ্ছে। এই ডাবল কনভার্সন প্রক্রিয়ায় লেনদেন অতিরিক্ত ব্যয়বহুল করে তুলেছে। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত ২-৩ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত বিনিময় খরচ যোগ হয়। এই উচ্চ আর্থিক ব্যয় সরাসরি পণ্যের আমদানি মূল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, যা দেশের মূল্যস্ফীতিতে প্রভাব ফেলে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের অবস্থান দুর্বল করে দেয়। বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) সভাপতি মো. খোরশেদ আলম বলেন, ‘বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগকারীরা যেসব অর্থ আনছেন, তা যদি ইউয়ানে গ্রহণ করা যায় এবং তা আবার আমদানি বিলের দায় পরিশোধে ব্যয় করলে লেনদেন ব্যয়ে প্রায় ১.৫ শতাংশ সাশ্রয় হবে। এতে উভয় পক্ষই উপকৃত হবে।’ তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে চীনা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা নিয়ে কিছু জটিলতা রয়েছে—বাংলাদেশ ব্যাংক কি অনুমতি দিচ্ছে না, নাকি চীনা ব্যাংকগুলোই আগ্রহ দেখাচ্ছে না, সেটি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। আমাদের দেশের যেসব দুর্দশাগ্রস্ত ব্যাংকের শেয়ার তলানিতে, সেগুলো চীনা উদ্যোক্তারা কিনে নিয়ে ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারেন।’ খোরশেদ আলম বলেন, ‘অন্যদিকে চীনে বাংলাদেশের কোনো ব্যাংকের শাখা খোলার উদ্যোগ নেওয়াও জরুরি, যাতে দ্বিপক্ষীয় আর্থিক লেনদেন আরও সহজ হয়।’
প্রাণ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াছ মৃধা বলেন, ‘চীন চায় আমরা ইউয়ানে লেনদেন করি। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে ইউয়ান পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। সে জন্য এখনো আমরা ডলারেই লেনদেন করছি। রপ্তানি খুবই কম হওয়ার কারণে ইউয়ানের জোগান নেই।’ এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, ‘চীনের সঙ্গে আমাদের আমদানি-রপ্তানির একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। এটা দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কমিয়ে আনা সম্ভব। যদি কোনো ব্যাংক চীনে শাখা খুলতে চায়, তাহলে আমাদের আপত্তি নেই। তারা নিয়ম অনুযায়ী আমাদের কাছে আবেদন করবে এবং আমরা তা বিচার-বিশ্লেষণ করে অনুমোদন দেব।’
দেশে চীনের ব্যাংক চান ব্যবসায়ীরা
বর্তমানে চীনের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি কিংবা কোনো সেবার অর্থ পরিশোধ করতে তিনটি স্তরে লেনদেন করতে হয়। প্রথমে দেশের ব্যবসায়ীরা টাকায় স্থানীয় ব্যাংকগুলোকে আমদানি করা পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধ করেন। স্থানীয় ব্যাংক সেই টাকাকে ডলারে রূপান্তর করে চীনের রপ্তানিকারকের ব্যাংককে পরিশোধ করে। সেই ব্যাংক আবার ডলারকে চীনা মুদ্রা ইউয়ানে রূপান্তরিত করে রপ্তানিকারককে পরিশোধ করে। এই তিন স্তরের লেনদেনে মোটা বিনিময় ফি গুনতে হয় ব্যবসায়ীদের। ব্যবসায়ীরা আশা করছেন, এখানে চীনের কোনো ব্যাংক থাকলে সরাসরি ইউয়ানে লেনদেন হতে পারে। এতে মোট লেনদেন খরচের ২-৩ শতাংশ কমে যাবে। এ ছাড়া ডলারের সংকট ও ডলারের বাড়তি দামের কারণে ব্যাবসায়িক যে ক্ষতি হয় তা-ও কমে আসবে। চীনে রপ্তানি থেকে আয় এবং বিভিন্ন প্রকল্প সহযোগিতার অর্থ মিলিয়ে ২-৩ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের ইউয়ান মজুত রাখা সম্ভব। এই ২ বিলিয়ন ডলারের লেনদেনও যদি ইউয়ানে করা যায়, তবে দেশে ডলারের ওপর চাপ অনেকটাই কমবে। ইউয়ানের মূল্য অনেকটাই স্থিতিশীল হওয়ায় আমদানি খরচও হুটহাট তেমন বাড়বে না বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। প্রায়ই ডলারের বাড়তি দামের কারণে যা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ৬টি দেশের মোট ৯টি বিদেশি ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করছে বাংলাদেশে। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যের ২টি ও পাকিস্তানের ৩টি। অন্যগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া ও শ্রীলঙ্কার ১টি করে ব্যাংক রয়েছে। বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) সভাপতি মো. খোরশেদ আলম বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে আমরা দেশে চীনের একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। এতে নানা দিক থেকে সুবিধা পাওয়া যাবে। তাই আমরা চীনা দূতাবাসে বিভিন্ন প্রস্তাবের সঙ্গে একটি কমার্শিয়াল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও দিয়েছি। তারা প্রস্তাবটি পেয়ে বেশ আগ্রহ দেখিয়েছে।’ বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিআই) সাবেক সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা বলেন, ‘এটা ঠিক, আমাদের হাতে ইউয়ানের মজুত কম থাকে। কারণ চীনে আমাদের রপ্তানি কম। কিন্তু বিভিন্ন প্রকল্পে তাদের সহায়তাসহ হিসাব করলে আমাদের হাতে ২-৩ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের ইউয়ান মজুত হয়। চীনা পণ্য আমদানির জন্য ৩ বিলিয়ন ডলারও যদি আমরা ইউয়ানে পরিশোধ করতে পারি, তা-ও রিজার্ভের ওপর চাপ কমাবে।’ আল মামুন মৃধা বলেন, তারা গত চার-পাঁচ বছর বাংলাদেশে চীনের একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কথা বলে আসছেন চীন দূতাবাসকে। তাঁদের জানা মতে, এ নিয়ে দুই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে কিছুটা আলোচনাও হয়েছে। তবে কী কারণে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই, তা তাঁরা জানেন না।
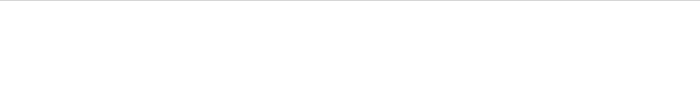



 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন


-20251110031019.webp)

-20251110030752.webp)
-20251110030639.webp)
-20251110030505.webp)



-20251110030407.webp)
-20251110030213.webp)















আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন