মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত কয়েক মাসে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছেন। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, এই পরিবর্তনের ফলে কি চীনের ক্ষমতা বাড়ছে? আবার অনেকে বলছেন, আমেরিকার পিছু হটা চীনের জন্য সুযোগ তৈরি করছে।
তবে এটা এখনও স্পষ্ট নয়, ট্রাম্প কি শুধু কিছু পরিবর্তন আনছেন, নাকি আসলে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে চীনের আধিপত্যের পথ খুলে দিচ্ছেন।
ওয়াশিংটনের পশ্চাদপসরণ স্পষ্ট। ট্রাম্প অনেক প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নীতির বিপরীতে গিয়েছেন। তিনি বিশ্ব বাণিজ্যের উপর কুঠার চালিয়েছেন, জাতিসংঘে অনুদান কমিয়েছেন, বিদেশি সাহায্য কমিয়ে দিয়েছেন, এমনকি ঐতিহ্যগত মিত্রদের সঙ্গেও দ্বন্দ্বে জড়িয়েছেন।
জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ‘খালি ঠোঙা’ করে দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটনের কৌশলগত সক্ষমতা হ্রাস করার ঝুঁকি নিচ্ছেন। ন্যাটো ও অন্যান্য মার্কিন-নির্মিত জোটের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও চাপে ফেলেছেন, যা আমেরিকার দীর্ঘদিনের শক্তির ভিত্তি দুর্বল করছে।
চীন ও আমেরিকার শক্তির ভারসাম্য বদলে যাওয়া নিয়ে বহু বছর ধরেই আলোচনা চলছে। ১৯৮০’র দশকে চীনের বাজার অর্থনীতি গ্রহণ, ১৯৮৭ সালে ইতিহাসবিদ পল কেনেডির ‘দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অফ দ্য গ্রেট পাওয়ারস’ বইয়ে চীনের উত্থান ও আমেরিকার পতনের আভাস, এবং ১৯৯০-এর দশকে চীনের অর্থনৈতিক সংস্কার নিয়ে উইলিয়াম ওভারহোল্টের মতামত সবই এই পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছিল।
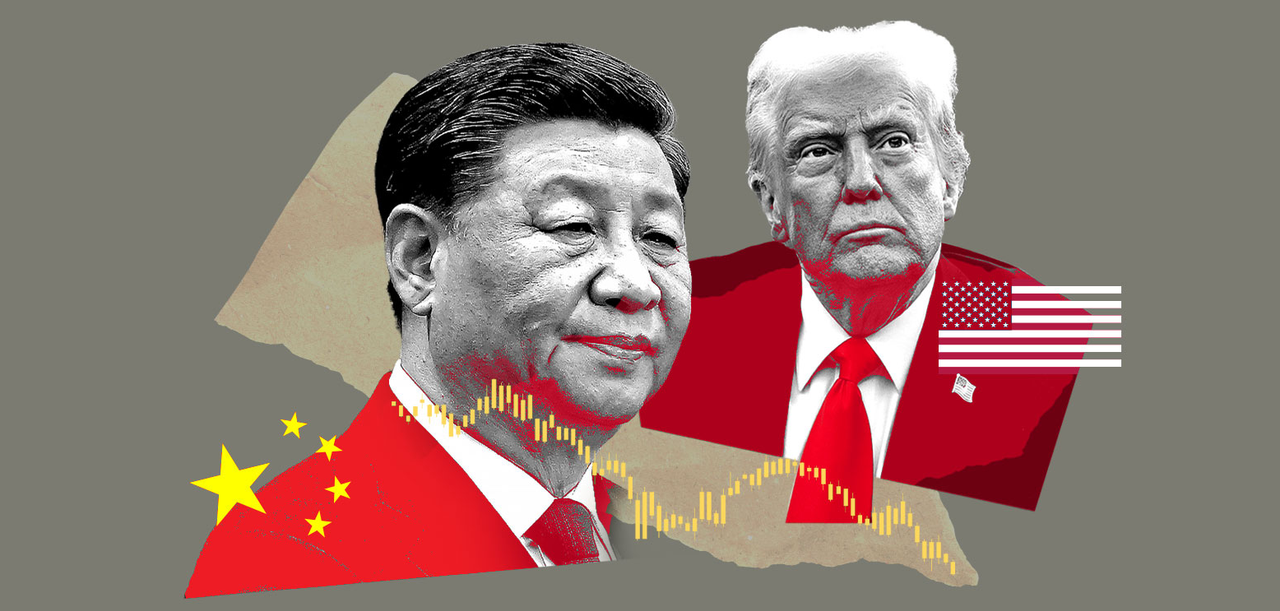
তবে ১৯৯০ ও ২০০০-এর দশকে চীনের অর্থনৈতিক সাফল্য সত্ত্বেও আমেরিকার পরাশক্তির অবস্থান টলে যায়নি। কারণ, তখনও ওয়াশিংটন উদার আন্তর্জাতিক নীতির পক্ষে থেকে বিশ্বে সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছিল।
২০০৮ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের পর চীনের উত্থান ও আমেরিকার শক্তি হ্রাস নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। এই সংকটের মূল কেন্দ্র ছিল পশ্চিমা দেশগুলো। তখন দ্য ইকোনমিস্ট লিখেছিল, ‘পুঁজিবাদ উপসাগরে’। কারণ পশ্চিমা দেশগুলো নিজেদের অর্থনৈতিক মডেল নিয়েই সন্দিহান হয়ে পড়ে। এই সুযোগে চীন তার নিজস্ব রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদে আত্মবিশ্বাস অর্জন করে। ‘বেইজিং ঐকমত্য’ নামে চীনা মডেলটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যা পশ্চিমা উদার অর্থনীতির এক বিকল্প হিসেবে দেখা দিতে শুরু করে।
সেই সময়ও যুক্তরাষ্ট্র চীনের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। কিন্তু ২০০৯ সালে মার্টিন জ্যাকসের ‘হোয়েন চায়না রুলস দ্য ওয়ার্ল্ড: দ্য অ্যান্ড অব দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য রাইজ অব এ নিউ গ্লোবাল অর্ডার’ বই তখনকার সময়ের মনোভাবের পরিবর্তন তুলে ধরে। বইটিতে বলা হয়েছিল, পশ্চিমা প্রাধান্য শেষের দিকে এবং চীন একটি নতুন বৈশ্বিক শৃঙ্খলা গড়ে তুলছে।
বইয়ের লেখক বলেন, সেই সময় তিনি বেইজিংয়ে কূটনীতিক হিসেবে কাজ করতেন এবং সেখানে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যে বাড়তে থাকা আত্মবিশ্বাস নিজের চোখে দেখেছেন। ওই আর্থিক সংকটের পর থেকেই চীনের পররাষ্ট্রনীতি আরও শক্ত অবস্থান নিতে শুরু করে।

২০১৭ সালে শুরু হয় চীন-আমেরিকা শক্তির ভারসাম্য নিয়ে আলোচনার তৃতীয় ধাপ। সেই বছরের জানুয়ারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এক নতুন মহাকৌশলের ঘোষণা দেন।
চীনের জাতীয় নিরাপত্তা কর্ম ফোরামের একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে শি বলেন, চীন আর আগের মতো কম প্রোফাইলে থাকবে না। ১৯৯০-এর দশকে দেং শিয়াওপিং বলেছিলেন, চীন ধীরে ধীরে শক্তিশালী হোক, কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে খুব একটা চোখে না পড়ুক। শি জিনপিং সেই নীতি বদলে দিয়ে বলেন, এখন চীন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে আরও সক্রিয় ও নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকবে।
এই কৌশলগত পরিবর্তনকে ২০১৭ সালের শেষের দিকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। বেইজিং এখন বিশ্বাস করে, চীন আর শুধু একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়, বরং আমেরিকার সঙ্গে সমান কাতারে থাকা এক নতুন পরাশক্তি। এই অবস্থান বদলের ফলে আবারও আন্তর্জাতিকভাবে ‘দ্বিমেরু বিশ্ব’ অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে ঘিরে দুটি শক্তিশালী শিবির নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।
চতুর্থ এবং সর্বশেষ ধাপটি শুরু হয়েছে ২০২৫ সালে ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার মাধ্যমে। অনেক সমালোচক আগেই বলেছিলেন, তার ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতি আসলে আমেরিকার প্রতিপক্ষদের বিশেষ করে চীনের জন্য একধরনের উপহার। তবে প্রথম মেয়াদে ট্রাম্প সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব নেতৃত্ব বা তার পররাষ্ট্রনীতিকে ভাঙার কথা বলেননি।
কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। ট্রাম্প এখন সত্যিই আমেরিকার কয়েক দশকের পুরোনো পররাষ্ট্রনীতি ভেঙে ফেলছেন, যা এতদিন যুক্তরাষ্ট্রকে বৈশ্বিক নেতৃত্ব ও প্রভাবের সুবিধা দিয়েছে। যদি ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকটের পর চীনা নেতারা বুঝতে পারতেন যে শক্তির ভারসাম্য তাদের দিকে ঝুঁকছে, তাহলে এখন বেইজিংয়ের অভ্যন্তরে যে আত্মবিশ্বাস ও উচ্ছ্বাস চলছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।



-20250706211132.webp)


 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন




-20251126094232.webp)




-20251129010608.webp)


-20251129004833.webp)


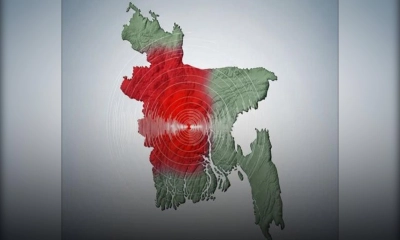



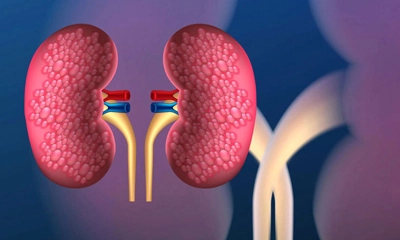


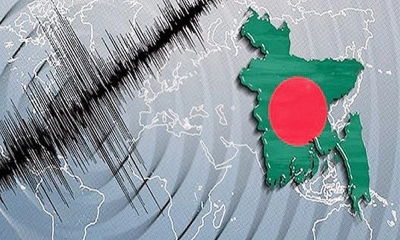





-20251124145649-20251126113752.webp)
আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন