বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থায় খেলাপি ঋণ অর্থনীতির একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। প্রতি বছর এই ঋণের বোঝা দেশের অর্থনীতির কাঁধে জেঁকে বসেছে। গুটিকয়েক অসৎ মানুষের লোভ, সীমাহীন দুর্নীতি এবং সিদ্ধান্তগত দুর্বলতার কারণে খেলাপি ঋণ আজকের এই অবস্থায় এসেছে। ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানও এই খেলাপি ঋণের ভারে জর্জরিত। বিগত কোনো সরকারের সময়কালেও দেশ এই খেলাপি ঋণের হাত থেকে মুক্তি পায়নি। ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদানের বিপরীতে সেই ঋণ ফেরত পায়নি। এটা এক ধরনের প্রবণতা তৈরি হয়েছে। অপরাধ করেও অপরাধীকে শাস্তির আওতায় আনার ক্ষেত্রেও দুর্বলতা রয়েছে।ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণের সঞ্চিত অর্থ এভাবে নষ্ট হয়েছে। বিপরীতে কিছু ব্যাংকের ক্ষেত্রে মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। অস্তিত্ব সংকটেও পড়েছে কয়েকটি ব্যাংক। এই অবস্থা তো একদিনে তৈরি হয়নি। কোনো একজন নির্দিষ্টভাবে দায়ী নন। ব্যাংকগুলোর ঋণ প্রদান এবং আদায় করতে না পারার পেছনে যে কারণগুলো রয়েছে মূলত সেসব দূরীভূত না হওয়ায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।
দেশের অর্থনীতি যখন একটু একটু করে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণ অর্থনীতিতে বাধার দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এভাবে চলতে থাকলে একদিন আরও বিপুল অংকের ঋণ খেলাপি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো ঋণ সময়মতো পরিশোধ করা না হলে খেলাপি হয়ে যায়। ব্যাংকগুলো আমানতকারীর অর্থই ঋণ হিসেবে বিতরণ করে। বিতরণ করা ঋণ সময়মতো ফেরত না পেলে আমানতকারীরা টাকা তুলতে সমস্যায় পড়েন। এখন যে কয়েকটি ব্যাংক গ্রাহকের টাকা ফেরত দিতে সমস্যায় পড়েছে, সেসব ব্যাংকের ঋণ আদায় হচ্ছে না। যখন কোনো ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন ব্যাংকের আমানতকারীদের উপরেও তার প্রভাব পরে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপরে সাধারণের আস্থা কমে এবং ব্যাংক তারল্য ঘাটতিতে পরতে পারে।
ব্যাংকগুলোর তারল্য সংকট যখন বাড়তে থাকে তখন এর প্রভাব দেখা যায় বাজারে। এক ধরনের সংকট তৈরি হয়। মূল্যস্ফীতি এবং কর্মসংস্থানেও প্রভাব পরতে থাকে। খেলাপি ঋণ এবং দুর্নীতি আর্থিক খাতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে, যা সাধারণ মানুষ এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থার অভাব তৈরি করে। মোট কথা সামগ্রিক অর্থনীতিতে একটি নেতিবাচক ধারা তৈরি করছে এই খেলাপি ঋণের পেছনের অসাধু মানুষগুলো। একটি চক্র দেশের অর্থনীতিকে সুপরিকল্পিতভাবে এবং নিজের স্বার্থে দুর্বল করছে। কেউ অবৈধভাবে ক্ষমতা খাটিয়ে মোটা ঋণ বাগিয়ে নিয়েছেন যার খবর আমরা পত্রিকায় পড়ছি, কেউ আবার অসাধু উপায় জেনেও দিয়েছেন! অপরাধ উভয়েরই। রাজনীতির ক্ষমতা নিয়ে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও নানা অপকর্ম করেছে, আবার অনেক ব্যাংকগুলোতে রাজনীতির প্রভাবের স্বীকার হতে হয়েছে। ব্যক্তিকে যখন রাজনৈতিক বিবেচনায় ঋণ দেওয়া হয় তখন সেটি ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনাও অন্ধকারে থাকে। কারণ এদেশে রাজনীতি মানেই অগাধ ক্ষমতা। অপরাধ এই সিস্টেমের। দুর্নীতির কালো থাবা ধরেছিল এদেশের ব্যাংকিং খাতকেও। লেজুরবৃত্তির রাজনীতি আর অসৎ মানুষ এই দুইয়ে ব্যাংকগুলোর অবস্থা খারাপ হয়েছে। সব ব্যাংক না হলেও বিশেষত যেসব ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেশি। প্রতিটি ঋণের বিপরীতে জামানত রাখার যে নিয়ম তা পালন করা হয়নি। আবার নামে-বেনামেরও ঋণ পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আর্থিক খাতে এতসব অনিয়ম এখন ঘাড়ে বড়সড় বোঝা হয়ে বসেছে।
দেশের একেবারে প্রান্তিক জনতা এসব ঋণ খেলাপি বোঝে না। এই যে কতিপয় ব্যাংক থেকে শত শত কোটি টাকা ঋণ নিয়ে অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তার প্রভাব যে সেই প্রান্তিক মানুষটার গায়েও লাগছে সেটি তিনি বুঝতে পারছেন না। তবে পরিণতি ভোগ করছেন। ব্যাংক সচ্ছল হলে লাভ আপামর জনসাধারণের। আর ব্যাংকের আর্থিক চিত্র দুর্বল হলে তা হতাশার। অথচ যাদের ঋণ সত্যিই দরকার, যারা ব্যবসাটাকে দাঁড় করাতে চান তাদের অনেককেই ফিরতে হয় খালি হাতে বা কম ঋণ পেয়ে। কারণ ওই যে তারল্য ঘাটতি।
চলতি মাসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৪ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। তিন মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৭৪ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা। এক বছরের ব্যবধানে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ২ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বেশি। গত মার্চ শেষে খেলাপি ঋণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ২০ হাজার ৩৩৪ কোটি ৯৪ লাখ টাকা, যা গত ডিসেম্বর শেষে ছিল ৩ লাখ ৪৫ হাজার ৭৬৪ কোটি ৮৬ লাখ টাকা।
এতে আরও দেখা গেছে, জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকেই শ্রেণিকৃত ঋণ বা খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৭৪ হাজার ৫৭০ কোটি ৮ লাখ টাকা। মার্চ শেষে মোট বিতরণ করা ঋণের ২৪ দশমিক ১৩ শতাংশ খেলাপি হয়ে গেছে। মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকগুলো বিতরণ করেছে ১৭ লাখ ৪১ হাজার ৯৯২ কোটি ১৩ লাখ টাকা। তিন মাস আগে তা ছিল ১৭ লাখ ১১ হাজার ৪০২ কোটি টাকা। গত মার্চ পর্যন্ত রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের মোট ঋণের ৪৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ খেলাপিতে পরিণত হয়েছে। তিন মাস আগে তা ছিল ৪২ দশমিক ৮৩ শতাংশ। বেসরকারি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ১৫ দশমিক ৬০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০ দশমিক ১৬ শতাংশ হয়েছে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের সময় খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। সেই জায়গা থেকে আজ তা প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এ সময়ে খেলাপি ঋণ সবচেয়ে বেশি বেড়েছে বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোয়।
খেলাপি ঋণের একটি অন্যতম কারণ হিসেবে বলা যায়, ঋণ প্রদানের নামে কতিপয় ব্যাংকের অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত। সরকার পরিবর্তনের পর যে ঋণ প্রদানে ব্যাপক অনিয়ম সামনে এসেছে সেটি প্রমাণ করে ঋণ প্রদানে যথাযথ নিয়ম পালন করা হলে এত বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণের বোঝা দেশকে বহন করতে হতো না। স্বজনপ্রীতি, দলপ্রীতি বা ক্ষমতার অপব্যবহার করার মাধ্যমে ঋণ দেওয়া-নেওয়া হয়েছে। ঋণের নামে বিপুল অর্থ লুট করা হয়। সেই টাকা আর ফেরত আসছে না। দখল করা কোনো কোনো ব্যাংকের খেলাপি ঋণের হার এখন ৯৮ শতাংশে ঠেকেছে। একসময় বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মোট ঋণের যেখানে ৫ শতাংশের কম ছিল খেলাপি। যদিও খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির পাঁচ কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে মেয়াদি ঋণখেলাপির সময় পুনর্র্নির্ধারণ, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনে কিছু বড় অঙ্কের ঋণ বিরূপমানে শ্রেণিকৃত হওয়া, গ্রাহকের চলতি ঋণ নবায়ন না হওয়া, পুনঃতফসিল করা ঋণের কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধ না হওয়া এবং বিদ্যমান খেলাপি ঋণের ওপর সুদ যোগ হয়ে বেড়েছে খেলাপি।
একদিকে বাড়ছে খেলাপি ঋণের বোঝা অন্যদিকে ব্যাংকগুলোতে কমছে ঋণ বিতরণ। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ সময়ে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মাত্র ৩০ হাজার ৫০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করেছে। ঋণ বিতরণ কমলেও প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। গত ডিসেম্বর শেষে প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৬ হাজার ১৩০ কোটি টাকা। চলতি বছরের মার্চ শেষে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৭০ হাজার ৬৫৫ কোটি টাকা। একই সময়ে বেড়েছে মন্দ ঋণের পরিমাণও। মার্চ শেষে মন্দ ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৪২ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। তিন মাস আগে গত ডিসেম্বর শেষে মন্দ ঋণের পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৯১ হাজার ৫৩৭ কোটি টাকা।
এই দুই চিত্র অর্থনীতির জন্য সুখকর নয়। বরং বেশ অস্বস্তিকর বিষয়। বিপরীতে যদি এই বিপুল অংকের ঋণের বড় অংশই আদায়যোগ্য হতো তাহলে দেশের অর্থনীতির চিত্রই পাল্টে যেত। আমরা যে বিপুল অংকের বিদেশি ঋণ দিয়ে দেশের অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন কার্যক্রম করছি তার একাংশ নিজেদের টাকা দিয়েই করা সম্ভব ছিল। অথচ এই টাকা আর ব্যাংকগুলো ফেরত পাবে না। পেলে ব্যাংকগুলোর আমানত বৃদ্ধি পেত এবং তা জনগণের কল্যাণে বিতরণ করা সম্ভব হতো। এ কারণে খেলাপি ঋণ আদায়ে আরও কঠোর অবস্থানে যেতে হবে। এমন নজির স্থাপন করা দরকার যেন ঋণ প্রদানে ঋণ গ্রহীতারা নিয়মিত হয়। আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। মোট কথা অর্থনীতি বাঁচাতে, বাজারের মূল্যস্ফীতি কমাতে এবং সার্বিকভাবে অর্থনীতি চাঙ্গা করতে খেলাপি ঋণ ক্রমহ্রাসমানের পথেই হাঁটতে হবে।


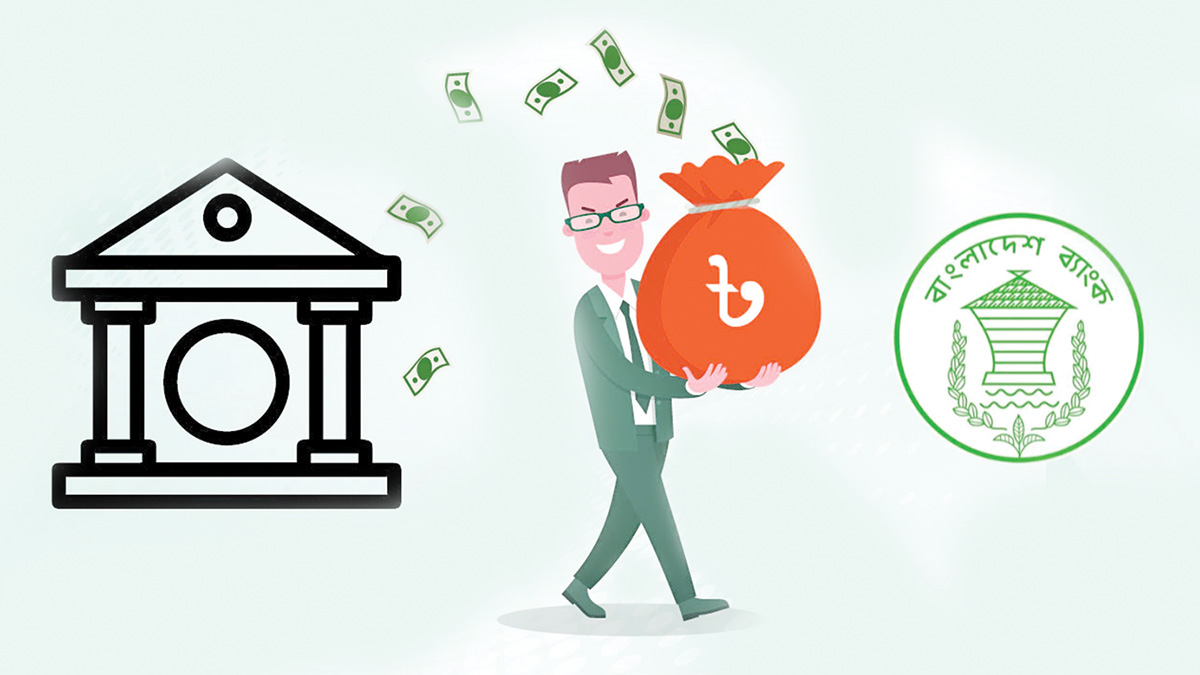


 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন


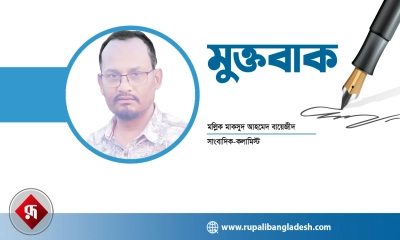










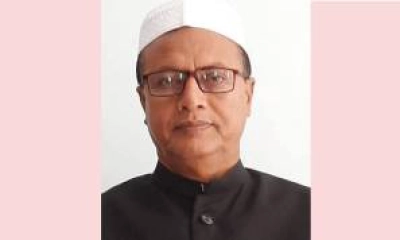
















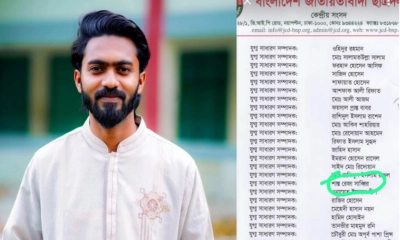
-20251025002118.webp)
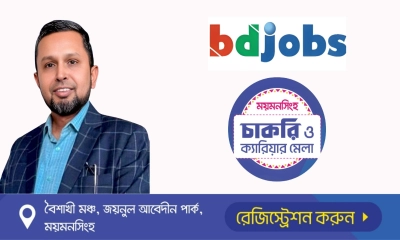




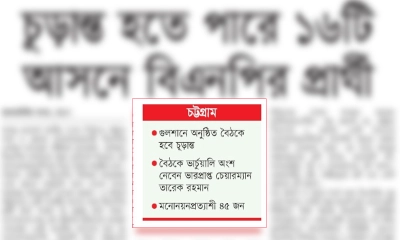

আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন