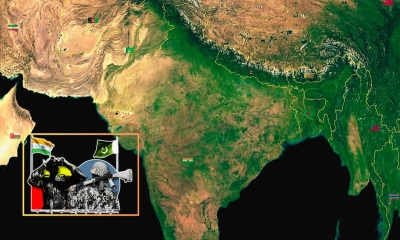বিশ্ব এখন অস্থিরতার আগুনে দগ্ধ। রাষ্ট্রক্ষমতার ভিত্তি ভেঙে পড়ছে একের পর এক দেশে। দক্ষিণ এশিয়া থেকে মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব এশিয়া থেকে ইউরোপ, সবখানেই ক্ষুব্ধ মানুষের ঢেউ। গণবিক্ষোভের ঘটনাগুলো বিশ্বব্যাপী ক্ষমতাসীনদের জন্য অশনিসংকেত। আর সরকারপতন যেন নতুন স্বাভাবিকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল সবখানেই জনতার রোষ আগুন হয়ে জ্বলে উঠেছে। প্রশ্ন উঠছে, এরপর কার পালা? ভারত, উত্তর কোরিয়া, চীন, রাশিয়া, তুরস্ক, নাকি ডোনাল্ড ট্রাম্প? এমনকি ইসরায়েলের বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু কি টিকে থাকতে পারবেন?
সমুদ্রবেষ্টিত শ্রীলঙ্কা দেখিয়েছে, দুর্নীতি আর অর্থনৈতিক ব্যর্থতা কীভাবে রাষ্ট্রকে ধসিয়ে দেয়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শূন্য। জ্বালানি, খাদ্য ও ওষুধের তীব্র সংকট জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। ঋণের দায় পাহাড়সম। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে পর্যটন শিল্পের পতন পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। ব্যাপক দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগ জনরোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
একসময় ক্ষুধার্ত মানুষ রাস্তায় নেমে এলো। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা ঢুকে পড়ল প্রেসিডেন্ট ভবনে। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। মুহূর্তেই গুঁড়িয়ে যায় রাজাপাকসে পরিবারের একচ্ছত্র রাজত্ব। অর্থাৎ জনতা যখন ক্ষুধার্ত হয়, তখন ক্ষমতা টিকে না।
বাংলাদেশে দৃশ্যপট ভিন্ন হলেও ফল একই। রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদ, ভুয়া নির্বাচন, রাষ্ট্রযন্ত্রের দমননীতি, লুটপাট, বিচার বিভাগের অপমৃত্যু সবমিলিয়ে জনআস্থার মৃত্যু ঘটেছে। তরুণ প্রজন্ম সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে আর চুপ করে থাকেনি। বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা দুর্নীতি, বেকারত্ব, বৈষম্য সবকিছুর বিরুদ্ধে তারা রাস্তায় নেমেছে।
দীর্ঘ ১৭ বছরের একনায়কতন্ত্রের আওয়ামী লীগ সরকারের দমননীতির লাঠি যত পিঠে পড়েছে, ক্ষোভ তত জ্বলে উঠেছে। এক সময় সেই ক্ষোভ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। ফলে ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মুখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। সঙ্গে পালায় তার দুর্ধর্ষ একপাল সাঙ্গও। বাংলাদেশের ইতিহাস রচিত হয়—‘জনআস্থার মৃত্যু মানেই সরকারের পতন’।
সুদূর মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সিরিয়ার পরিস্থিতি ছিল আরও ভয়াবহ। ২০১১ সালের আরব বসন্তের ঢেউ সিরিয়াতেও লেগেছিল। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের দাবিতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল, যা বাশার আল-আসাদ সরকারের কঠোর দমন-পীড়নের কারণে দ্রুত গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। পরবর্তী সময়ে দেশটির শাসন টিকে ছিল শুধু রাশিয়ার বন্দুকের নল আর আসাদের লৌহমুষ্টি দিয়ে।
ইসলামিক স্টেটের (আইএস) উত্থান সিরিয়ার সংকটকে নতুন মাত্রা দেয়। গৃহযুদ্ধের ফলে দেশজুড়ে মহামারী আকার ধারণ করে ধ্বংসস্তূপ, দুর্ভিক্ষ আর লাখ লাখ মানুষের বাস্তুচ্যুতি। জনগণের শ্বাসরুদ্ধ জীবন। ক্ষোভ জমেছে। যদিও বিস্ফোরণ ঘটেছে আধিপত্যবাদী পশ্চিমা শক্তির মদদে। দামেস্কের প্রাসাদ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন বাশার আল-আসাদ।
বহুকাল ধরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় নিমজ্জিত নেপাল। রাজতন্ত্র পতনের পরও স্থিতিশীলতা আসেনি। ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন, দুর্বল জোট সরকার এবং মাওবাদী বিদ্রোহ দেশটির উন্নয়নের পথে বড় বাধা। অর্থনৈতিক দুর্বলতা, বেকারত্ব, ব্যাপক দুর্নীতি এবং অবকাঠামোগত অভাব জনমনে তীব্র অসন্তোষ তৈরি করেছে।
গত সোমবার জেন-জিদের বিক্ষোভের মুখে নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। যদিও দেশটিতে বড় ধরনের গণবিক্ষোভের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটেনি। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং ক্ষমতার লড়াই দেশটির সরকারকে দুর্বল করে রেখেছিল দীর্ঘদিন।
টেক্সাসের ডালাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডজাংক্ট ফ্যাকাল্টি ও ভূ-রাজনৈতিক কলাম লেখক শাফকাত রাব্বির মতে, বিশেষজ্ঞের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে এমন তিনটি মূল বিষয়ের মিল রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে। তা হলো পারিবারিক শাসনের অধীনে কর্তৃত্ববাদ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি এবং ঋণ-চালিত অহংকার (মেগা) প্রকল্প।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইন্দোনেশিয়াতেও বড় ধরনের সরকার পতন ঘটেনি। তবে, সেখানেও জনবিক্ষোভ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা গেছে। দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং পরিবেশগত ইস্যুগুলো জনঅসন্তোষের কারণ। সরকার এই সমস্যাগুলো মোকাবিলায় প্রায়শই ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও বেকার তরুণদের ক্ষোভ জমছে তীব্রভাবে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দেশটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অনিশ্চয়তার দিকে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে সাম্প্রতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বও বড় বেকায়দায় ফেলেছে মুসলিম অধ্যুষিত দেশটিকে।
গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত অং সান সু চির সরকারকে ২০২১ সালে সামরিক বাহিনী উৎখাত করার পর থেকেই মিয়ানমার এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি। সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। এই পরিস্থিতি দেশটিকে এক নৃশংস সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে।
তবে জান্তা সরকার সম্প্রতি নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ায় কিছুটা আশার আলো দেখছেন অনেকেই। কিন্তু ভূ-রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মত, সংকট এখনও কাটেনি। আরাকানে ক্ষমতার লড়াই বিদ্যমান। জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিবেশী দেশে আশ্রিত এবং বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ দেশটির জন্য মাথাব্যথার অন্যতম কারণ।
শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি-বিষয়ক অধ্যাপক পল স্ট্যানিল্যান্ডের দাবি, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের বিক্ষোভগুলোর ‘বেশিরভাগেরই নাটকীয় কোনো ফলাফল না থাকলেও, ভুল পদক্ষেপ এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনা’ যেকোনো মুহূর্তে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। তার মতে, ‘নেপাল দক্ষিণ এশিয়ায় অস্থিতিশীলতার নতুন রাজনীতির দৃষ্টান্ত’।
তবে এখন বড় প্রশ্ন হলো বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলো কী টিকতে পারবে?
দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ রাষ্ট্র ভারতে প্রবৃদ্ধির জোয়ার থাকলেও বেকারত্ব ও মূল্যস্ফীতি অস্বীকার করা যাচ্ছে না। সবচেয়ে বড় বিপদ ধর্মীয় বিভাজন। বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা আপাতত অটুট, কিন্তু আস্থা ভাঙতে শুরু করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে ভারতের গণতন্ত্রও ভেঙে পড়তে দেরি হবে না। সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে গণবিক্ষোভ ও সরকার পতনের আঁচ থেকে রেহাই পাবে কি না, সেটা নিয়েও চলছে চুলছেঁড়া বিশ্লেষণ।
নেপালের বিক্ষোভ ও প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের পর ভারতের শিক্ষা নেওয়া উচিত উল্লেখ করে সংবাদমাধ্যম ইকোনমিক টাইমস এক প্রতিবেদনে বলেছে, ‘নেপালের আগুন ক্ষুধা ও বেকারত্বের স্ফুলিঙ্গ। ভারতের এ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। ভারতে কর্মসংস্থান ধ্বংস হয়ে গেছে, নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহ গণতন্ত্র ধ্বংস করে নির্বাচনে জয়লাভ করছেন। গণতন্ত্রের সমস্ত স্তম্ভ ভেঙে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে। ধর্ম ও বর্ণের রাজনীতি চরমে পৌঁছেছে। এই সমস্ত ব্যাধি দেশের জন্য বিপজ্জনক।’
প্রতিবেদনে নেপাল সরকারের পতনের পর মোদি তার ক্ষমতা হারাবেন কি না—এমন প্রশ্নও ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। সামনার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, দুর্নীতি অসহনীয় হয়ে পড়ায় জনগণ শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের সরকার উৎখাত করেছে। যখন জনগণের মনে আত্মসম্মানের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে, তখন তা জ্বলতে বেশি সময় লাগে না। তখন মানুষ বন্দুক-কামানেরও তোয়াক্কা করে না। নেপাল সরকারের পতনের পর মোদি কি তার ক্ষমতা হারাবে?
পূর্ব এশিয়ার উত্তর কোরিয়া একটি অত্যন্ত স্বৈরাচারী রাষ্ট্র। সেখানে জনগণের ক্ষোভ প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। কিম জং উন সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং গণমাধ্যমের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বজায় থাকায় সরকার পতন ততটাও সহজ নয়। জনগণের উপর কঠোর নজরদারি এবং দমন-পীড়ন সেখানকার শাসনের মূল ভিত্তি। কিন্তু ইতিহাস বলে, একনায়কতন্ত্র ভেতর থেকেই ভাঙে। কবে হবে, তা সময়ই বলে দেবে।
চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেশটির স্থিতিশীলতার প্রধান কারণ। তবে, অর্থনৈতিক মন্দা, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য ভবিষ্যতে জনঅসন্তোষের কারণ হতে পারে। সম্প্রতি কোভিড-১৯ সংক্রান্ত কঠোর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে কিছু বিক্ষোভ দেখা গেছে, যা চীনের জন্য বিরল এবং তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল। ইন্টারনেট সেন্সরশিপ ক্ষোভ আড়াল করতে পারে, কিন্তু নিভিয়ে দিতে পারে না। অবশ্য ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের বাণিজ্য দ্বন্দ্ব চীনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধে জড়িয়ে নিজেকেই জালে আটকে ফেলেছেন। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার ফলে রাশিয়ার অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি হলেও, পুতিন সরকার অভ্যন্তরীণভাবে শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। আপাতত শক্তিশালী মনে হলেও ভেতরে ক্ষয় শুরু হয়ে গেছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।
রুশ নাগরিকরা যুদ্ধে যেতে অনীহা জানালেও বল প্রয়োগের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এজন্য প্রতিবাদও হয়েছে, যা দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কিন, ইউরোপ ও ন্যাটোর সঙ্গে দ্বন্দ্বের ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কোণঠাসা ক্রেমলিন। এছাড়াও ভিন্নমতের প্রতি কঠোর দমন-পীড়ন এবং রাষ্ট্রীয় প্রচারণার কারণে জনবিক্ষোভ বড় আকার ধারণ করতে পারে।
এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় রয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান। মূলত তিনি টিকে আছেন ইসলামপন্থি-জাতীয়তাবাদী ভোটব্যাংকে ভর করে। অর্থনৈতিক অস্থিরতা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং এরদোয়ান সরকারের ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা জনঅসন্তোষের কারণ হয়ে উঠছে। বিশেষ করে বিরোধী মতের ওপর তার সরকারের কঠোরতা গদি নড়বড়ে করার অন্যতম কারণ হতে পারে বলে আশঙ্কা।
তবে, এরদোয়ানের জনসমর্থন এখনও অনেক বেশি এবং তিনি শক্ত হাতে দেশ চালাচ্ছেন। আগামী নির্বাচন তার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প এক অদ্ভুত বাস্তবতা। তিনি পতনশীলও, আবার শক্তিধরও। মামলার বোঝা আছে, কিন্তু জনতার বড় অংশ এখনও তাকে চাইছে। আমেরিকান সমাজ বিভক্ত। গণতন্ত্রের ভেতরেই যুদ্ধ চলছে। ট্রাম্পের উত্থান যেমন আমেরিকাকে কাঁপিয়ে তুলেছিল, তেমনটিই হবে তার পতনে বেলায়ও! আর সেই কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বজুড়ে। ইতোমধ্যেই ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতির কারণে গোটা বিশ্বে তোলপাড় বাধালেও, এখন অবধি এই ধাক্কা বেশ শক্ত হাতেই সামলেছেন।
বিশ্বজুড়ে জনবিক্ষোভ এবং সরকারপতনের কারণগুলো পরস্পর সংযুক্ত। বিশ্ব ক্রমশই আরও বেশি সংযুক্ত হচ্ছে, ফলে এক দেশের ঘটনা সহজেই অন্য দেশকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, বিশ্বজুড়ে জনতা কেন ক্ষুব্ধ? উত্তরও সহজ। অর্থনৈতিক বৈষম্য, দুর্নীতি, বেকারত্ব, রাষ্ট্রীয় দমননীতি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সব উন্মোচিত হচ্ছে। মানুষ আর চুপ নেই। জনগণই শেষ কথা বলে এবং ইতিহাস সাক্ষী—যখন জনগণ রাস্তায় নামে, তখন কোনো বন্দুক, কোনো সেনাবাহিনী, কোনো শাসক তাদের থামাতে পারে না।
লেখক: সাংবাদিক।


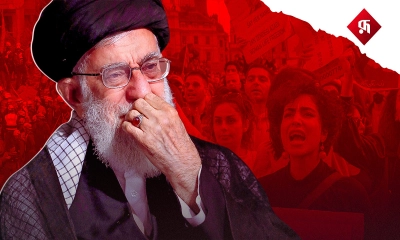
-20250406173810.webp)