ভয় মানুষের অন্যতম প্রাচীন অনুভূতি। আদিম মানুষ অন্ধকার, বজ্রপাত, জঙ্গল, মৃত্যু ও অজানার ভয়ে ভীত থাকত। সেই ভয়ই ধীরে ধীরে রূপ নেয় গল্পে, রূপকথায় ও কাহিনিতে। আমাদের লোককাহিনিতে যেমন পেত্নী, ডাইনি, মামদো ভূত বা শাকচুন্নির উপস্থিতি দেখা যায়, তেমনি বিদেশি সাহিত্যে দেখা মেলে ড্রাকুলা, ওয়ারউলফ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীদের। প্রাচীনকালে মুখে মুখে ছড়ানো এসব গল্প থেকেই জন্ম নেয় ভয়ের সাহিত্য। একসময় তা রূপ নেয় লিখিত রূপে। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় কাহিনিতেও নরক, শাস্তি ও পাপের ভয় দেখানো হতো। এইভাবেই ভয়ের উপাদান ধীরে ধীরে সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।
বিশ্ব সাহিত্যে ভয়ের উত্থান
বিশ্ব সাহিত্যে ভয়ের একটি সোনালি সময় ছিল, যখন এই ধারায় অসাধারণ সব সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হয়। ইউরোপে রচিত গল্পসমূহে একদিকে ছিল অতিপ্রাকৃত অশরীরী অস্তিত্ব, অন্যদিকে ছিল মানুষের মানসিক বিভ্রান্তি ও মনস্তাত্ত্বিক ভয়।
এইসব সাহিত্যকর্মে ভয় কেবল বিনোদনের মাধ্যম ছিল না, বরং তা হয়ে উঠেছিল সমাজ ও মানুষের অন্তর্জগৎ অন্বেষণের এক মাধ্যম। এই সময়কার ভয়ের সাহিত্য মানুষকে ভাবতে শেখায়, ভয়ের পেছনে থাকা কারণ, সমাজের অন্ধকার দিক কিংবা মানুষের ভিতরে লুকিয়ে থাকা বিকৃত রূপগুলো।
বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বিশ্বজুড়ে ভয়ের সাহিত্যের কদর কমতে থাকে। তার অনেকগুলো কারণ আছে।
প্রথমত, পাঠকের রুচির পরিবর্তন ঘটে। তারা ধীরে ধীরে বেশি ঝুঁকে পড়ে বাস্তবধর্মী সাহিত্য, প্রেমের উপন্যাস কিংবা ঐতিহাসিক কাহিনির দিকে।
দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের মধ্যে যুক্তিবোধের চর্চা বাড়িয়ে তোলে। মানুষ আর ভূত, প্রেত, জিন কিংবা অশরীরীতে আগের মতো বিশ্বাস করতে চায় না।
তৃতীয়ত, আধুনিক সমাজে ভয়ের নতুন রূপ সৃষ্টি হয়—যেমন অর্থনৈতিক সংকট, যুদ্ধ, মহামারি, প্রযুক্তির প্রভাব, পরিবেশ বিপর্যয়। এসব বাস্তবভিত্তিক ভয় মানুষের মনে এতটাই গভীরভাবে বসে যায় যে, অতিপ্রাকৃত ভয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে যায়।
সাহিত্যে ভয়ের নতুন পথ
যদিও অতিপ্রাকৃত ভয়ের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে, তবুও ভয় সাহিত্য থেকে একেবারে হারিয়ে যায়নি। বরং তা অন্য রূপে থেকেই গিয়েছে। বর্তমান সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও নাটকে আমরা দেখি ভয় এখন এসেছে আরও সূক্ষ্ম রূপে ধরা দিয়েছে। কখনো তা মানসিক ভীতির রূপে, কখনো সামাজিক অস্থিরতার রূপে, আবার কখনো প্রযুক্তির আশঙ্কা থেকে।
বলতে গেলে ভয়ের চরিত্রও এখন পাল্টেছে। এখন আর ভূত-প্রেতের ভয়ই একমাত্র নয়- মানুষ ভয় পায় একাকীত্বে, বিচ্ছিন্নতায়, সমাজের অসঙ্গতিতে কিংবা নিজের মধ্যকার অন্ধকার প্রবৃত্তিগুলোতে। ফলে, আজকের ভয়ের সাহিত্য আরও মনস্তাত্ত্বিক, জটিল ও গভীর হয়েছে।
বিশ্বায়ন ও নতুন কণ্ঠস্বর
আগে ভয়ের সাহিত্য বলতে মূলত ইউরোপ বা আমেরিকার রচনাকেই বোঝানো হতো। কিন্তু বর্তমান যুগে ভয়ের সাহিত্যে বিশ্বজনীনতা এসেছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার লেখকেরাও এখন তাদের নিজস্ব লোকজ সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও কল্পনার মাধ্যমে নতুন নতুন ভয়ের গল্প তৈরি করছেন।
ভারতের সাহিত্যে যেমন ঠাকুরদা-দিদার মুখে শোনা কাহিনি, বাঙালির বটগাছের ডাইনি, গৃহদেবতার অভিশাপ- এসব এখন নতুন করে সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে ফিরে এসেছে। এইসব কাহিনিতে ভয়ের সঙ্গে সমাজ, পরিবার, রাজনীতি এবং ধর্মের টানাপোড়েনও উঠে আসে। ফলে, ভয়ের সাহিত্য কেবল ভীত করার মাধ্যম নয়—এখন তা হয়ে উঠেছে চিন্তার অনুষঙ্গ।
বাংলা সাহিত্যে ভয়ের চর্যা
বাংলা সাহিত্যে ভয়ের একটি গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। টেনিদার ‘জ্যান্ত ভূত’, সত্যজিৎ রায়ের ‘ভূতের গল্প’, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের অতিপ্রাকৃত রচনা, হুমায়ূন আহমেদের ‘ভয়ঙ্কর রাত’, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘ঘোর’—এসব গল্পে যেমন রোমাঞ্চ রয়েছে, তেমনই রয়েছে সাহিত্যিক উৎকর্ষ।
বাংলা সাহিত্যে ভূতের গল্প সবসময়ই জনপ্রিয়, তবে আজকের পাঠকের কাছে এগুলো নতুনভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে। নতুন প্রজন্মের লেখকেরা এখন হরর বা ভয়ের সাহিত্যে প্রযুক্তি, রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা ও মানুষের মনোজগতকে একত্রে মিশিয়ে দিচ্ছেন- যা এই ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করছে।
ভয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ
ভবিষ্যতে ভয়ের সাহিত্যের পথ কোন দিকে যাবে, এই প্রশ্ন এখন আলোচনার বিষয়। সম্ভবত, ভয় আরও বেশি হয়ে উঠবে মনস্তাত্ত্বিক ও প্রযুক্তিনির্ভর। মানুষের মনের ভিতরের দ্বন্দ্ব, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তৈরি হওয়া আতঙ্ক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিগত তথ্য চুরি, ডিজিটাল গোয়েন্দাগিরি- এসব নিয়ে গড়ে উঠবে নতুন ভয়ের উপাখ্যান।
এছাড়াও, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক সংকটও সাহিত্যে নতুন ভয়ের জন্ম দেবে। অর্থাৎ, ভয় তার রূপ পাল্টাবে, কিন্তু তার প্রয়োজন কখনোই ফুরাবে না। কারণ ভয় মানুষের আবেগ, চিন্তা ও চেতনার গভীরতম স্তরের সাথে সম্পর্কিত।


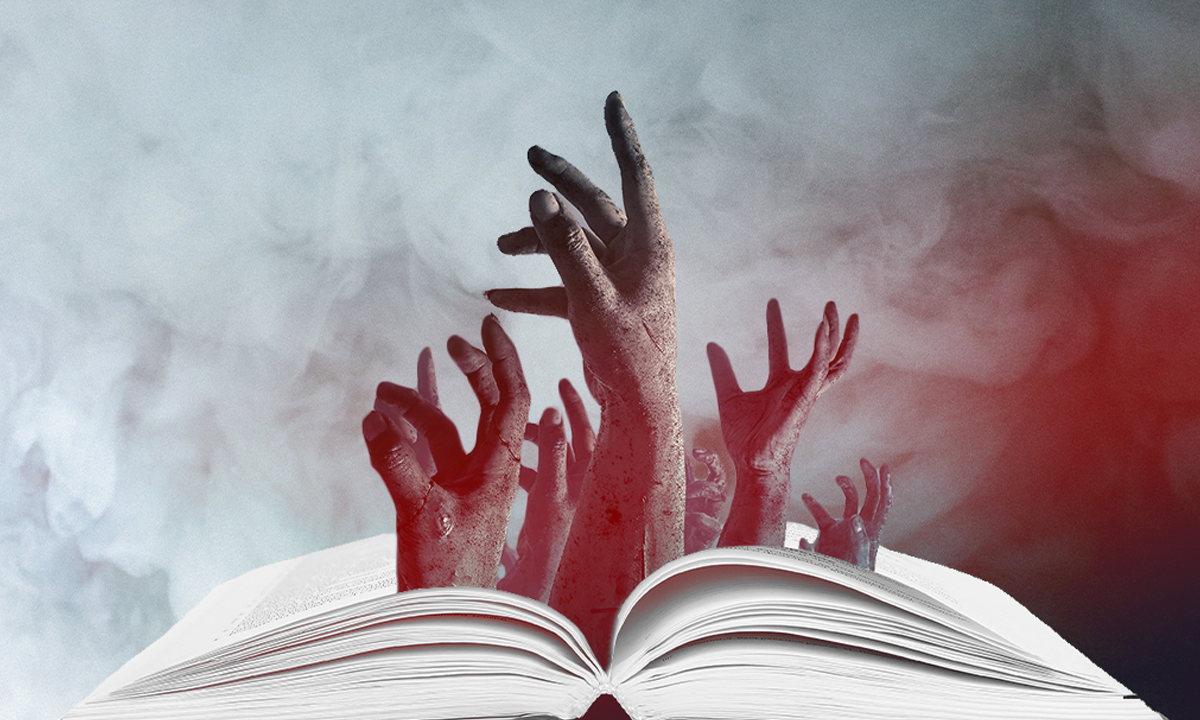
 সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন




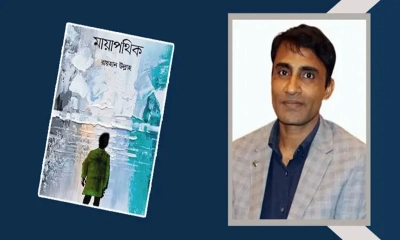
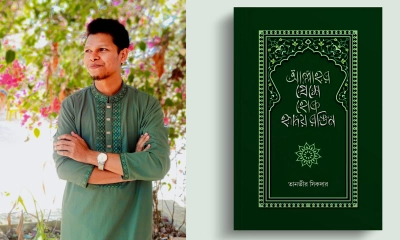




-20251020020047.webp)
-20251020015814.webp)
-20251020015712.webp)

-20251020015407.webp)









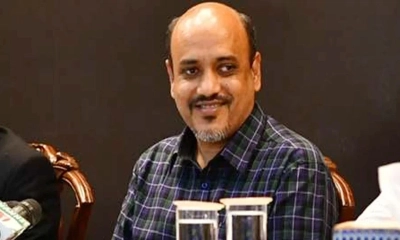





আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন